বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান

বিংশশতাব্দীতে
বিজ্ঞানে কিছু
আবিষ্কার ও উদ্ভাবন এবং ঘটনা
( ৪)
জৈব
যৌগ পৃথকীকরণে কলাম ক্রোমাটোগ্রাফির কৃত্কৌশল
( Column
Chromatography Technique for Organic Compound
Separation )
আবিষ্কার : ১৯০১
খীষ্টাব্দ
বিজ্ঞানী : মিখাইল টিভেট, রশিয়া
একটা সাদা দড়ি
বা সুতা (string)-র একটা দিক ঝুলন্ত অবস্থায়
রঞ্জকের পাত্রে নিমজ্জিত করে রাখলে দড়িটি
রঞ্জককে শুষে নিতে শুরু করে । কিন্তু রং বিভিন্ন
হলে দড়ি ধরে ওঠার দূরত্বও হবে বিভিন্ন । বহুদিন
ধরেই রঞ্জক প্রস্তুতকারকরা 'ক্রোমাটোগ্রাফি'
ব্যবহার করে আসছেন, মিশ্রণ থেকে বিভিন্ন রংকে
আলাদা করার কাজে, বিশেষতঃ যদি মিশ্রণের উপাদানগুলি
অল্প পরিমাণে হয় । এই কৃত্কৌশলটি অত্যন্ত
প্রযোজ্য যখন মিশ্রণের উপাদানগুলির ভৌতিক
(physical) ও রাসায়নিক (chemical) ধম একই
হয় এবং সাধারণ পৃথক্করণের উপায়গুলি কাজে দেয়
না । 'ক্রোমাটোগ্রাফি' কথাটির অর্থ রং দিয়ে
লেখা [গ্রীক ভাষায় : khromatos অর্থ রং, graphos
অর্থ লিখিত]। ক্রোমাটোগ্রাফি কৃত্কৌশলটি আবিষ্কার
করেন মিখাইল সোয়েট (Mikhail tswett) ১৯০৬
খ্রীষ্টাব্দে ।
ক্রোমাটোগ্রাফি-তে
আলাদা করার কৃত্কৌশলগুলির ভিত্তি হল মিশ্রণে
উপাদানগুলির বিন্যাস- স্থির (stationary)
এবং সচল (mobile) অবস্থা । স্থির অবস্থাটি
হতে পারে একটি শোষকের কলাম, একটি কাগজ, একটি
পাতলা শোষকের আবরণ কাচের উপর, ইত্যাদি, যার
মধ্য দিয়ে সচল অবস্থা যায় । সচল অবস্থাটি
হতে পারে তরল পদার্থ বা গ্যাস । যখন স্থির
কঠিন অবস্থাকে একটি কলাম হিসাবে নেওয়া হয়,
প্রথাটিকে বলা হয় 'কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি' (
চিত্র ) ।
কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি
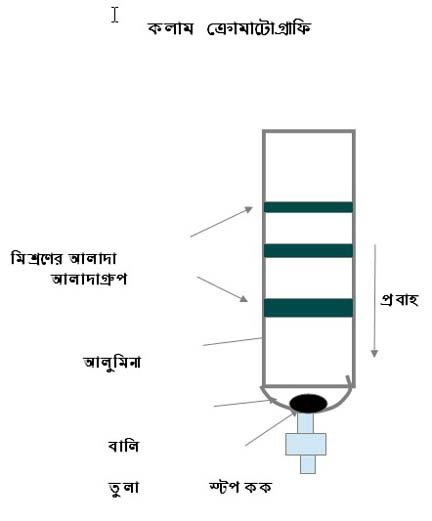
চিত্র : কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি
কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি-তে
সাধারন শোষকগুলি হল সিলিকা, আলুমিনা, ক্যালসিয়াম
কার্বনেট, ক্যালসিয়াম ফসফেট, ম্যাগনেসিয়া,
স্টার্চ, ইত্যাদি । দ্রাবক (solvent) নির্বাচন
করা হয় শোষক ও দ্রাবকের প্রকৃতি বিচার করে
। মিশ্রণের উপাদানগুলির কত তাড়াতাড়ি পৃথক্করণ
হবে তা' নির্ভর করবে শোষকের তত্পরতা এবং দ্রাবকের
বিপরীত-ধর্মিতার উপর । যদি শোষকের তত্পরতা
খুব উচ্চ হয় এবং দ্রাবকের বিপরীত-ধর্মিতার
খুব কম হয়, পৃথক্করণ হবে খুব ধীরে, কিন্তু
তার গুণমান হবে ভাল । অন্যদিকে যদি শোষকের
তত্পরতা নিম্নস্তরের হয় এবং দ্রাবকের বিপরীত-ধর্মিতার
উচ্চস্তরের হয়, পৃথক্করণ হবে খুব তাড়াতাড়ি,
কিন্তু গুণমান হবে নিকৃষ্ট অর্থাত্ উপাদানের
পৃথক্করণ ১০০-শতাংশ বিশুদ্ধ হবে না ।
শোষককে তরলায়িত (slurry) করা হয় উপযুক্ত তরল
পদার্থ সংযোগে এবং ঢালা হয় একটি নলাকৃতি টিউবে
যার তলাটি হল ছিদ্রপূর্ণ বা তুলা দিয়ে আটকানো
। যে মিশ্রণটিকে আলাদা করতে হবে, তাকে একটি
উপযুক্ত দ্রাবকে দ্রবীভূত করে টিউবে উপর দিক
থেকে ঢালতে হবে । মিশ্রণ টিউব ধরে যত নামবে
উপাদানগুলি বিভিন্ন উচ্চতায় শোষিত হবে ; যার
শোষণ-ক্ষমতা সবথেকে বেশি সে থাকবে সবথেকে
উপরে এবং সেই মতন নলের উপরথেকে নীচে আলাদা
আলাদা ব্যাণ্ড তৈরি হবে । যে পদ্ধতিতে শোষক
থেকে উপাদানগুলিকে ব্যাণ্ডে রূপান্তর করা
হয়, তাকে বলে 'এলুশন' (এলতেেওন) ।
( ৫)
মনুষ্য-রক্তের
শ্রেণির আবিষ্কার
আবিষ্কার : ১৯০১
খ্রীষ্টাব্দ
বিজ্ঞানী : কার্ল ল্যাণ্ডস্টাইনার
১৭১৮
খ্রীষ্টাব্দে হারভে 'রক্তসংবহন' আবিষ্কার
করার পর থেকেই ক্রমাগত প্রচেষ্টা চলেছিল মানুষের
দেহে শোণিত সংক্রমণ করার জন্য । ফরাসী দার্শনিক
ডেনিস এবং শল্যচিকিত্সক মারে প্রথম চেষ্টা
চালান মানুষের দেহে ভেড়ার রক্ত (১৫০ মিলিলিটার)
সংক্রমন করার । পরবর্তীকালে আরও অনেকে এই
প্রচেষ্টা চালান কিন্তু ফল হয় মারাত্মক ।
ফলশ্রুতি হিসাবে শোণিত সংক্রমণ বন্ধ হয়ে যায়
।
এক শতাব্দী পরে আবার প্রচেষ্টা হয় শোণিত সংক্রমণের
। ১৮১৯ খ্রী-তে ব্ল্যান্ডেল ইতিহাসে প্রথম সাফল্যের
সঙ্গে শোণিত সংক্রমণ করান, একজন মানুষের শরীর
থেকে আরেকজনের শরীরে । তবে সাধারণভাবে বলা
যায় শোণিত সংক্রমণ প্রচেষ্টা হতাশাজনক হয়ে
দাঁড়ায় ; কখনও বা রোগী সুস্থ হন, কখনও বা
তাঁর মৃত্যু হয় । বস্তুতঃ, এর কারণ মানুষের
কাছে অজ্ঞাত ছিল ।
অস্ট্রিয়া-র স্কলার কার্ল ল্যাণ্ডস্টাইনার
এই বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন ১৯০০ খ্রী-তে ।
একটা টেস্ট টিউবে তিনি নিজের লোহিত রক্তকণিকা
সঙ্গে মেশালেন নিজের শরীরের রক্তাম্বু (blood serum), কোনও পুঞ্জীভবন হতে দেখলেন না : যখন
বিভিন্ন ব্যক্তির রক্তকণার সঙ্গে রক্তাম্বু
মেশালেন, দেখলেন পুঞ্জীভুত হচ্ছে বা কখনও
কখনও হচ্ছে না । এই ঘটনা অবশ্য অনেকেরই নজরে
এসেছিল, কিন্তু ল্যাণ্ডস্টাইনার ছাড়া কেহই
ব্যাখ্যা দিতে পারেননি । লোহিত রক্তকণিকার
দু'প্রকারের বিশেষ গঠনবিন্যাস আছে যারা একত্রে
অথবা আলাদা ভাবে থাকতে পারে । রক্তাম্বু-র
একটি প্রতিরক্ষিকা (antibody) আছে, নাম লোহিত
রক্তকণিকার ভিতরের বিশেষ গঠনের agglutinin;
এই agglutinin যখন লোহিত রক্তকণিকার বিশেষ
গঠনবিন্যাসের মধ্যে পড়ে, পূঞ্জীভবন হয় যা
রোগীর রক্তসংবহন-কালে মারাত্মক হতে পারে ।
এর থেকে ল্যাণ্ডস্টাইনার একটি সিদ্ধান্তে
উপনীত হন যে, মনুষ্য রক্ত-শ্রেণী হল বংশাণুধৃত
।
১৯০৯ খ্রী-তে সমস্যার সমাধানকল্পে ল্যাণ্ডস্টাইনার
রক্তকে চারটি শ্রেণী-তে ভাগ করলেন-
A, B, AB এবং O। ডাক্তাররা রোগীর রক্ত পরীক্ষা করে
সঠিক শ্রেণী নির্ধারণ করে রক্তসংবহন করতেন
।
যেহেতু রক্ত-সংবহন পূর্বে ধারাবাহিকভাবে বিফল
হয়েছে, সাধারণ চিকিত্সকরা এটি ব্যবহার করা
থেকে বিরত থাকতেন ; তবে বহু সংখ্যক বিজ্ঞানী
এটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যাচ্ছিলেন
। নাটকীয়ভাবে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এনে দিল রক্ত-সংবহন
পরীক্ষার এক বিশাল সুযোগ । যেহেতু যুদ্ধে
আহতদের জীবন নিয়ে সমস্যা, রক্ত-সংবহন প্রথা
হয়ে দাঁড়ালো আহতদের মৃত্যুর নিশ্চিত দরজা
থেকে ফিরিয়ে আনার এক অস্ত্র । ডাঃ ওল্ডেনবার্গ
প্রথম পুঞ্জীভবনের প্রতিক্রিয়া জানবার জন্য
রক্ত-মিলান পরীক্ষা শুরু করলেন রক্ত-সংবহন
প্রক্রিয়ার আগে । দু'জন ব্যক্তির মধ্যে রক্তসংবহন
তখনই সম্ভব যখন কোনও পূঞ্জীভবন হবে না লোহিত
রক্তকণিকা আর রক্তাম্বু মেশালে । এই প্রক্রিয়া
বিশাল সাফল্য এনে দিল এবং প্রচুর জীবন বাঁচলো
। পরবর্তী বত্সরগুলিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও
ব্যবহারের ফলে রক্ত-সংবহন হয়ে দাঁড়ালো একটি
নিরাপদ ব্যবস্থা, এবং ১৯২০ খ্রী-র শেষদিকে
ইয়োরোপ ও উত্তর আমেরিকায় রক্ত-সংবহন হয়ে দাঁড়ালো
মেডিকেল শাস্ত্রের একটি সফল ও সর্বগ্রাহ্য
প্রক্রিয়া ।
আমরা এখন জানি বিভিন্ন জাতির নরনারীর রক্ত-শ্রেণী
বিভিন্ন রকমের । যথা, শ্রেণী O খুবই সাধারন
UKতে, শ্রেণী B- এশিয়া মহাদেশে । O শ্রেণী
হল সব থেকে পুরাণো- প্রস্তরযুগ থেকে এর অস্তিত্ব
পাওয়া যাচ্ছে । শ্রেণীদ্বয় A ও B পরে এসেছে
অভিপ্রয়াণ মারফত্, যেমন আফ্রিকা থেকে ইয়োরোপ
খ্রী-পূর্ব ২০,০০০ থেকে ১০,০০০ -এর মধ্যে
।
বিশদ তথ্যের জন্য
দেখুন : অবসর-স্বাস্থ্য বিভাগ, 'রক্ত অনুপ্রবেশীকরণের
কথা' ।
দ্র:
The
Discovery of Human Blood Group, www.nobelkepu.org.cn/english/life/134450.shtml
শঙ্কর
সেন
( চলবে
)