বঙ্কিমচন্দ্র
চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪ - ১৮৯৯)

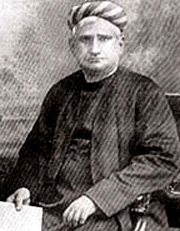 ১৮৩৮
খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জুন চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত কাঁঠালপাড়া গ্রামে
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। আইন পড়বার জন্য প্রেসিডেন্সি
কলেজে ভর্তি হন এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সেখান থেকে প্রথম বিভাগে
এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নতুন স্থাপিত
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি. এ. পরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র
দ্বিতীয় বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। আইন পড়া শেষ হওয়ার
আগেই যশোরের ডেপুটি ম্যাজিস্টেট ও ডেপুটি কালেক্টরের চাকরি পান।
তেত্রিশ বছর সরকারি চাকরি করার পর ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর
বঙ্কিমচন্দ্র অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ এপ্রিল
তাঁর মৃত্যু হয়।
১৮৩৮
খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জুন চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত কাঁঠালপাড়া গ্রামে
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। আইন পড়বার জন্য প্রেসিডেন্সি
কলেজে ভর্তি হন এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সেখান থেকে প্রথম বিভাগে
এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নতুন স্থাপিত
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি. এ. পরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র
দ্বিতীয় বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। আইন পড়া শেষ হওয়ার
আগেই যশোরের ডেপুটি ম্যাজিস্টেট ও ডেপুটি কালেক্টরের চাকরি পান।
তেত্রিশ বছর সরকারি চাকরি করার পর ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর
বঙ্কিমচন্দ্র অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ এপ্রিল
তাঁর মৃত্যু হয়।
বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন দীর্ঘ
নয়, তারই মধ্যে তাঁর সাহিত্য সাধনা বিস্ময়কর। হুগলি কলেজে ছাত্র
জীবনে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনার আদর্শে 'সংবাদ প্রভাকরে'
ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' গদ্য, পদ্য লিখতেন। ৪২ বছরের সাহিত্যসাধনা
তাঁর ছাত্রজীবন, কর্মজীবন, শেষজীবন পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। 'দুর্গেশনন্দিনী'
উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাহিত্য জীবনের আরম্ভ। এই উপন্যাস
দিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র এক নতুন দিগন্ত খুলে ধরলেন। বাঙালীর রোমান্টিক
সত্তার এক নতুন জাগরণ ঘটলো বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার তিনটি উপন্যাস
দিয়ে- 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫ খ্রী), 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬ খ্রী),
এবং 'মৃণালিনী' (১৮৬৯ খ্রী)।
বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যযুগের
রচনায় দেখা যায় সৌন্দর্য ও লোকশিক্ষার মিলন। শেষ যুগে লোকশিক্ষার
প্রাধান্য। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার শেষ পর্যায়ে পূর্ণভাবে প্রকাশ
পেল স্বাদেশিকতা ও অনুশীলন ধর্মের ব্যাখ্যা। দেশের রাষ্ট্রীয়,
জাতীয়, ধর্মীয়, সামাজিক ও শিক্ষামূলক উন্নতির সব রকম প্রয়াসে
তিনি অবিরাম লেখনী চালনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র কেবলমাত্র সাহিত্যিক
বা লেখক নন, উপরন্তু তিনি যুগস্রষ্টা। ঐতিহাসিক, রোমান্টিক,
পারিবারিক - এই তিন ধারায় উত্সারিত বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যানগুলি
সমসাময়িক ও পরবর্তী সাহিত্য ও জীবনের ওপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার
করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে এইখানে ক্লিক
করুন।
ব্যাঙ্গ করে বেশ কিছু হালকা
লেখাও বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন। এযুগের পাঠকরা সেগুলি কতটা উপভোগ
করবেন বলা শক্ত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চিন্তাধারা, রুচি
ও মূল্যবোধের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এই মন্তব্য নীচের লেখাটি
সম্পর্কেও প্রযোজ্য। এটি বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন দেশে যেভাবে
আইন যেভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়, সেই কাঠামোটি বজায় রেখে। লেখাটি
পাঠিয়েছেন পুষ্পেন্দুসুন্দর মুখোপাধ্যায়।(প্রথম পর্বের লেখাগুলি
ইউনিকোড-এ তোলা হয় নি। হরফ ফন্টে সেগুলি দেখতে চাইলে
এইখানে ক্লিক করুন।)
দাম্পত্য
দণ্ডবিধির আইন (৩)
CHAPTER
VII
OF OFFENCES RELATING TO THE ARMY AND NAVY
19. The
Army and Navy shall, in this code, mean the sons and the daughters
and daughters-in-law.
20. Whoever abets the commiting of mutiny by a son or a daughter
or a daughter-in-law shall be liable to be punished by scolding
and tears and lamentations.
সপ্তম অধ্যায়
পল্টন এবং নাবিকসেনা সম্বন্ধীয়
১৯ ধারা। এ আইনে পল্টন
অর্থে ছেলের দল। নাবিক সেনা ঝি (এবং)বৌ।
২০ ধারা। যে স্বামী, পুত্র বা কন্যা বা বধুকর্তৃক গৃহিণীর প্রতি
বিদ্রোহিতার সহায়তা করিবে, সে তিরস্কার ও রোদনের দ্বারা দণ্ডণীয়
হইবে।
CHAPTER
VIII
OF OFFENCES AGAINST DOMESTIC TRANQUILITY
21. An assembly of two
or more husbands is designated an unlawful assembly if the
common object of such husbands is,
First, To drink as defined by law or to gamble or to commit
any other matrimonial offence,
Secondly, To overawe by show of authority (to) their wives
from exercise of the lawful authority of such wives,
Thirdly, To resist the execution of a wife's order.
22. Whoever is a member
of an unlawful assembly shall be punished by imprisonment
with hard words and shall also be liable to contemptuous silence
or to scolding.
OF DRINKING WINE AND SPIRITS
23. Any liquid kept in a bottle and taken in a glass vessel
is wine and spirits.
24. Whoever has in his possession wine and spirits as above
defined is said to drink.
EXPLANATION.
He is said to drink even though he never touches the liquid
himself.
25. Whoever is guilty
of drinking shall be punished with imprisonment of either
description within the four walls of a bed-room during the
evening hours and shall also be liable to scolding.
OF RIOTING
26. Whoever shall speak
in an ungentle voice to his wife shall be guilty of domestic
rioting.
27. Whoever is guilty of domestic rioting shall be punished
by contemptuous silence or by scolding or by tears and lamentations.
অষ্টম অধ্যায়
গৃহমধ্যে শান্তিভঞ্জনের অপরাধ
২১ ধারা। দুই, কি তাহার
অধিক বিবাহিত ব্যক্তির জনতা হইলে যদি জনতাকারীদের নিম্নের লিখিত
কোন অভিপ্রায় থাকে তবে "বে আইনী জনতা" জনতা বলা যায়।
প্রথম। যদি, মদ্যপান করা, কি অন্যপ্রকার দাম্পত্য অপরাধ করিবার
অভিপ্রায় থাকে।
দ্বিতীয়। যদি আস্ফালন দ্বারা পত্নীদিগকে আইনমত ক্ষমতা প্রকাশ
করণে নিবৃত্ত করার জন্য ভয় প্রদর্শন করার অভিপ্রায় থাকে।
তৃতীয়। যদি কোন স্ত্রীর আজ্ঞামত কর্মের প্রতিবন্ধক হইবার অভিপ্রায়
থাকে।
২২ ধারা। যে কেহ "বে
আইনী জনতার ব্যক্তি" হয়, সে কঠিন তিরস্কারের সহিত কয়েদ
হইবে, অথবা মান অথবা তিরস্কারের সহিত দণ্ডনীয় হইবে।
মদ্যপানের কথা
২৩ ধারা। যে কোন জলবত্ দ্রব্য বোতলে থাকে এবং কাঁচের পাত্রে
পীত হয়, তাহা মদ্য।
২৪ ধারা। উক্তরূপ দ্রব্য যে ঘরে সেই মদ্যপায়ী।
অর্থের কথা
সে ঐ দ্রব্য স্বহস্তে স্পর্শ না করিলেও মদ্যপায়ী।
২৫ ধারা। যে মদ্যপায়ী সে
প্রত্যহ সন্ধ্যার পর শয্যাগৃহের চারি ভিত্তির মধ্যে কয়েদ থাকিবে
এবং তিরস্কার প্রাপ্ত হইবে।
২৬ ধারা। যে কেহ স্ত্রীর প্রতি কর্কশ স্বরে কথা কহে, সে হাঙ্গামা
করে।
২৭ ধারা। যে কেহ গৃহমধ্যে হাঙ্গামা করিবে, তাহার সাজা মান বা
তিরস্কার বা অশ্রুবর্ষণ ও রোদন।
['দাম্পতদণ্ডবিধি আইন'
(The matrimonical code) রচনাটি এখানেই সমাপ্ত; অন্ততঃ আমার
কাছে যে 'বঙ্কিম্চন্দ্র সাহিত্যসমগ্র' গ্রন্থটি আছে, তাতে এর
বেশী পাইনি।
লেখাটিতে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা ভষার যে ধরণটি ব্যবহার করেছেন,
অর্থাত্ তত্সম ও তত্ভব শব্দ, তাই রাখা হয়েছে। এর পিছনে দুটি
কারণ আছে। এক, তাঁর ব্যবহৃত সাধুভাষার বদলে চলিত ভাষায় রূপান্তর
করলে ব্যাঙ্গের স্বাদটি আলুনী হয়ে যাবে। দ্বিতীয়, আইন রচনার
কাজে এখনও সাধুভাষা থাকে সচরাচর এমন কি কিছু বিদেশী শব্দও ব্যবহার
করা হয়। এ ছাড়া, বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং অনৃতসুন্দরী দাসী মরফত ইংরাজী
তর্জমা দাখিল করেছেন; কাজেই যাঁরা দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলা ভাষা
ও সাহিত্যের সম্পূর্ণ ও সঠিক স্বাদ পান নি তাঁদের পক্ষেও বাংলা
অধ্যায়গুলির ভাব গ্রহনে কোন অসুবিধা হবার কথা নয়।
মহিলা পাঠকদের প্রতি সবিশেষ, সবিনয় ও সশ্রদ্ধ অনুরোধ তাঁরা লেখাটি
হাল্কাভাবেই নেবেন ও তাঁদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট বলে অভিযোগ
যেন না করেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে উগ্র পুরুষতান্ত্রিক ধরে নেবার
আগে বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য'- শীর্ষক প্রবন্ধের পঞ্চম পরিচ্ছেদ
পড়ে দেখতে অনুরোধ করি; এবং মনে রাখবেন 'সাম্য' প্রবন্ধ লেখা
হয়েছিল আজ থেকে 135 বছর আগে যখন সত্যই বাংলা তথা ভারতবর্ষের
সমাজ উগ্র পুরুষতান্ত্রিক ছিল এবং স্ত্রী জাতির প্রতি এইরকম
সাম্যের প্রস্তাব কল্পনাই করা যেত না, যা বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য'
প্রবন্ধটিতে দেখিয়েছেন। ইচ্ছা আছে দুটি বা তিনটি কিস্তিতে সেটি
পরিবেশন ক'রব।
- পুষ্পেন্দুসুন্দর মুখোপাধ্যায়
(আপনার
মন্তব্য জানানোর জন্যে ক্লিক করুন)
অবসর-এর
লেখাগুলোর ওপর পাঠকদের মন্তব্য
অবসর নেট ব্লগ-এ প্রকাশিত হয়।