রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ ও ধর্মচেতনা
১ – নাস্তিক রবীন্দ্রনাথ?
রবীন্দ্রনাথের ‘দিবসশেষের শেষ জাগরণ-সম’ অশীতি-বৎসর বয়সের অভিজ্ঞতা-প্রসূত প্রবন্ধ ‘সভ্যতার সংকট’-এর রেশ কাটিয়ে উঠতে পারিনি আমরা, পরবর্তীকালে জীবনানন্দের ‘অদ্ভুত এক আঁধার এসেছে এ পৃথিবীতে আজ’- এর জের তো চলছেই। ‘চতুরঙ্গ’-এর জ্যাঠামশাইয়ের মত যুক্তিবাদী মানবপ্রেমিকের দল আজও আসেন মাঝে মাঝে এই দেশে, এই ধরায়। আসেন প্রেমের বাণী নিয়ে শ্রীচৈতন্য-রামকৃষ্ণ, অহিংসার অবসান ঘটাতে বুদ্ধ-গান্ধী। আমরা তাঁদের কথা শুনি, তাঁদের পূজা করি কিন্তু শিক্ষা গ্রহণ করি না- ‘আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।’ তাই এখনও এই একবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তি-প্রগতির অভাবনীয় ঐশ্বর্যমণ্ডিত পৃথিবীতে শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসের পার্থক্যের কারণে হিংসা আর মারণযজ্ঞের তাণ্ডব অনবরত ঘটে চলেছে, ধর্মের নামে মনুষ্যত্ব হারাতে বসেছে মানুষ।
এমন মনুষ্যত্বহীন বিবেকহীনতার বিরুদ্ধে বরাবরই সোচ্চার ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে বেদনাহত হয়ে ৬৫ বছর বয়সে ধর্মের প্রতি মোহগ্রস্ত অন্ধকারের পূজারিদের উদ্দেশ্যে তিনি লেখেন-
‘ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।’
‘ধর্মমোহ’ নামক এ বিখ্যাত কবিতাটির রচনাকাল ১৩৩৩-এর ৩১শে বৈশাখ। সে বছর মার্চে হঠাৎ কলকাতায় আর্যসমাজীদের আইন অগ্রাহ্য করে মসজিদের সামনে মিছিল এনে বাদ্য বাজানোয় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা বাধে। অবশ্যই ইংরেজ সরকারের এই আইনটিও ছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, কিন্তু দাঙ্গা ছিল অনভিপ্রেত। তারপর ৮ই বৈশাখ শান্তিনিকেতনে এক ভাষণে বলেন- ‘এ কী হল ধর্মের চেহারা? এ মোহমুক্ত ধর্ম বিভীষিকার চেয়ে সোজাসুজি নাস্তিকতা অনেক ভালো। ঈশ্বরদ্রোহী পাশবিকতাকে ধর্মের নামাবলি পরালে যে কী বীভৎস হয়ে ওঠে তা চোখ খুলে একটু দেখলেই বেশ দেখা যায়।’
তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম, প্রকৃতি ও পরম ব্রহ্মের উপাসক। প্রচুর কবিতা, গান লিখেছেন সেই নিরাকার ঈশ্বরকে স্মরণ করে। আবার তিনি শেষ বয়সে লিখলেন ছোট গল্প ‘রবিবার’ (আশ্বিন ১৩৪৬)। গল্পের নায়ক ব্রাহ্মণসন্তান অভীক, নায়িকা ব্রাহ্মকন্যা বিভা। রক্ষণশীল সমাজে এই প্রেম নিষিদ্ধ। অভীক বোঝে ধর্মই মানুষকে মানুষের সঙ্গে মিলতে দেয় না। সে গোঁড়া হিন্দু বংশের ছেলে, কিন্তু নাস্তিক। রবীন্দ্রনাথ অভীকের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, ‘ধর্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভালো। তোমরা ভারতবর্ষের ঐক্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখ। কিন্তু যে দেশে দিনরাত্রি ধর্ম নিয়ে খুনোখুনি সে দেশে সব ধর্মকে মেলাবার পুণ্যব্রত আমার মতো নাস্তিকেরই।’ পরের বছর তিনি লেখেন ‘ল্যাবরেটরি’ (আশ্বিন ১৩৪৭)। সেই গল্পেরও অধ্যাপক চরিত্র নিজেকে নাস্তিক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।
তাহলে কি রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে নাস্তিক ছিলেন, না কি নাস্তিক্য-ধর্মের শ্রেষ্ঠতা মেনে নিয়েছিলেন। অথচ তাঁর লেখা অজস্র কবিতা, পূজা ও প্রকৃতি-পর্যায়ের গান তাঁর গভীর ঈশ্বর-বিশ্বাসের সাক্ষ্য দেয়। দীর্ঘ জীবনকালে তিনি অনেক দুঃখকষ্টই পেয়েছেন। তার জন্যে দায়ী করেছেন ঈশ্বরকে কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য এক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। তিনি মনে করতেন তাঁর সৃষ্টির সাধনাকে অব্যাহত রাখতে ঈশ্বর তাঁকে এভাবে দুঃখ-আঘাত দিয়ে জাগিয়ে রাখেন, তাঁর বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়। তাই তিনি লিখতে পারেন-
’তোমায় গান শোনাব। তাইত আমায় জাগিয়ে রাখ,
ওগো দুখজাগানিয়া। বুকে চমক দিয়ে তাইত ডাক।।’
প্রশ্ন ওঠে রবীন্দ্রনাথ কি জীবন-সায়াহ্নে এসে নাস্তিক হন? সারা জীবন ব্রাহ্ম ধর্মে আস্থা রেখে বার্ধক্যে এসে তিনি কি সে আস্থা হারিয়েছেন? জীবনসায়াহ্নে এসে তিনি হেমন্তবালা দেবীকে একটি চিঠিতে স্পষ্ট ভাবে লেখেন ‘ধর্মমত আমার আছে কিন্তু কোনো সম্প্রদায় আমার নেই। আমি নিজেকে ব্রাহ্ম বলে গণ্যই করি না। …আমি ধর্ম-সমাজের রকম-পরা ছাপমারাদের মধ্যে কেউ নই, রাজার দত্ত উপাধি আমি ত্যাগ করেছি, সম্প্রদায়ের দত্ত উপাধিও আমার নেই।’ (৮ই নভেম্বর, ১৯৩২)
দুরূহ প্রসঙ্গ সন্দেহ নেই। তাই এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে দেখা দরকার নাস্তিক কারে কয়?
‘নাস্তিক’ শব্দটি হালফিলের নয়, শব্দটি মৈত্রয়নী উপনিষদের সমকালীন। ভারতীয় সনাতনী বৈদিক ধর্মমতে নাস্তিক তারাই যারা বেদে অবিশ্বাসী। আবার পাণিনি বলেছেন, সে-ই নাস্তিক যে পরলোক মানে না। নাস্তিকতা নিয়ে ধর্মবেত্তারা (এবং ধর্মব্যবসায়ীরা!) বহুদিন থেকে চিন্তিত। অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে, প্রাচীনকালে দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতারা পরাজিত হলে তাঁরা শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু বুদ্ধ হয়ে জন্ম নেন পৃথিবীতে। অসুরদের মধ্যে বেদ বিরোধী তত্ত্ব প্রচার করেন বুদ্ধদেব, ফলে তারা নরকগামী হয়। অসুরের বিনাশ হয়। অবশ্য বুদ্ধকে অবতার ঘোষণা করা সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অনুমান অন্যরকম, সে অন্য প্রসঙ্গ। এই ভারতেরই চার্বাক গোষ্ঠী, আজিবিকাশ, কেশকম্বলিন, পুকূথ কাত্যায়ন, প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃত্ব বেদ ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে লড়াই করেন, হিন্দুসমাজ তাঁদের নিন্দা বা বিরোধিতা করলেও ত্যাগ করেনি। ফলশ্রুতিতে পৃথিবীতে আসেন বুদ্ধ, জৈন তীর্থঙ্করেরা- সেই অর্থে তাঁরা নাস্তিক। তবে আধুনিক পরিভাষায় নাস্তিক তারাই, যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, গীতায় কৃষ্ণকথিত ‘চতুর্বর্ণম্ ময়া সৃষ্টম্’- বর্ণবিভাজনের বিরোধিতা করে। তাই সব ধর্মেই নাস্তিকদের জন্য আর সনাতন ধর্মে তৎসহ বেদ ও বর্ণাশ্রম-বিরোধীদের প্রতি কঠোর শাস্তির বিধান আছে। বাল্মীকি রামায়ণে আছে বনগমনকালে নাস্তিক ঋষি জাবালির পরামর্শের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে রামচন্দ্র বলেন- তস্করের, নাস্তিকের আর বৌদ্ধদের কঠিনতম শাস্তি হওয়া উচিত-
’’যথা হি চৌরঃ সঃ তথা হি বুদ্ধঃ তথাগতং নাস্তিকমাত্র বিদ্ধি।
তস্মাদ্ধি যঃ শক্যতমঃ প্রজান্যং সনাস্তিকেনাভিমুখো ভুবঃ স্যাৎ।।’ (অযোধ্যাকাণ্ড ১০৯/৩৪)
জানিনা রামায়ণ রচনাকালে তথাগত বা বৌদ্ধধর্ম ছিল কিনা, হয়ত এসবই প্রক্ষিপ্ত।
(২) ধর্মচেতনার উৎস ও বিবর্তন
প্রত্যেক মানুষের সৃষ্টিকর্মের পিছনে একটি বিশেষ ভাব, চিন্তা-দর্শন, মনন ও দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে যা তার সৃষ্টিকর্মে প্রতিফলিত হয়। যিনি নাস্তিক, তার সৃষ্টিকর্মেও তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বা নাস্তিক্য চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটে। তাই রবীন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাসের মূলে যেতে হলে আগে অনুসন্ধান করা দরকার তাঁর বংশের শিকড়ের, যা তাঁর ভাবাদর্শকে গড়ে তুলেছে।
রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ আস্তিক্যবাদী ও গভীর ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন। তবে ধর্মপালনে তাঁর অনীহা না থাকলেও আচার-সর্বস্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠান তিনি সজ্ঞানে পরিহার করতেন। ভয়ে নয়, ঈশ্বরকে পেতে চেয়েছেন ভালবেসে, একান্তে, কাছের মানুষরূপে। আরও একধাপ এগিয়ে এও বিশ্বাস করতেন যে ভক্তের যতটা ভগবানকে, ভগবানের ততটাই ভক্তকে প্রয়োজন, হয়ত বা কিছু বেশি-
’তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে।।’
ঈশ্বরের কেন চাই ভক্তকে? তারও উত্তর তিনি পেয়েছেন অন্তরে, লিখেছেন তাঁর গানে-
’আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি।’
এখানে ‘কবি’ আর কেউ নয়, বিশ্বস্রষ্টা, সমগ্র বিশ্ব যাঁর রচিত এক মহাকাব্য! তাঁর সৃষ্টির রস উপভোগ করার একটি দোসর, একজন ভক্ত যে চাই, কারণ- ‘একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুইজনে।’
এসব গেল কাব্যে-গীতে প্রতিফলিত তাঁর একান্ত মনের কথা। ব্যবহারিক জীবনেও তিনি ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নানা প্রসঙ্গে বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করেছেন। এবার তাঁর ধর্মভাবনা ও চেতনার উৎস-সন্ধানে একটু প্রবৃত্ত হওয়া যাক।
রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষগণ ছিলেন উচ্চবর্ণীয় ব্রাহ্মণ। ‘ঠাকুর’ পদবি মূলে ছিল না, তাঁরা ছিলেন কুশারী। ইংরেজ আমলে রবীন্দ্রনাথের ষষ্ঠ পূর্বপুরুষ যশোহর-নিবাসী পঞ্চানন কুশারী ‘ঠাকুর’ উপাধি লাভ করেন, পরবর্তীকালে ঘটনাচক্রে যশোর ছেড়ে তৎকালীন কলকাতার গোবিন্দপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। পুত্র জয়রাম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে চব্বিশ পরগণায় আমিনের কাজ করতেন। তাঁর দুই ছেলে দর্পনারায়ণ ও নীলমণি। নীলমণি ঠাকুরের পুত্র দ্বারকানাথ। দ্বারকানাথ প্রথমে ল-এজেন্ট, পরে ব্যবসা এবং সর্বশেষে চব্বিশ পরগণায় কালেক্টরের সেরেস্তাদার হিসেবে প্রভূত বিত্ত উপার্জন করেন। অতঃপর তিনি রাজশাহী, কুষ্টিয়া, রংপুর, হুগলি, পাবনা, মেদিনীপুর ও ত্রিপুরা জেলায় বিভিন্ন জমিদারী কেনেন। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) এ বিশাল জমিদারীর অন্যতম মালিক হন। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩), সংস্পর্শে এসে তাঁর ধর্মচেতনায় আমূল বদল ঘটে এবং পরবর্তীকালে তিনি ব্রাহ্মধর্মের একনিষ্ঠ অনুসারী হন। রামমোহন বিভিন্ন ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, ইংরেজি শিক্ষা-সভ্যতা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে তাঁর মানস পরিগঠিত। শিক্ষিত হিন্দু যুবকদের ধর্মত্যাগ রোধ করার উদ্দেশ্যে রামমোহন হিন্দুধর্মের সংস্কারসাধনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বেদে ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ অর্থাৎ একেশ্বরবাদের কথা বলা হয়েছে, প্রায় একই কথা শিখ, ইসলাম ও খ্রিস্টানধর্মেও আছে। এসব ধর্ম সম্পর্কে বহুকালব্যাপী পঠন, চিন্তন আর আলোচনার পর ১৮২৮ সালে রামমোহন ব্রাহ্মমতের প্রবর্তন করেন। ব্রাহ্মমতে মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ। এর ভিত্তি স্থাপিত জ্ঞান, যুক্তি ও আধুনিক বিজ্ঞানমনষ্ক চিন্তাধারার উপর। দেবেন্দ্রনাথ-সহ সেকালের বহু শিক্ষিত জ্ঞানী-গুণী হিন্দুগণ এ মতের অনুসারী হন। তাই রবীন্দ্রনাথ জন্মসূত্রে ব্রাহ্ম।
দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষগণ উচ্চবর্ণীয় হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন। তবে বংশানুক্রমে পাওয়া ধর্ম, পিতৃধর্ম আর রবীন্দ্রনাথের স্বোপার্জিত ধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্মচেতনা যে অনেকটাই পৃথক তার আলোচনা-প্রসঙ্গে আসি। তিনি ছিলেন বিশ্বমানের প্রতিভা। জীবনে অনেক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে অনেকটা উদার দৃষ্টিতে তিনি গ্রহণ-বর্জনের ধারা অব্যাহত রেখেছেন। তাঁর মানস-জগতে কাল-বিবর্তনের সাথে সাথে অনেক কিছুই পরিবর্তিত হয়েছে, ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও বদল ঘটেছে। পিতা দেবেন্দ্রনাথ অতিশয় বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও ধর্মপালনে নিষ্ঠাবান ছিলেন। জমিদারী দেখাশুনার পাশাপাশি তিনি ধর্ম ও সমাজ-সংস্কৃতি নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করতেন। তিনি স্বগৃহে ব্রাহ্মমন্দির স্থাপন করেন এবং সেখানে নিয়মিত উপাসনা ও ব্রহ্মসঙ্গীত গাওয়া হতো। রবীন্দ্রনাথের শৈশবকাল এ ধরনের ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণের মাধ্যমেই অতিবাহিত হয়েছে। তাঁর প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠিত হয় পিতার আদর্শে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- ‘পিতৃদেবের সমস্ত কল্পনা এবং কাজ অত্যন্ত যথাযথ ছিল। ……ভুল করিব বলিয়া তিনি ভয় পান নাই, কষ্ট পাইব বলিয়া উদ্বিগ্ন হন নাই। তিনি আমাদের সম্মুখে জীবনের আদর্শ ধরিয়াছিলেন কিন্তু শাসনের দণ্ড উদ্যত করেন নাই।’ দেবেন্দ্রনাথের জীবনকালে তাঁর পরিবার থেকে ক্রমে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব বিলুপ্ত হয়ে ব্রাহ্মধর্ম আধিপত্য অর্জন করে। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজে মতভেদ সৃষ্টি হয়, কেশবচন্দ্র পৃথক ব্রহ্মমন্দির স্থাপন করেন। এসময় যুবক রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হন।


এদিকে, গোঁড়া ব্রাহ্মণসমাজ হিন্দুধর্মের বিপণ্নদশা দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদের মহিমা প্রচারে আত্মনিয়োগ করে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪) অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় ‘নবজীবন’ ও জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘প্রচার’ নামে দু’টি পত্রিকায় ব্রাহ্মধর্মের অসারতা প্রতিপন্ন করে ‘ধর্ম-জিজ্ঞাসা’ ও ‘হিন্দুধর্ম’ শীর্ষক দু’টি প্রবন্ধ লেখেন।

ফলে ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকগণ কিছুটা হতবল হয়ে পড়লেও যুবক রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচিত ‘হাস্য-কৌতুক’, ‘স্বপ্ন মঙ্গলের কথা’ ও ‘হিং টিং ছট্’ কবিতার মাধ্যমে কঠোরভাবে এর জবাব দেন। এসব তথ্যসমূহের দ্বারা সহজেই বোঝা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে শৈশবকাল থেকে যৌবন অবধি ব্রাহ্মধর্মের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মধর্ম প্রায় আড়ম্বরসর্বস্ব ও গোঁড়ামিতে পরিপূর্ণ হয়ে পড়ে, রবীন্দ্রনাথও তখন ধীরে ধীরে ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ থেকে আংশিক সরে এসে অন্য ভাবনা-চিন্তার সন্ধান শুরু করেন। ইতোমধ্যে তিনি আরও অনেক মত ও চিন্তা-দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, যার মধ্যে বৈষ্ণব, ইসলামের সুফি এবং পূর্ব বাংলার মুর্শিদি ও বাউল মতাদর্শ তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষিত করে যাদের প্রতিটাই ঈশ্বরের চেয়ে মানবতাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। সুফিবাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণও অনেকটা আজন্ম এবং পিতার কারণে। দেবেন্দ্রনাথ ফারসি কবি রুমী, হাফিজ প্রমুখের অতিশয় ভক্ত ছিলেন। পিতার আদর্শে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চিন্তায় ও তাঁর রচিত বিভিন্ন কাব্য-কবিতায় সুফিবাদের ঘনিষ্ঠ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এর থেকেই ক্রমান্বয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটে ও ধর্মীয় উদারতা প্রকাশ পেতে থাকে। শেষ জীবনে তিনি পারস্য যাত্রা করে আগ্রহসহকারে হাফিজের সমাধি দর্শন করেন, তাতে তাঁর সুফিবাদের প্রতি জীবনব্যাপী আস্থাই প্রকাশ পায়।
উপাসনালয়ের তথাকথিত পবিত্র আবেষ্টনে সর্বব্যাপী ঈশ্বরের অনুসন্ধান যে অর্থহীন, তাঁর আবাস যে বাইরে শাস্ত্রশাসন-বর্জিত উদার বসুন্ধরার বুকে, সে কথা রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে অন্তরে উপলব্ধি করেন যা নানাভাবে প্রকাশ করেছেন তাঁর বিভিন্ন রচনায়। মন্দির তাঁর মতে দেবতার বন্দিশালা, এই উপলব্ধির কথা তিনি লেখেন ‘পত্রপুট’ কাব্যগ্রন্থে-
‘‘আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায় আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।
পূজারী হাসিমুখে মন্দির থেকে বাহির হয়ে আসে,
আমাকে শুধায়, ‘দেখে এলে তোমার দেবতাকে?’
আমি বলি, ‘না।’
‘দেখ রে চেয়ে, দেবতা নাই ঘরে।’ তাই তিনি ঈশ্বরের খোঁজে মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে এসে পথে নেমে দেখেছেন-
‘তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ–
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে, ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে;
তাঁরই মতন শুচি বসন ছাড়ি আয় রে ধুলার ’পরে।’ (ধূলামন্দির)
তিনি ঈশ্বরকে খুঁজেছেন, পেয়েছেন মন্দিরের বাইরে মানুষের মাঝে, পঞ্চক হয়ে দর্ভক-শোণপ্রাংশু জাতির শ্রমজীবীদের মাঝে, ‘বসন্ত’-এর রাজা, কবি হয়ে প্রকৃতির মাঝে। ‘বনবাণী’ কাব্যগ্রন্থে ‘মধুমঞ্জরী’ কবিতাটির ভূমিকায় কবি লেখেন, ‘আমাদের দেশের মন্দিরে এ লতার ফুলের ব্যবহার চলে না; কিন্তু মন্দিরের বাইরে যে দেবতা মুক্তস্বরূপ আছেন তাঁর প্রচুর প্রসন্নতা এর মধ্যে বিকশিত। কাব্যসরস্বতী কোনো মন্দিরের বন্দিনী দেবতা নন, তাঁর ব্যবহারে এ ফুলকে লাগাব ঠিক করেছি…।’ দেবতাকে তিনি পেয়েছেন আপন অন্তরে- ’অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী / তবু সদা দূরে ভ্রমিতেছি আমি।।’ তাঁর চিত্রা কাব্যগ্রন্থের জীবনদেবতার ধারণা অন্যরকম, প্রচলিত দেবতার স্থানে নয়। এই দেবতা স্বর্গের ঈশ্বর নন, ‘হৃদিস্থিত হৃষীকেশ’ও নন। অথচ তিনি জীবের সত্তার বাইরে নেই, কবির ব্যক্তিত্বেরই অংশ। তিনি তাঁর জীবনের অলক্ষ্য-অমূর্ত চালিকাশক্তি, কৌতুকময়ী, রহস্যময়ী নায়িকা। জীবনদেবতা ও কবি উভয়ে মিলে একটি যুগ্মসত্তা, ‘অর্ধনারীশ্বর’।
স্বভাবতঃই কবির এ মনোভাব আচারসর্বস্বতার বিরোধাভাসই প্রতিপন্ন করে। ‘মানুষের ধর্ম’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,
‘আচারীরা সামাজিক কৃত্রিম বিধির দ্বারা যখন খণ্ডতার সৃষ্টি করে তখন কল্যাণকে হারায়, তার পরিবর্তে যে কাল্পনিক পদার্থ দিয়ে আপনাকে ভোলায় তার নাম দিয়েছে পুণ্য। সে পুণ্য আর যাই হোক সে শিব নয়। সেই সমাজবিধি আত্মার ধর্মকে পীড়িত করে।… আত্মার লক্ষণ হচ্ছে শুভবুদ্ধি, যে শুভবুদ্ধিতে সবাইকে এক করে।’
এরই প্রতিচ্ছবি আমরা পাই ‘অনধিকার প্রবেশ’ গল্পে, আচারনিষ্ঠ জয়কালী তাঁর পবিত্র মন্দিরে প্রাণভয়ে পলায়মান একটি নিরীহ অথচ ঘৃণ্য শূকরছানাকে আশ্রয় দেন, পশ্চাতে ধাবমান ছোটলোকদের তাড়িয়ে দিয়ে বলেন- ‘যা ব্যাটারা, আমার মন্দির অপবিত্র(!) করিসনে’।
ধর্মের সত্য রূপের যাঁরা সন্ধান করেছেন তাঁরা সবাই স্থান-কালনির্বিশেষে ধর্মকে শাস্ত্র এবং আচারসর্বস্বতার বন্ধন থেকে মুক্ত করে উচ্চ-নিচ সকলকে কল্যাণময় পথে পরিচালিত করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন, হিন্দু পুরাণ ভাগবত, হরিবংশ ও মহাভারতের গীতায় কৃষ্ণ যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন সে ধর্ম পুরোহিত-শাসিত শাস্ত্রসিদ্ধ বিধান নয়, তিনি ধর্মের আবেদন আর্য-অনার্যনির্বিশেষে সব শ্রেণীর মানুষের জন্য প্রসারিত করেছিলেন। গোপালক-সমাজের মধ্যমণি কৃষ্ণ- তাঁর ধর্ম মূলত ছিল অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের আশ্রয়স্থল। পরবর্তীকালে গৌতম বুদ্ধ এবং মহাবীর ও যিশু তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন ধর্মীয় চেতনাকে সব মানুষের কল্যাণমুখী করে তুলতে। ‘খৃস্ট’ রচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- ‘মানবপুত্র আচার ও শাস্ত্রকে মানুষের চেয়ে বড় হইতে দেন নাই……নৈবেদ্যের দ্বারা ঈশ্বরের পূজা নহে অন্তরের ভক্তির দ্বারাই তাহার ভজনা। এই বলিয়াই তিনি অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করিলেন, অনাচারীর সহিত একত্রে আহার করিলেন এবং পাপীকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহাকে পরিত্রাণের পথে আহ্বান করিলেন।’
(৩) ধর্ম ও ধর্মমোহ
রবীন্দ্রনাথ সমাজবিজ্ঞানীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করেছেন ধর্মের সর্বনাশা সাম্প্রদায়িক উৎসাহে দেশের মানুষ বারবার ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। ‘হিন্দু-মুসলমান’ প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন- ‘মানুষ বলেই যে মানুষের মূল্য সেইটিকে সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি।’ মানবপ্রেমের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই ধর্মবুদ্ধি থেকে বিচ্যুত হয় বলেই ধর্মের নামে অধর্ম মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে এক ধর্ম তখন অন্য ধর্মকে আঘাত করতে অগ্রসর হয় এবং সব ধর্মের সারকথা ‘মানবিকতা’ ভূলুণ্ঠিত হয়। এ মনোভাবকেই তিনি স্পষ্ট করে তুলেছেন ‘স্ফুলিঙ্গ’ কবিতায়-
‘যে গোঁড়ামি সত্যেরে চায় সুধায় রক্ষিতে-
যত জোর করে, সত্য মরে অলক্ষিতে।’
নিজের সাহিত্যকর্মে নিপুণভাবে ধর্মীয় মৌলবাদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ‘অচলায়তন’ নাটকের মহাপঞ্চক, ‘বিসর্জন’ নাটকের রঘুপতি, ‘মালিনী’ নাটকের ক্ষেমঙ্কর ধর্মান্ধ অপশক্তির প্রতিভূ। অন্ধকারের পূজারি এ চরিত্রগুলো বরাবরই যুক্তিবিরোধী। এ যুগের ধর্মান্ধ উগ্রবাদীদেরও একই রূপ। ‘মালিনী’ নাটকে আমরা তাই শেষ পর্যন্ত দেখি মৌলবাদী শক্তির নেতা ক্ষেমঙ্কর মৌলবাদের প্রচলিত ছকে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। ব্রাহ্মণদের দিয়ে উচ্চারণ করিয়েছে মালিনীর নির্বাসনের কথা। সুপ্রিয় প্রশ্ন তুলেছে-
‘ধর্মাধর্ম সত্যাসত্য কে করে বিচার!
আপন বিশ্বাসে মত্ত করিয়াছ স্হির,
শুধু দল বেঁধে সবে
সত্যের মীমাংসা হবে, শুধু উচ্চরবে?
যুক্তি কিছু নহে?’
মৌলবাদীরা তো যুক্তির ধার ধারে না! ‘বিসর্জন’-এর রঘুপতি, ‘অচলায়তন’-এর মহাপঞ্চক ধারেননি। এঁরা ধর্মরক্ষার নামে আরও এককাঠি এগিয়ে তঞ্চকতার আশ্রয় নিয়েছেন। রঘুপতি দেবীপ্রতিমার মুখ নিজের হাতে ঘুরিয়ে জয়সিংহকে মিথ্যাচার দিয়ে প্রভাবিত করেছেন। মহাপঞ্চক ক্ষমতার লোভে উন্মত্ত হয়ে গুরুকে অমান্য করেছেন। তাঁদের মিথ্যাচারের ফলশ্রুতি অবশ্য ভাল হয়নি, রঘুপতি হারিয়েছেন পুত্রসম জয়সিংহকে, মহাপঞ্চকের বিরুদ্ধে গেছে তাঁর সহোদর পঞ্চক।
ধর্মান্ধ প্রতিক্রিয়াশীলদের মনস্তত্ত্ব নিখুঁতভাবে উপলব্ধি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাই তথাকথিত ধর্মের নামে ছলনা ও মিথ্যাচারের অন্যায়গুলিও সহজেই বুঝতে পারেন। ‘ধর্ম’ গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করে বলেছেন, ‘ধর্মব্যবসায়ী ধর্মের স্বরচিত গণ্ডি রক্ষার্থে প্রবল উৎসাহ দেখায়, বিষয়ী নিজের জমির সীমানা রক্ষা করতেও এত উৎসাহ দেখায় না। এ গণ্ডি রক্ষাকেই তারা ধর্মরক্ষা মনে করে।’ ‘খৃস্টধর্ম’ রচনায় তিনি বলেন- ‘এই জন্যই মানুষকে সাম্প্রদায়িক খৃস্টানের হাত থেকে খৃস্টকে, সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের হাত থেকে বিষ্ণুকে, সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মের হাত থেকে ব্রহ্মকে উদ্ধার করে নেয়ার জন্য বিশেষভাবে সাধনা করতে হয়।’
যুক্তিহীন ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের কলম ঝলসে উঠেছে উপন্যাসেও। ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসের জ্যাঠামশাই জগমোহন এক অবিস্মরণীয় চরিত্র। ‘তিনি ঈশ্বরে-অবিশ্বাস করিতেন বলিলে কম বলা হয়, তিনি না-ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন।’ ঈশ্বরবিশ্বাসীর সঙ্গে তাঁর তর্কের একাধিক বিবরণ রয়েছে এ উপন্যাসে। জগমোহন বলতেন- ‘ঈশ্বর যদি থাকেন তবে আমার বুদ্ধি তাঁরই দেয়া। সেই বুদ্ধি বলিতেছে ঈশ্বর নাই। অতএব ঈশ্বর বলিতেছেন যে ঈশ্বর নাই।’ ভাইপো শচীশকে বলতেন, ‘দেখ বাবা, আমরা নাস্তিক, সেই গুমরেই আমাদিগকে একেবারে নিষ্ফলঙ্ক নির্মল হইতে হইবে। আমরা কিছু মানি না বলিয়াই আমাদের নিজেকে মানিবার জোর বেশি।’
ধর্মীয় উন্মাদনা ও উগ্র জাত্যাভিমানের বিরুদ্ধে চিরন্তন দ্রোহ রবীন্দ্রনাথের মহত্তম উপন্যাস ‘গোরা’। ভারতবর্ষ আর হিন্দুত্ববাদ সমার্থক- এমন যুক্তিবর্জিত ধারণা পোষণের মাধ্যমে জীবনের মূল্যবান সময় অপচয় করে গোরা। যে হিন্দুত্বের অহঙ্কারে গোরা গর্বিত ছিল সেই অহঙ্কার একদিন চূর্ণ হয়ে যায়। গোরা জানতে পারে সে জন্মসূত্রে হিন্দু নয়, এক আইরিশ দম্পতির সন্তান। নিজের ভুল বুঝতে পেরে পরেশবাবুকে গোরা বলেছিল- ‘আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন যিনি হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান, ব্রাহ্ম সবারই, যার মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে, কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না, যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন- যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।’
রবীন্দ্রনাথ নিজের যে বক্তব্যগুলো বার্তালাপে, বক্তৃতায় বা চিঠিপত্রে প্রকাশ করতে পারেননি, তা বেরিয়ে এসেছে তাঁর কলমে অজস্র গল্প-উপন্যাস-কাব্য-নাটকের মাধ্যমে। তবু যেন কোন ছলনাময়ী অন্তর্যামী তাঁকে দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাঁর বক্তব্য থেকে দূরে-
’এ কী কৌতুক নিত্যনূতন ওগো কৌতুকময়ী,
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে বলিতে দিতেছ কই?’ (অন্তর্যামী)
পরবর্তীকালে তিনি সঠিক ভাবপ্রকাশ করতে বেছে নিয়েছেন তাঁর গানকে, গানে গানে সব বন্ধন টুটে গেছে। ধর্মান্ধতার স্বরূপ বোঝাতে টেনে এনেছেন যিশুর প্রসঙ্গ তাঁর গানে-
’একদিন যারা মেরেছিল তারে গিয়ে, রাজার দোহাই দিয়ে-’ ……
তারপরেই প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে ঘটিয়েছেন তার বিশ্বায়ন। আধুনিক যুগের ভক্তদের অন্ধভক্তির চূড়ান্ত প্রকাশ তার পরের পংক্তিতে-
’এ যুগে তারাই জন্ম নিয়েছে আসি, এসেছে ভক্ত সাজি।’
তার পরিণাম?
’গর্জনে মিশে পূজামন্ত্রের স্বর–
মানবপুত্র তীব্র ব্যথায় কহেন, হে ঈশ্বর!
এ পানপাত্র নিদারুণ বিষে ভরা,
দূরে ফেলে দাও, দূরে ফেলে দাও ত্বরা।।’
এই কোলাহলের নামই কি আরাধনা, না কি হলাহলের বিভীষিকা? রবীন্দ্রনাথ এই উন্মত্ত খেলা থেকে বেরিয়ে আসার আবেদন রেখেছেন তাঁর গানে-
’তোমায় নিয়ে খেলেছি মোর খেলার ঘরেতে
খেলার পুতুল ভেঙে গেছে প্রলয় ঝড়েতে।’
খেলার পুতুল, তারের বীণা ভাঙলে কি গান থেমে যায়? ‘কেবল খেলা’ নয়, হৃদয়ের যোগ থাকলে, ভক্ত আর ভগবানের হৃদয়তন্ত্রী যখন এক সুরে অনুরণিত হয়, সেই তো পূজা!
’তারের বীণা ভাঙল, হৃদয়-বীণায় গাহি রে।।’
আজকের পৃথিবীতে ধর্মাশ্রিত মৌলবাদ ও স্বৈরতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের ছোবল মানবধর্মকে প্রতিনিয়ত রক্তাক্ত করছে। এর মূলে রয়েছে উগ্র ধর্মান্ধতা ও ধর্মমোহ। রবীন্দ্রনাথ ‘ধর্মমোহ’ কবিতায় এ ব্যাধি থেকে মুক্ত হওয়ার যে উপায় নির্দেশ করেছিলেন তা এ যুগেও প্রাসঙ্গিক-
‘যে পূজার বেদি রক্তে গিয়াছে ভেসে
ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে-
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক জ্বালো।’
(৪) বিশ্বাসের সংঘাত
সনাতন ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে কোন বিরোধে না গেলেও ধর্মের অপব্যাখ্যা আর অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে চিরকাল সোচ্চার ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এ বিষয়ে তিনি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিত্বদেরকেও রেহাই দেননি- সত্যের খাতিরে এ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা মনে হয়।
গান্ধীজীর সঙ্গে নিজের তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ মহাত্মাকে বলেছিলেন তপস্বী আর তিনি নিজে প্রেমিক। সেই তপস্বী আর প্রেমিক একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও বহু বিষয়ে ছিলেন ভিন্ন মতের শরিক। অসহযোগ আন্দোলন, বিদেশি কাপড় পোড়ানো, চরকা কাটা ইত্যাদি বিষয়ে যে তাঁর পূর্ণ সায় নেই, তা জোর গলায় বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসের সৎ দেশপ্রেমিক জমিদার নিখিলেশের কণ্ঠে আছে তার অভিব্যক্তি। যাকগে সেসব রাজনৈতিক ইস্যু। ওসব ছাপিয়ে সূক্ষ্ম একটা প্রশ্নে বাদানুবাদে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছিলেন তপস্বী ও প্রেমিক। ভূমিকম্প। উপলক্ষ প্রাকৃতিক দুর্বিপাক হলেও, বিরোধিতা ভাল করে চেনায় ওই দুই মনীষীকে। ধরা পড়ে দু’জনের বিশ্ববীক্ষা, যা অবশ্যই ছিল ভিন্ন। ১৫ জানুয়ারি, ১৯৩৪ দুপুর ২টো নাগাদ বিরাট এক ভূমিকম্পের শিকার হয়েছিল নেপাল এবং বিহার-সংলগ্ন ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা। ভূমিকম্পের এপিসেন্টার বা উৎস-কেন্দ্র ছিল এভারেস্টের ১০০ কিলোমিটার দক্ষিণে। কাঠমান্ডু থেকে পুর্ণিয়া-চম্পারণ হয়ে মুঙ্গের জুড়ে বিশাল ক্ষয়ক্ষতি। প্রাণহানি ১০ হাজারেরও বেশি। শুধু বিহারেই ৭ হাজার!
ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা দেখে বাপুজি বিচলিত। তা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রতিক্রিয়া? সে আরও বিচিত্র! মহাত্মা বললেন, ভূমিকম্প নাকি ঈশ্বরের শাস্তি যুক্তিবাদীর বিরুদ্ধে, নীচু জাতির প্রতি উচ্চ জাতির ঘৃণার শাস্তিস্বরূপ। তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বললেন, ‘প্রাকৃতিক ঘটনার মূলে জাগতিক কারণ ভিন্ন আর কিছু থাকতে পারে না।’ দেশের গণমানসে মহাত্মার ভূমিকা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বাড়তি সমালোচনাও জুড়লেন মন্তব্যে- ‘দেশবাসীর মনে ভয় আর দুর্বলতা থেকে মুক্তির অনুপ্রেরণা জোগানোর জন্য যাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই, তাঁর মুখের কোনও কথায় যদি সেই জনগণের মনে অযুক্তির বীজ প্রোথিত হয়, তবে আমরা ভীষণ আহত হই। অযুক্তি যার মূল উৎস, সেই অন্ধ ক্ষমতা আমাদের স্বাধীনতা এবং আত্মসন্ধান থেকে দূরে ঠেলে রাখে।’ রবীন্দ্রনাথের এ হেন সমালোচনার পরেও অবশ্য গান্ধীজী নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল। তাঁর প্রতিক্রিয়া- ‘ভূমিকম্প ঈশ্বরের খামখেয়াল কিংবা নানা প্রাকৃতিক কারণের সমাহার নয়। ঈশ্বর-প্রবর্তিত সব বিধান মানুষ জানে না।’
ভূমিকম্প ঘোর বাস্তব এক সত্য। তার পিছনে কারণ অন্বেষণে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তার আগের মতো নন, এ বার তিনি রীতিমত বাস্তববাদী এবং বিজ্ঞানমনস্ক। কেন ভূমিকম্প হয়, সে প্রশ্নে আজ শতকরা কত জন গান্ধীজীর দলে, আর কত জন রবীন্দ্রনাথের, তা বোধ করি বলে দিতে হবে না। সমস্যা অন্যত্র। ভূমিকম্পের মতো বিপর্যয়ের পূর্বাভাসদানে গান্ধীজীর দাবি মানলে কাজটা হয়ে ওঠে সহজ অথচ এক কুযুক্তির মিথ্যাচারের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে। যখনই কোথাও হবে পাপাচার, কেড়ে নেওয়া হবে ক্ষুধার্তদের মুখের গ্রাস, কিংবা হামলাকারীর আক্রমণে প্রাণ হারাবে নিরপরাধ মানুষ, তখন অত্যাচারীর দেশে নামবে বিপর্যয়, বাস্তবে যা দেখা যায় না। এ যেন যুগযুগান্ত ধরে নিরক্ষর দরিদ্র শ্রেণীকে পাপ-পুণ্যের, স্বর্গ-নরক-পরজন্মের অলীক ভীতিপ্রদর্শন করে নিজেদের অক্ষমতার দায় ঢাকতে ব্রাহ্মণ-শাসক-শ্রেষ্ঠীদের মিলিত চক্রান্তেরই এক আধুনিক রূপ। ‘ধর্মভয়’ ঘুচাতে প্রেমের বাণী প্রচার করেছিলেন শ্রীচৈতন্য, ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন রামমোহন-বিদ্যাসাগর আর রবীন্দ্রনাথ সক্রিয় হয়েছিলেন ধর্মের নামে মিথ্যাচার, ধর্মমোহ আর ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে।
রবীন্দ্রনাথের তরফে নাস্তিকের বিশ্ববীক্ষা-প্রসূত মতামতে আমাদের মনে জাগে কিঞ্চিৎ কৌতূহল। কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের। আলাপচারিতায় উঠে এসেছে এক কূট প্রশ্ন। সত্য কী? বিতর্কে আইনস্টাইন ধ্রুপদী বিজ্ঞানের ধ্বজা তুলে বলছেন, সত্য আপনা-আপনি বিরাজমান, তা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথ মানলেন না, বলেন, সত্য অনেকটাই দর্শকের রচনা। তার নিজস্ব কোন অস্তিত্ব বা ভিন্ন সত্তা নেই। এ হেন দাবি কবির পক্ষে স্বাভাবিক। তিনি যে নতুন নতুন সত্য রচনা করেন আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে। প্রসঙ্গতঃ শ্রীহট্টের কবি-গীতিকার হাসন রাজা (১৮৫৪-১৯০৬) সম্বন্ধে বৃহত্তর বিশ্বের পরিচয় ঘটান কবিগুরুই ১৯৩০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া একটি বক্তৃতায়। তারও আগে ১৯ ডিসেম্বর ১৯২৫-এ একটি অভিভাষণে তিনি প্রসঙ্গক্রমে হাসন রাজার দুটি গানের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে তাঁর দর্শন চিন্তার পরিচয় দেন। তার একটি ছিল-
‘মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমিন
শরীরে করিল পয়দা শক্ত আর নরম
আর পয়দা করিয়াছে ঠান্ডা আর গরম
নাকে পয়দা করিয়াছে খুসবয় বদবয়।’
১৯৩৬ এ রচিত কবিগুরুর এই কবিতাটির সাথে দেখুন তো এর কোনও মিল পাওয়া যায় কিনা।
‘আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চূনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠল আলো পূবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম ‘সুন্দর’,
সুন্দর হল সে।’
(৫) ব্রাহ্ম না হিন্দু? কিছু দ্বিধা, কিছু সংশয়
আগেই বলেছি স্রষ্টার সৃষ্টিকর্মের পিছনে তাঁর মতাদর্শ, চিন্তা-দর্শন, মন-মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে, তাঁর প্রতি সৃষ্টিকর্মে তা প্রতিফলিত হয়। রবীন্দ্রনাথের বিশাল ও ব্যাপক সৃজনকর্মেও তাঁর ধর্মচেতনার প্রভাব পড়বে, সেটাই স্বাভাবিক। এখন প্রশ্ন ওঠে তাঁর ধর্মবিশ্বাসে নাস্তিক্য-আস্তিক্য, হিন্দু-ব্রাহ্ম- কোন মতাদর্শের প্রভাব বেশি।
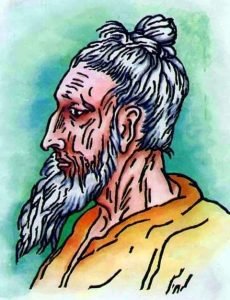
১৮৯০ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রথম জমিদারি কার্যোপলক্ষ্যে কুষ্টিয়ার শিলাইদহে এসে বাউল-সম্রাট লালন শাহ (১৭৭২-১৮৯০), ফিকিরচাঁদ ফকিরের চেলা সুনা-উল্লা ও গগন হরকরার (১৮৪৫-১৯১০) সান্নিধ্যে আসেন, যদিও লালনের সঙ্গে তাঁর চাক্ষুষ সাক্ষাৎ ঘটেনি। গ্রামীণ জনপদের অশিক্ষিত প্রতিভাবান কবিদের রচিত গানে লোকায়ত দর্শন ও জীবনচর্যা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হন। সৃষ্টিতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, আধ্যাত্মচেতনা ও গভীর জীবন-জিজ্ঞাসামূলক বাউল গানে প্রতিফলিত জীবনদর্শন কবির প্রাক্-অধীত চেতনাকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনায় বাউলের প্রভাব পরবর্তীকালে গভীরভাবে পরিলক্ষিত হয়।
১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার লাভের পর সারা বিশ্বের দ্বার রবীন্দ্রনাথের জন্য উন্মুক্ত হয়। তিনি ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্য ও দূর-প্রাচ্য, চীন-জাপানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফর করেন। সেই সঙ্গে বাংলার শ্যামলিম প্রকৃতি, ‘অবারিত মাঠ, গগনললাট চুমে তব পদধূলি’, কলকল্লোলা স্রোতস্বিনী, ভাটিয়ালি গেয়ে বর্ষার ভরা নদীতে মাঝি-মাল্লার নৌকা বেয়ে চলা, স্নিগ্ধ-শুভ্র চাঁদের আলোয় দীপ্তরজনী রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিপ্রবণ হৃদয়ে স্থান পেয়ে তাঁর জীবনতরীকে সোনার ধানে ভরে তোলে। হেগেল, ফ্রয়েড, মার্কস, ডারউইন, হাক্সলি প্রমুখ আধুনিক চিন্তানায়ক ও দার্শনিকদের যুগান্তকারী চিন্তা-চেতনার দ্বারা প্রভাবিত রবীন্দ্রনাথ নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন। তিনি জন্মসূত্রে ব্রাহ্ম, তাঁর স্বসমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হিন্দু, সে হিসাবে পূর্বপুরুষদের সনাতন আদর্শ-ঐতিহ্যের অনুসারী হিসাবে আত্মপরিচয় দেয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। তবে ইতিপূর্বে তাঁর বিশ্বাস ও আচরণে ব্রাহ্মধর্মের যে ছাপ লেগে গিয়েছিল, সেটাকেও তিনি সম্পূর্ণ বর্জন করেননি। বরং হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মধর্ম যে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অথবা সনাতন হিন্দুধর্মের পরিমার্জিত আধুনিক সংস্করণ হলো ব্রাহ্মধর্ম প্রকারান্তরে এটাই যেন তিনি বলতে চেয়েছেন। এসময় হেমন্তবালা দেবীকে লেখা একপত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেন- ‘আমি হিন্দু সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমি ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত। আমার ধর্ম বিশ্বজনীনতা এবং সেটাই হিন্দুধর্ম।’ আশ্বিন ১৩৪১ সংখ্যা ‘প্রবাসী’তে তিনি লেখেন-
‘আমি বলছি, যা কিছু মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শের সঙ্গে মেলে তাই হিন্দুধর্ম কেননা হিন্দুধর্মে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম তিন পন্থাকেই ঈশ্বরের সঙ্গে যোগের পন্থা বলেছেন। … কেননা, এতে মানুষের হৃদয়, মন, আত্মা এবং কর্মচেষ্টা সমস্তকেই ভূমার দিকে আহ্বান করেছে। আমি এই জন্যেই হিন্দু নাম ছাড়তে পারিনে, ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্ম থেকে পৃথক করতে পারিনে।’
পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ মনের দ্বিধা-সংকোচ দূর করে অনেকটা আত্মপ্রত্যয়ের সাথে বলেন-
‘আমি হিন্দু, এ-কথা বলিলে যদি নিতান্তই কোনো লজ্জার কারণ থাকে তাহলে সে লজ্জা আমাকে নিঃশব্দে হজম করিতেই হইবে।’ (আত্মপরিচয়)
রবীন্দ্রনাথের হিন্দুত্বপ্রসঙ্গে রবীন্দ্র গবেষক পরমেশ চৌধুরী বলেন-
‘বিশ্বমানবতা, আন্তর্জাতিকতাবাদ-অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি এসব কিছুর মূলই রবীন্দ্রনাথের হিন্দুত্ব। আধুনিক রবীন্দ্রসমালোচকদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এ-কথাটা ভুলে যান যে হিন্দুত্বই তাঁর ‘প্রতিষ্ঠাভূমি’, তিনি কোন নূতন মতবাদ, নূতন কোন আদর্শ প্রচার করতে চাননি। চিরন্তন হিন্দুত্বের আদর্শ বা ভারতীয় আদর্শগুলোর পুনর্জাগরণই চেয়েছিলেন তিনি, এবং নাটকে, গানে, প্রবন্ধে কবিতায় প্রচার করে যাবার চেষ্টা করেছেন যথাসাধ্য।’
শান্তিনিকেতনে প্রথম স্কুল প্রতিষ্ঠার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিন্তাধারা সম্পর্কে আচার্য জগদীশচন্দ্রের (১৮৫৮-১৯৩৭) নিকট এক চিঠিতে লেখেন-
‘শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীন কালের গুরুগৃহ বাসের মত সমস্ত নিয়ম। ধনী-দরিদ্র সকলেই কঠিন ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত হইতে হইবে। …ছেলেবেলা হইতে ব্রহ্মচর্য না শিখিলে আমরা প্রকৃত হিন্দু হইতে পারিব না।’
অবশ্য এ সম্বন্ধে সাহিত্য-সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় কিছুটা অনুযোগের সুরে লেখেন- ‘রবীন্দ্রনাথ তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরো স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ‘আমি ভারতীয় ব্রহ্মচর্যের প্রাচীন আদর্শে আমার ছাত্রদিগকে নির্জনে নিরুদ্বেগে পবিত্র নির্মলভাবে মানুষ করিয়া তুলিতে চাই। বিদেশী ম্লেচ্ছতাকে বরণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়, ইহা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিও।’ এই উক্তি থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্য ও তপোবনের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সে আদর্শে নতুন প্রজন্মের তরুণদেরকে গড়ে তোলার কাজে সচেষ্ট ছিলেন। ……তপোবন বিদ্যালয়ের কাঠামো যে সর্বভারতীয় হওয়া সম্ভব নয়, বাস্তব পরিস্থিতিতে সম্ভব নয়, তা রবীন্দ্রনাথের মনে হয়নি, অন্তত তখন মনে হয়নি। ভারতীয়ত্ব আর হিন্দুত্বকে সেদিন তিনি মিলিয়ে ফেলেছিলেন।’ (রবীন্দ্র-মানসে হিন্দুধর্ম)।
পাঠক মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করবেন, এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা করলাম, রবীন্দ্রজীবনে সবই এক-একটা খণ্ডচিত্রের মতো। এ যেন অন্ধের হস্তী-দর্শন। রবীন্দ্রনাথের বিশালত্বকে আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে মাপার চেষ্টা বাতুলতা। তবু এ যেন বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন, তিনি নিজে যেমন অনন্তের বাণী আভাসে পেতেন কান পেতে, প্রকাশ করতেন লেখনী দিয়ে, অনেকটা সেই রকম-
’…কিছু তার দেখি আভা, কিছু পাই অনুমানে-
কিছু তার বুঝি নি বা।’
(৬) পরিশেষে- আজও প্রাসঙ্গিক, ‘মানুষের ধর্ম’
(এই অংশটির রচনা আমার নয়, ঢাকার জাতীয় নাট্যশালায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান ‘ছায়ানট’-এর সভাপতি ও রবীন্দ্র–গবেষক প্রয়াত সনজিদা খাতুন নিচের প্রবন্ধটি পাঠ করেন যা এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক মনে করি।)
“‘মানুষের ধর্ম’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ মানুষের ভিতর দু’রকম ধর্মের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। প্রথমটি নিতান্ত প্রাকৃতিক তথা জৈব ধর্ম, যে-ধর্মে শারীরিক প্রয়োজনই সব। মানুষের পূর্বপুরুষ অতীতকালে চার হাত-পায়ে চলাফেরা করেছে। উবু হয়ে চলবার কালে তাদের দৃষ্টি কেবল নিচের দিকেই নিবদ্ধ থেকেছে। তার পরে এক সময়ে মানুষ যখন চলাফেরার কাজ থেকে হাত দুটো মুক্ত করে উঠে দাঁড়াতে পেরেছে, তখন তার দৃষ্টিসীমা গেছে বেড়ে। দূরকে সে প্রত্যক্ষ করেছে। আর মুক্ত হাত দুটিকে অন্য নানা কাজে ব্যবহার করতে সে অভ্যস্ত হয়েছে।
শারীরিক প্রয়োজন ছাড়াও নানা সূক্ষ্ম কাজে হাতের ব্যবহার শুরু হয়েছে এইভাবে। আদিগন্ত প্রসারিত দৃশ্য আর বিনা প্রয়োজনের কাজ মানুষকে সৌন্দর্যবোধে দীক্ষা দিয়েছিল। জীবসত্তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে মানসধর্মের জাগরণ হওয়ার ফলে প্রাণীজগতের স্বভাবধর্ম থেকে মানুষের ধর্মে উত্তরণ ঘটে মানবজাতির। এই তার দ্বিতীয় ধর্ম।
মানুষকে রবীন্দ্রনাথ চিরযাত্রী বলেছেন। মনুষ্যত্বের সারসত্তার দিকে তার নিয়ত অভিযাত্রা। যে-যাত্রার কথা রয়েছে এলিয়টের ‘দি জার্নি অব দি ম্যাজাই’ কবিতায়। পূর্বদেশীয় বৃদ্ধরা দীর্ঘ যাত্রার অন্তে তীর্থে পৌঁছে বলেছিল, ‘মাতা দ্বার খোলো’। শিশু যিশুখ্রিস্টের মতো মহামানব তথা শাশ্বত মানবের আবির্ভাব ঘটে তখন। ‘শিশুতীর্থে’র যাত্রীরাও ভয়াবহ ওঠাপড়া বাদবিসংবাদের ভিতর দিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ওই চিরমানবতার তীর্থে উপনীত হয়েছিল। ‘সভ্যতার সংকট’-এর যন্ত্রণাদীর্ণ কবিও শেষ পর্যন্ত গেয়ে উঠেছেন—
‘ওই মহামানব আসে।
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।’

চিরন্তন মানুষ হওয়ার জন্যই যাত্রা সর্বমানবের। দেশে দেশে কালে কালে মানুষ তার সাধনা দিয়ে এক অখণ্ড মানবসত্তা গড়ে তোলে। সেই সত্তা তাকে আপন আত্মা অর্থাৎ আত্মস্বরূপের উপলব্ধিতে পৌঁছে দেয়। সকল মানুষের মিলিত সাধনাতেই অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান পাই আমরা। তা থেকে মানব মূল্যবোধ তৈরি হয়ে সভ্যতার ভিত্তি পত্তন করে।
রবীন্দ্রনাথ তুলনা করে দেখিয়েছেন— মানবদেহে যেমন অসংখ্য জীবকোষের অবস্থান এবং সেগুলি স্বতন্ত্র থেকেও দেহের সার্বিক পরিপোষণে নিয়োজিত থাকে, তেমনি স্বতন্ত্র ব্যক্তি মানুষই সমন্বিতভাবে মানবসত্তা গড়ে তোলে। সেই পূর্ণের অনুভব ব্যক্তি মানুষের উপলব্ধিতে থাকে। তাই মানুষ জানতে পারে সে ব্যক্তিমাত্র নয়, বিশ্বমানবের অন্তর্গত সত্তা। এতে জাগতিক কোনো সুবিধা নেই, কিন্তু বিরাট সত্তার সঙ্গে একাত্মতার বোধ থেকে জন্মায় অহেতুক আনন্দ। এ সবই মনুষ্যত্বধর্মের পরিচয় বহন করে।
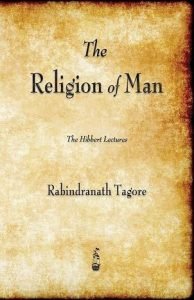 শিল্পসাধনার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান আর কর্মের সাধনা মানুষের জগৎকে ক্রমপ্রসারিত করে। সকল সাধনার ফসল মানসসম্পদ হিসেবে পরবর্তী প্রজন্মকে সমৃদ্ধ করে। বর্তমানের মানুষ যেমন পূর্বপুরুষের মানসসম্পদের উত্তরাধিকারী হয়েছে।
শিল্পসাধনার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান আর কর্মের সাধনা মানুষের জগৎকে ক্রমপ্রসারিত করে। সকল সাধনার ফসল মানসসম্পদ হিসেবে পরবর্তী প্রজন্মকে সমৃদ্ধ করে। বর্তমানের মানুষ যেমন পূর্বপুরুষের মানসসম্পদের উত্তরাধিকারী হয়েছে।
রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিসত্তাকে অহং আর ব্যক্তির ভিতরের অর্থাৎ অন্তর্গত সত্তাকে বলেছেন আত্মা। তুলনা দিয়েছেন, ব্যক্তিসত্তাকে যদি বলি প্রদীপ, তো আত্মা হচ্ছে তার শিখা। অন্তর্গত সত্তার কথা রবীন্দ্রনাথের কবিতায়-গানে ফিরে ফিরে এসেছে। গানের দৃষ্টান্ত দিই, যেখানে অন্তর্বাসী সত্তাকে জাগ্রত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন কবি—
‘মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন-’পরে—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।।’
অন্তর-সম্পদই মানুষকে মহৎ করে। আর অন্ধ ধর্মাচরণে ব্যক্তি হয়ে পড়ে অহংপ্রবণ, যেমন আমরা দেখেছি কাব্যনাট্য ‘বিসর্জনে’ রঘুপতির আচরণে। অপরপক্ষে জয়সিংহ মানবিক বিশ্বাসে স্থির থেকে প্রাণ দিয়ে প্রেমের ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করে। তখন রক্তপায়ী দেবী মূর্তিকে পরিহার করে মহৎ মানব-আত্মাকেই পুষ্পার্ঘ্য দেন কবি। ঘোষণা করেন, প্রেমধর্ম দীক্ষিত মানুষই আকাঙ্ক্ষিত মনুষ্যত্বের ধারক।
‘পত্রপুট’ কাব্যের পনেরো নম্বর কবিতাতে মানবধর্মে বিশ্বাসী পরিণতবয়সী রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য তুলে ধরছি।
‘শুনেছি যাঁর নাম মুখে মুখে,
পড়েছি যাঁর কথা নানা ভাষায় নানা শাস্ত্রে,
কল্পনা করেছি তাঁকেই বুঝি মানি।
তিনিই আমার বরণীয় প্রমাণ করব বলে
পূজার প্রয়াস করেছি নিরন্তর।
আজ দেখেছি প্রমাণ হয়নি আমার জীবনে।
…মন্দিরের রুদ্ধদ্বারে এসে আমার পূজা
বেরিয়ে চলে গেল দিগন্তের দিকে-
সকল বেড়ার বাইরে, নক্ষত্রখচিত আকাশতলে,
পুষ্পখচিত বনস্থলীতে।,…
……আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন
সকল মন্দিরের বাহিরে আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে মানবলোকে আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।’
প্রবন্ধের চেয়ে সাহিত্যে মানুষের ধর্মে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের ছাপ গভীরতর। ‘শিশুতীর্থ’ কবিতাতেও মনুষ্যত্বের জয় ঘোষণা রয়েছে। কষ্টসাধ্য দীর্ঘ মানবযাত্রায় অসহিষ্ণু মানুষ ক্রোধবশে বিশ্বাসী তীর্থযাত্রীকে হনন করে বসে। মানবতাবোধে অবিশ্বাসী হয়ে চীৎকার করে ‘পশুশক্তিই আদ্যাশক্তি’। সকাল বেলার আলোতে নিজেদের কীর্তি দেখতে পেয়ে শিউরে ওঠে নিজেরাই। ধর্মপ্রাণ পথপ্রদর্শকের দেখানো পথেই যাত্রা করে আবার। মহামানবের জন্মতীর্থে পৌঁছে ধ্বনি দেয়- ‘জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের’।
সমসাময়িক কালের যাত্রায় আজ আমরাও পৌঁছেছি অসহিষ্ণু হানাহানির পরিস্থিতিতে। হত্যা এখন তুচ্ছ বিষয়। তথাকথিত ধর্মের নামে হত্যা, স্বার্থ উদ্ধারে হত্যা, এমনকি অকারণ আনন্দের জন্যেও হত্যা! জৈব প্রবৃত্তি হয়ে উঠেছে প্রধান। পশুশক্তিই হয়েছে আদ্যাশক্তি! মানুষের ধর্মের সঙ্গে এই পরিস্থিতি সাংঘর্ষিক। আচারসর্বস্ব ধর্মতন্ত্র প্রবল হয়ে ধর্মকে কোণঠাসা করে ফেলছে ক্রমে। ‘কালান্তর’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ধর্ম আর ধর্মতন্ত্রের বৈপরীত্য নির্দেশ করেছেন বিস্তৃত ভাষ্যে। তার সামান্য অংশ উদ্ধার করি—‘ধর্ম বলে, মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও অপমানকারী কারও কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, মানুষকে নির্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁত করিয়া না মান তবে ধর্মভ্রষ্ট হইবে।…ধর্ম বলে, অনুশোচনা ও কল্যাণ কর্মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, গ্রহণের দিনে বিশেষ জলে ডুব দিলে, কেবল নিজের নয়, চোদ্দপুরুষের পাপ উদ্ধার।’
ধর্মতন্ত্রীরা প্রবল হয়ে উঠে ধর্মকে দলিত করছে আজ। হিংসার অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিশ্বের সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করে তারা ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে নেমেছে। সমগ্র বিশ্ব আজ সংকট-জর্জরিত। মানুষকে আজ মানসসম্পদে ঋদ্ধ হতে হবে। বাংলার কি-নাগরিক কি-লোকসাহিত্যে মহৎপ্রাণ কবিরা যে সব কথা বলে গেছেন, আজ তা স্মরণ করতে হবে। আস্থা রাখতে হবে তার ওপর। ‘সবার উপরে মানুষ সত্য। তাহার উপরে নাই’—চণ্ডীদাসের এই বাণী থেকে শক্তি সঞ্চয় করা জরুরি। লালন-ও গেয়েছেন—‘সর্বসাধন সিদ্ধ হয় তার, মানুষগুরু নিষ্ঠা যার’। নজরুল আবার ধর্মের চেয়েও বড়ো করে দেখেছেন মানুষকে, বলেছেন—‘মানুষ এনেছে ধর্ম, ধর্ম আনেনি মানুষ কোনো’।
অধর্মাচারী হিংসার কবল থেকে মুক্ত হবার জন্য মানুষকে আজ সত্যধর্ম আর যুক্তিবাদী চিন্তার প্রসার ঘটাতে হবে। এই হচ্ছে আমাদের অস্ত্র।”
সহায়ক গ্রন্থ ও রচনাপঞ্জি–
১) রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী
২) প্রভাত মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, বিশ্বভারতী
৩) প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, আনন্দ
৪) উজ্জ্বলকুমার মজুমদার সম্পাদিত ‘রাতের তারা দিনের রবি’, আনন্দ
৫) রানী চন্দ, গুরুদেব, বিশ্বভারতী
৬) অশোকবিজয় রাহা, প্রবন্ধসংগ্রহ, বিশ্বভারতী
৭) প্রঃ মতিউর রহমান, রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা, ইনকিলাব ২০১৭
৮) রাজীব সরকার, ধর্মমোহের যুগে রবীন্দ্রদর্শন, যুগান্তর ২০১৯
৯) ডাঃ গোলাম সামাদ, রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাভাষী মুসলমান সমাজ, দৈনিক নয়াদিগন্ত ২০১৭
১০) www.tagoreweb.in, www.amarboi.com ও অন্যান্য ওয়েবসাইট।
১১) হিমাদ্রিকুমার দাশগুপ্ত- ধর্মমোহ (প্রবন্ধ)
১২) ডাঃ সনজিদা খাতুন, ছায়ানট, বক্তৃতা- রবীন্দ্রনাথ ও মানুষের ধর্ম।
