প্রীতম বসুর - “ছিরিছাঁদ”
উপন্যাস-গ্রন্থ- ‘ছিরিছাঁদ’
লেখক- প্রীতম বসু
প্রচ্ছদ- সপ্তর্ষি দাস
ধ্রুবপদ প্রকাশনী, ২ পটলডাঙা স্ট্রীট, কোলকাতা-৯
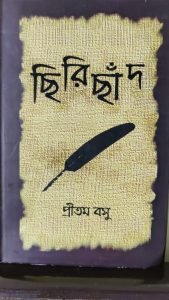
প্রবাসী যে কয়েকজন বাঙালি সাহিত্যপ্রেমী বাংলাভাষাকে ভালবেসে বাংলা সাহিত্যের সেবা ও সমৃদ্ধিসাধন করে চলেছেন সেই ঘরানার অন্যতম হলেন আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক রাজ্যের গ্লেনভিল-নিবাসী সাহিত্যিক প্রীতম বসু। এর আগে আমাদের পরিচয় হয়েছে বাংলা নেট-সাহিত্যপত্রিকা ‘অবসর’-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত সুমিত রায় ও তাঁর সহযোগী প্রয়াত সুজন দাশগুপ্তের (একেনবাবু গোয়েন্দা-খ্যাত) সাহিত্যকর্মের সঙ্গে। সুজনদার যোগ্য সহধর্মিণী নিউজার্সিবাসী শমিতা দাশগুপ্ত, শরদিন্দু-পৌত্রী ক্যালিফোর্নিয়ার তন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও বেশ কয়েকজন আমেরিকায় থেকেও বাংলায় সাহিত্য-চর্চা করে চলেছেন, তাঁদের এদেশের পাঠকমহলে পরিচিতি ও খ্যাতি বড় কম নয়। তবে দেরিতে এলেও নিজস্ব রচনাশৈলীর মাধ্যমে বাংলাপ্রেমী পাঠকমহলে রীতিমত সাড়া জাগিয়ে তুলেছেন প্রীতম বসু।
প্রীতমবাবুর প্রথম উপন্যাস ‘ছিরিছাঁদ’ প্রকাশিত হয় ২০১৩ সালে। তারপর প্রতি দুই বছরের অন্তরালে তিনি প্রকাশ করেছেন একের পর এক সাহিত্যসৃষ্টি- পাঁচমুড়োর পঞ্চাননমঙ্গল, চৌথুপীর চর্যাপদ, অন্ত্যমিলের অঙ্গনে, প্রাণনাথ হৈয়ো তুমি ও কপিলাবস্তুর কলস। এযাবৎ প্রকাশিত গ্রন্থগুলিতে তাঁর সাহিত্যের যে ধারা বা জঁর প্রকাশ পেয়েছে তা হল ভারতীয় পরিবেশে ও পটভূমিতে ইতিহাস-স্থাপত্য-সাহিত্য-লোকসংগীতের এক রহস্যময় জগতের দ্বার আধুনিক যুগের চরিত্র ও পরিবেশের মিশ্রণে পাঠকের সামনে উন্মুক্ত করা- যার স্বাদ আমরা কিছুটা পেয়েছি এককালে বঙ্কিম-রমেশ দত্ত-শরদিন্দুর রচনায়- তবে সেগুলি মূলতঃ ঐতিহাসিক ফিকশন। তার মধ্যে রহস্যময়তার স্বাদ ইদানীংকালে ইংরেজি সাহিত্যে তুমুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে ড্যান ব্রাউনের ‘দ্য ভিঞ্চি কোড’ বা ‘লস্ট সিম্বল’-এর মত উপন্যাসগুলি। তবে প্রীতমবাবুর উপন্যাস কিছুটা সমধর্মী হলেও কোনমতেই তাদের সমধারা বা অনুসরণ নয়, বরং নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বাংলাসহ এই দেশের সাহিত্য-ইতিহাস-বিজ্ঞান-সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ।
এই প্রসঙ্গে প্রীতম বসুর অন্য এক পরিচয় দিয়ে রাখি- সম্পর্কে তিনি বাংলার খ্যাতনামা ছান্দসিক কবি সুনির্মল বসুর দৌহিত্র যাঁর ‘ছন্দের টুং-টাং’, ‘ছন্দের ঝুমঝুমি’ আর ‘ছন্দের গোপন কথা’ সত্যিই ছন্দের দুনিয়ার গোপন দরজা রসিক পাঠকের কাছে খুলে দিয়েছে এককালে। ফলে কিছুটা হলেও উত্তরাধিকার-সূত্রে ছন্দের জাদু তাঁর শিরায় প্রবাহিত। ‘ছিরিছাঁদ’ গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে মহান কবিদ্বয় রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ও ছন্দ-জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে। তাই এই উপন্যাসের গোড়াতেই তোটকের ঝুমঝুমি কড়া নাড়ে কানের কাছে। শুনবেন কিছুটা?
“তব রন্ধন গন্ধতে ক্রন্দন পায়
ঝাঁঝে চক্ষুতে অশ্রু যে বর্ষা ঝরায়
এত লঙ্কা যে মাংসেতে ঢালছে কড়ায়
খেলে বাঁচবো কি শঙ্কাতে মনটা ডরায়-”
তোটকের পরিচয় কী? ০০- ০০- ০০- ০০- । দুর্বোধ্য ঠেকছে? তাহলে জানিয়ে রাখি তবলার তালের ঠেকা বা বোলের মত প্রতিটা ছন্দেরই রুদ্ধ-মুক্ত দুই মাত্রার বাইনারি কোডের পরিচিতি আছে। প্রতি একমাত্রার ‘০’ হল রুদ্ধ বা স্বরান্ত আর ‘-’ হল মুক্ত বা হসন্তযুক্ত ব্যঞ্জনান্ত। তাহলে মাত্রাবিভাগ মেনে ছড়াটা কিভাবে পড়তে হবে?
০ ০ – / ০ ০ – / ০ ০ – / ০ ০ –
ত ব রন্ / ধ ন গন্ / ধে তে ক্রন্ / দ ন পায়্ *
ছন্দের মাত্রাবিভাগের স্বরলিপির আরও কিছু রূপ এ বইয়ে এনেছেন লেখক- যেমন ভুজঙ্গপ্রয়াতের উদাহরণে –
০ – – / ০ – – / ০ – – / ০ – –
ড্যা ড্যাং ড্যাং / ড্যা ড্যাং ড্যাং / ড্যা ড্যাং ড্যাং / ড্যা ড্যাং ড্যাং
তা ধিন ধিন / তা ধিন ধিন / তা ধিন ধিন / তা ধিন ধিন
দু ধের জল / জ লের কল / ক লের গান / গা নের তাল
তা লের গুড় / গু ড়ের ভাঁড় / ভাঁ ড়ের রঙ / র ঙের হাল।
হুম! এতটা পড়েই মনে হতে পারে, আরে এ তো ছন্দের ব্যাকরণ-শিক্ষা, যা এযাবৎ বহু ছন্দ-বিশেষজ্ঞরা শিখিয়ে গেছেন বিভিন্ন রচনায়। ভাবছেন রহস্যটা কী তাহলে? আছে, আছে! পুরো গল্পটা বলে দিলে আমার এই প্রবন্ধের পাঠক ‘ছিরিছাঁদ’-এর রহস্যটা নিজে আবিষ্কার করার মজাটা পাবেন না। তবু কিছুটা আভাস দিয়ে রাখছি।
বঙ্গলেখনী পত্রিকার মালিক-সম্পাদক হাঁদু চক্কোত্তির হাতে একদিন কিভাবে যেন এসে পড়ল একটা তুলোট কাগজে লেখা পাণ্ডুলিপি যার রচয়িতা মনে হয় বেশ কয়েকজন, অথচ প্রথম পাতায় এক অজ্ঞাতপরিচয় নাম- শ্রীছন্দ। পাণ্ডুলিপির প্রতিটা পাতায় আলাদা আলাদা ছন্দের চমক, যার একটা নিদর্শন আগেই দেওয়া হয়েছে। হাঁদুর কাগজের ছন্দের-‘ছ’-না-জানা ফাঁকিবাজ গুড-ফর-নাথিং রিপোর্টার প্রণবেশ ওরফে পানুর কাঁধে চাপানো হল এই শ্রীছন্দ ও তার দলবলকে খুঁজে বের করার গুরুদায়িত্ব। হাঁদুর মতে পানুর নাকি নেড়ি কুকুরের নাক, জঞ্জাল থেকে হাড্ডি ঠিক খুঁজে নিতে পারে। কথাটা প্রশংসা না নিন্দা ধরতে না পারলেও পানু নেহাৎই চাকরি বাঁচাতে লেগে পড়ল কাজে।
পরের দিন শেয়ালদা স্টেশনের অব্যবস্থা দেখে পানুর মন্তব্য- ‘কী দুরবস্থা! কোনো ছিরিছাঁদ নেই।’ অমনি এক ময়লা ফতুয়া পরা লোক পাশ থেকে বলে উঠল- ‘ছিরিছাঁদ ছড়িয়ে আছে। শুধু চাই দেখার চোখ আর শোনার কান।’
কে এই লোকটা যে সিঙাড়াওলার ছড়া শুনে বলে ওঠে- ‘পারফেক্ট অনুষ্টুপ!’ সেটাও শোনাই, তাহলে অনুষ্টুপের মত একটা সিরিয়াস ছন্দের মজাটা ধরতে পারবেন-
”মনে গো কেন দুশ্চিন্তা ঝিমিয়ে কেন ক্লান্তিতে।
চা সিঙাড়া মনস্ফুর্তি রাখে দুদণ্ড-শান্তিতে।।”
তারপর লোকটা অনায়াসে গীতার শ্লোক- “ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে…।” আউড়ে ৪-৪-৪-৪ মাত্রা-বিভাগের অনুষ্টুপ জলের মত বুঝিয়ে দিল।
আর কথা নয়, পানু লেগে পড়ে এই ছন্দপাগল অথচ মস্ত গুণী কবির সঙ্গে। চরিত্রটি যেন সুকুমারের হ-য-ব-র-ল গল্পের ন্যাড়া আর হিজিবিজবিজের মিলিত সংস্করণ। তাই সে কখন পেটুক রামু, কখনও ছাপোষা কেরানি, কখনও বা বার্নার্ড পঞ্চাশ, কভু অসিতবরণ, ভোলা নর্তক কিংবা বীরপুরুষ সাহা। অন্তিম অবতারে তিনি নিত্য গোঁসাই। একই অঙ্গে এতো রূপ! তুখোড় ছন্দোজ্ঞ ও ছড়াকার।
কিন্তু কী তার আসল পরিচয়? সেটাই রহস্য এবং হ্যাঁ সেটাই ইতিহাস যা নিয়ে এই কাহিনি। আপনারা কি খেয়াল করেছেন যে আদি শঙ্করাচার্য, জয়দেব ও বিদ্যাপতির কিছু গীতধর্মী রচনা বাদ দিলে সংস্কৃত কাব্যে অন্ত্যমিল নেই বললেই চলে। তাহলে চর্যা-কবিদের পর বড়ু চণ্ডীদাস থেকে ভারতচন্দ্র বাংলায় অন্ত্যমিল আমদানি করলেন কোথার থেকে? সংস্কৃত ছন্দগুলির বঙ্গীয়করণই বা প্রথম হয় কার হাতে আর যিনি এর উদ্ভাবক ও প্রবর্তক সেই শ্রীছন্দ-ধারার আদিকবি শ্রীছন্দকে কারা ও কেন হত্যা করে? তাঁর ভাবশিষ্যেরা কার ভয়ে আজও পালিয়ে বেড়ান, শ্রীছন্দনিকেতন নামে এক অখ্যাত গোপন গ্রামে এক অজ্ঞাতবাসে কেন তাঁদেরকে কাটাতে হয়, ছদ্মবেশে থাকতে হয় জনসমক্ষে? লক্ষ্মণসেনের আমলে শুরু হওয়া এক সম্পূর্ণ অজানা কল্পকথার রহস্যের কিনারা আছে এই কাহিনিতে। প্রীতমবাবুর পরবর্তী রচনা পঞ্চাননমঙ্গলের মতো রুদ্ধশ্বাস না হলেও কাহিনীতে মজা আছে। সম্যক জানতে হলে বইটা পড়তেই হবে।
শেষে যা হয় হোক, এই উপন্যাসে প্রাপ্তি শুধু সেটাই নয়। গল্প ছাড়াও পুরো বইটা জুড়ে ছড়িয়ে আছে অজস্র ছড়া। অসম্ভব নিপুণতায় ছড়াগুলো নির্মাণ করা হয়েছে বিভিন্ন ছন্দে। ছন্দের দৃষ্টান্তরূপে গদ্যের মাঝে এলেও ছড়াগুলো কোথাও আরোপিত লাগে না। আর এগুলোকে মূলত ছড়া বললেও তার মাঝেই লেখক রেখে দিয়েছেন রামায়ণ, গীতগোবিন্দ, মেঘনাদবধ কাব্যের কিছু কিছু বাংলা ছন্দরূপ যা অন্যান্য ছড়াগুলোর লঘুতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।
এক বিদগ্ধ পাঠক তাঁর রিভিউয়ে লিখছেন-
“হালকা চালে শুরু হওয়া এই উপন্যাসটি এক কথায় যেন নাগরদোলায় সফর করায় পাঠককে! ছন্দের নাগরদোলা! বাংলা সাহিত্যের সমুদ্রমন্থন করে লেখক তুলে এনেছেন হারিয়ে যাওয়া, বিস্মৃতপ্রায় ছন্দ সম্ভার। শ্রীছন্দের পাণ্ডুলিপি খুঁজে বের করার এক থ্রিলারের আধারে বিভিন্ন ছন্দের ঝর্ণাধারায় অবিরাম স্নান করিয়েছেন পাঠককে। তোটক, তূণক, অনুষ্টুপ, মন্দাক্রান্তা, পঞ্চচামর, ভুজঙ্গপ্রয়াত, চম্পক, একপদী, দ্বিপদীর মত ছন্দ নিয়ে অবলীলায় পদ্য লিখে উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে সম্ভব! সংস্কৃতের কঠিন ব্যাকরণের গণ্ডিতে বাংলাভাষাকে আটকে না রেখেও ছন্দের ঢেউতে দুলিয়ে দেওয়া সম্ভব।”
বইয়ের প্রসঙ্গে আসি। ১২০ পৃষ্ঠার হার্ড-বাউন্ড বই, ওপরে পেপার জ্যাকেট। প্রচ্ছদে একটা পালকের ছবি, সম্ভবত প্রাচীন লেখনীর দ্যোতক। পটলডাঙা স্ট্রিটের ধ্রুবপদ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত, কোন এক বইমেলায় তাদেরই স্টল থেকে বইটি সংগ্রহ করি। সুন্দর বাঁধাই, সুন্দর ছাপা, সুন্দর কাগজ। মুখবন্ধ লিখেছেন শ্রদ্ধেয় কবি শঙ্খ ঘোষ। এ কাজের সবচেয়ে উপযুক্ত মানুষ। শুনেছি বইটার পাণ্ডুলিপি পড়ে শঙ্খ ঘোষ উচ্ছ্বসিত হয়ে নিজেই এই মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন।
ছিরিছাঁদে অন্ততঃ দশখানা সংস্কৃত ছন্দের গঠন ও তাদের উদাহরণ দেওয়া আছে ছড়ার আকারে। লেখক রসিক মানুষ, জানেন রস সরবরাহে ছড়ার কোন তুলনা নেই। প্রত্যেকটা ছন্দের উদাহরণে এক বা একাধিক চমৎকার ছড়া। আগেই বলেছি, বইটা শুরু হচ্ছে তোটক দিয়ে। এই সুস্বাদু তোটকের স্বাদে অন্য ছন্দগুলোও এসে গেছে একের পর এক। সংস্কৃত ছন্দগুলোর মধ্যে তোটক ছাড়া আছে মন্দাক্রান্তা, অনুষ্টুপ, তূণক, পঞ্চচামর, ভুজঙ্গপ্রয়াত, রুচিরা, মালিনী, শিখরিণী ও শার্দূলবিক্রীড়িত। এ ছাড়াও উনি নিজের মত করে সৃষ্টি করেছেন গোটা চারেক ছন্দ এবং তাদের নাম দিয়েছেন বলাকা, কল্পনা, বিপরীত মন্দাক্রান্তা আর চণ্ডী।
ছন্দের জাদুতে তিনি দাদামশাই সুনির্মল বসু আর সত্যেন দত্তেরই ধারাবাহক। অবাক করা মধ্যমিলের সাথে তাঁর তূণকের একটা উদাহরণ দিই। এই ছন্দের প্রকৃতি হচ্ছে ধিন্তাধিন্তা ধিন্তাধিন্তা ধিন্তাধিন্তা ধিন্তাধিন, প্রতি লাইনে। কী অসম্ভব নৈপুণ্যে জিনিসটা পরিবেশন করেছেন লেখক –
“ভিক্ষা ধর্ম নিত্যকর্ম অস্থিচর্ম টঙ্কা নাই
অন্নবস্ত্র মন যে ত্রস্ত শূন্যহস্ত শঙ্কা তাই
কোপ্তাকোর্মা মাংসদোর্মা রাঁধছে তোর মা গন্ধ পাই
গন্ধ সামলা নিত্য হামলা দরজা জানলা বন্ধ তাই।”
এই তূণক আর তোটক ছন্দ ভারতচন্দ্র রায় বাংলায় এনেছেন অন্নদামঙ্গল কাব্যে, যদিও তা সংস্কৃত হ্রস্ব-দীর্ঘ মাত্রার নিয়ম মেনেই। তূণকে লিখছেন-
”মৈল দক্ষ ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে।
ভারতের তূণকের ছন্দবদ্ধ বাড়িছে।।”
আর তোটক? ভারতচন্দ্রের ভণিতায় পাবেন-
”দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দ ভনে।
কবিরাজ কহে যত গৌড় জনে।।”
এসব কথাপ্রসঙ্গে এসে পড়েছে এই উপন্যাসে, গল্পের গতিকে অক্ষুণ্ণ রেখে। উল্লেখনীয় যে সংস্কৃত তোটকের অনুসরণে লেখা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের বিখ্যাত গুরুস্তোত্র “ভবসাগর তারণ কারণ হে” তারও অনেক পরে এসেছে।
অন্য সংস্কৃত ছন্দ, যাদের নাম বললাম, সেগুলোও একই ধরনের মজলিশি। আবার নিজের মতন করে ছন্দও বানিয়ে নিয়েছেন, নাম দিয়েছেন তাদের। যেমন নীচের ছড়াটার নাম দিয়েছেন বলাকা। এগুলো সব সংস্কৃত সমবৃত্ত ছন্দ, মানে প্রতি লাইনে সিলেবলের ক্রম একই রকম–
“বন্ধঘরে অন্ধভূতে রন্ধনেতে মেতে
অন্ধকারে কন্ধকাটা গন্ধে এল খেতে
গন্ধ ভাল ধন্ধ তবু ছন্দ কাটে কেন
সন্ধ্যাশেষে চন্দ্র ওঠে দ্বন্দ্ব কাটে যেন।”
এখানে আবার প্রতি পর্বে আদ্যমিল, প্রতি লাইনে তিনটে করে। আসলে পুরো ছড়াটা একই আদ্যমিলে ভরা!
হরেক রকম মিল দেওয়া প্রীতমবাবুর কাছে ছেলেখেলা, বইটাতে আছে তার অজস্র উদাহরণ। বাংলা বিভিন্ন ছন্দের স্বরূপ বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি একই মুনশিয়ানায়। এদের তালিকায় আছে বিভিন্ন রকমের পয়ার, দীর্ঘ একাবলী, একাবলী, দিগক্ষরা, একপদী-দ্বিপদী-ত্রিপদী-চৌপদী, মালতী, লাচাড়ির মত ছন্দ। সবাই জানে যে পয়ারে সাধারণভাবে চোদ্দমাত্রা প্রতি লাইনে। মালঝাঁপ পয়ারের নাম শুনেছেন, যেখানে এই চোদ্দমাত্রা ৪/৪/৪/২-এ বিভক্ত এবং প্রতি চারমাত্রায় মধ্যমিল? দেখুন তার কেমন নমুনা পেশ করেছেন তিনি–
“জটাজালে বাঘছালে চাঁদ ভালে বরে
রে কনে তোর মনে এ কেমনে ধরে
শূল হাতে ভূত সাথে চমকাতে আসে
নেই রুজি নেই পুঁজি সাপ বুঝি ডাঁসে।”
বস্তুত মিল ও হাস্যরস বস্তুটা প্রীতমবাবুর এতটাই সহজাত, যে বলার নয়। সঙ্গে আছে অনুপ্রাসের মজা।
“কঙ্কালে কুলকুচি করোটিতে ফাঁক
খটখটে খালি খুলি খাবি খায় খাক
গরু করে গাঁকগাঁক গাধাদের গীতে
ঘুণপোকা ঘাবড়িয়ে ঘামে ঘন ঘৃতে”
অথবা শুধুই চ-দিয়ে
“চিংড়ির চার চাচা চালচুলোহীন
চেন্নাই যাবে বলে চলে গেল চিন
চন্দ্রগ্রহণে করে চিল্কায় চান
চাপদাড়ি চুমে হবে চেঙ্গিস খান…”
অনুপ্রাস নিয়ে এমন ছড়া “শ্রীশ্রীবর্ণমালাতত্ত্ব” নামে এক অসাধারণ কবিতামালা লিখতে শুরু করেছিলেন সুকুমার রায়, তাঁর অকালমৃত্যুতে ‘ঝ’ পর্যন্ত গিয়ে তা থেমে যায়। রবীন্দ্রনাথের “চল-চপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ/ কোথা চম্পক আভরণ”- স্টাইলকে মাটিতে নামিয়ে এনে দেখুন চ-এর অনুপ্রাস নিয়ে কেমন চমকপ্রদ চর্বিত-চর্বণ করেছেন তিনি-
“চিকন চাদর চিকুর চাঁচর চোখা চালিয়াৎ চ্যাংড়া,
চলে চ্যাংব্যাং চিতল কাতল চলে চুনোপুটি ট্যাংরা।”
বইয়ের প্রসঙ্গে ফিরি। বাংলা ও সংস্কৃতের বিভিন্ন ছন্দ, সরস আদ্য-মধ্য-অন্ত্যমিল ও অনুপ্রাসে ভরপুর এই ছিরিছাঁদ, যা আসলে শ্রীছন্দেরই অপভ্রংশ, গল্পের আকারে বিধৃত। হারিয়ে যাওয়া শ্রীছন্দের খোঁজে ঘুরে মরছে এক সাংবাদিক, আর কী আশ্চর্য এখান থেকে ওখান থেকে পেয়ে যাচ্ছে ছন্দের মণিকণা। পেয়ে যাচ্ছে বাউলের গীতে, হকারের বিজ্ঞাপনে, মিছিলের স্লোগানে। বাংলার সম্পদ বাংলার মধ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছে সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে ইথারে, অথচ কেউ তাকে চিনতে পারছেনা।
কিন্তু সব উপেক্ষা করা যায়, যেটা পাওয়া গেল তার বিশালত্বের তুলনায়। বাংলায় সংস্কৃত ছন্দের প্রয়োগ নিয়ে ছোটখাটো প্রবন্ধ লেখা হয়েছে বিভিন্ন বইতে, মুখবন্ধে শঙ্খবাবু তার উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়াও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ‘ছন্দ-সরস্বতী’, মোহিতলাল মজুমদার, দিলীপ রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও প্রবোধচন্দ্র সেনের বাংলা ও সংস্কৃত ছন্দ নিয়ে উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু লেখা আছে। তবে সেগুলোর কোনটাই প্রীতমবাবুর ছিরিছাঁদের মত সরস রহস্যকাহিনির আকারে বিধৃত নয়, সহজপাঠ্যও নয়।
ছন্দ-পুস্তিকার তালিকায় ছিরিছাঁদ এক আকরগ্রন্থ হয়ে থাকবে বলেই আমার বিশ্বাস।
কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ
১) অমিতাভ প্রামাণিক
২) সূর্যনাথ ভট্টাচার্য
* সংস্কৃত তোটকে লেখা আচার্য শঙ্করের শিবস্ত্রোত্র “প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং” থেকে বাংলায় এই ছন্দে দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের লেখা এই বহুশ্রুত গান– “ভবসাগর-তারণ কারণ হে/ রবিনন্দন-বন্ধন-খণ্ডন হে…” সব আদি ও অকৃত্রিম তোটক, শুধু বাংলা কথায় বা পাঠে সংস্কৃত বা হিন্দির মত হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের পার্থক্য থাকেনা, তাই কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এর সরলীকরণে ড্যা-ড্যা-ড্যাং/ ড্যা-ড্যা-ড্যাং (০ ০ -/ ০ ০ -) হিসেব মত রুদ্ধ-মুক্তদলের আইডিয়া আনেন, প্রীতমবাবু তা-ই ব্যবহার করেছেন।

1 Comment