ইংরেজি রহস্য সাহিত্যে কিশোরী গোয়েন্দার সন্ধানে
মহিলা নীচু স্বরে বললেন, “সম্পত্তি ভাগের মীমাংসা এখনও হয়নি, আর ওই মেয়েরা নিশ্চিন্ত হয়ে দিন গুনছে। গত সপ্তাহে শুনলাম এডা তার বোনকে বলছে, ‘ওঃ, বুড়ো ক্রাউলির টাকাপয়সা যে আমরা পাব তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অন্য কেউ এসে সম্পত্তিতে ভাগ বসাবে, বাবাকে এই ভয় আর করতে হবে না।’”
দোকানি মহিলার পরচর্চায় ন্যান্সি যোগ দিতে চায় না। কিন্তু এই নতুন তথ্য শুনে চমকে উঠল। মিস্টার টপহাম এ বিষয়ে চিন্তিত মানে উনিও সন্দেহ করছেন জসাইয়্যা ক্রাউলি দ্বিতীয় একটা ইচ্ছাপত্র লিখে কোথাও লুকিয়ে রেখে গেছে।
(ক্যারোলাইন কিন, দ্য সিক্রেট অফ দ্য ওল্ড ক্লক)
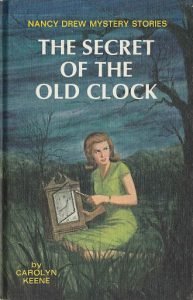
রহস্যভেদী বা গোয়েন্দা বলতে মনে ভেসে ওঠে এক সুঠাম, বুদ্ধিমান, সাহসী পুরুষের ছবি। এডগার অ্যালেন পো’র আগুস্ত ডুপ্যাঁ, কোনান ডয়েলের শার্লক হোমস, বা অ্যাগাথা ক্রিস্টির এর্ক্যুল পোয়ারো, নিদেনপক্ষে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ বক্সী, বা সত্যজিৎ রায়ের প্রদোষচন্দ্র মিত্র, ওরফে ফেলুদা। এঁরা নিজেদের কর্মদক্ষতা আর ক্ষুরধার বুদ্ধির বলে নানান জটিল সমস্যার চটজলদি সমাধান করে ফেলেন – তা কাল্পনিক হলেই বা। সঙ্গে একজন সহকারী থাকলেও আসলে পুরুষ গোয়েন্দাই সর্বেসর্বা। অবশ্য সেই সহকারীও পুরুষ।
গোয়েন্দা কাহিনিতে নারীর ঐতিহাসিক স্থান অপরাধের শিকার হিসেবে। কোনো সুন্দরী মহিলাকে রক্ষা বা উদ্ধার করতেই গল্পের অবতারণা। মাঝেমধ্যে নারীকে অবশ্য অন্য একটি ভূমিকাতেও দেখা যায় – মোহময়ী ভ্যাম্প। তার কাজ রহস্যভেদীর সঠিক অনুসন্ধানের পথে বাধা সৃষ্টি করা। তবে সেই প্রচেষ্টা হয় সাময়িক এবং শেষ পর্যন্ত বিফল। গল্পের সমাপ্তিতে এসে খলনারী তার কু-কাজের উপযুক্ত শাস্তিও পায়। এই দুই ভূমিকা ছাড়া রহস্যকাহিনিতে নারীর আত্মপ্রকাশের দৌড় কোনো পুরুষ চরিত্রের মা, বোন, প্রেমিকা, বা বৌ হয়ে। প্রতিটি ভূমিকাই সাধারণত নগণ্য – এগুলি ছেঁটে দিলেও গল্পের কোনো ইতরবিশেষ হয় না।
রহস্য কাহিনিতে নারীচরিত্রের এই অবস্থান অধুনালুপ্ত বললে ভুল হবে। একবিংশ শতাব্দীতে এসেও গোয়েন্দা গল্পের মুখ্য চরিত্রে, অর্থাৎ গোয়েন্দার ভূমিকায়, নারীর আনাগোনা সহজ হয়নি। আধুনিক লেখকদের মনে মহিলা গোয়েন্দার রহস্যভেদের ক্ষমতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ রয়ে গেছে। পুরুষ লেখকের কথা না হয় বাদই দিলাম, মহিলা লেখকরাও এর ব্যতিক্রম নন। অথচ ইংরেজি সাহিত্যের রহস্য ও গোয়েন্দা রচনা ধারায় মহিলা লেখকের অন্ত নেই। সেক্ষেত্রে আশা করা যেতেই পারে মহিলা লেখক পাঠককে নারী গোয়েন্দা চরিত্র উপহার দেবেন। তা কিন্তু সবসময় ঘটেনি। ইংরেজি সাহিত্যে মহিলা লেখকের কলম থেকেই জন্ম নিয়েছে তাবড় তাবড় পুরুষ রহস্যভেদী – এর্ক্যুল পোয়ারো (অ্যাগাথা ক্রিস্টি), লর্ড পিটার উইমসি (ডরোথি সেয়ার্স), অ্যালবার্ট ক্যাম্পিয়ন (মার্জারি অ্যালিংহ্যাম), রডেরিক অ্যালেন (ন্যেও মার্স), অ্যাডাম ডাগলিস (পি.ডি. জেমস), এবং রেজিনাল্ড ওয়েক্সফোর্ড (রুথ রেন্ডেল)।
অথচ গোয়েন্দা গল্পের আদিকাল থেকেই মহিলা লেখকেরা রহস্যকেন্দ্রিক গল্প-উপন্যাস লিখে চলেছেন। ডিটেকটিভ ধারার জনক হিসেবে এডগার অ্যালেন পো সর্বজনস্বীকৃত হলেও অনেকের মতে সেই খেতাবটি পাওয়া উচিত ছিল ক্যাথারিন ক্রো-এর। পো-এর প্রথম গোয়েন্দা উপন্যাস, দ্য মার্ডার্স ইন দ্য রু মর্গ (১৮৪১) প্রকাশ হবার কয়েক মাস আগেই ক্রো-এর উপন্যাস, দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ সুসান হপলি, অর সার্কামস্ট্যানসিয়াল এভিডেন্স, আত্মপ্রকাশ করেছিল। তবে সমাজে পুরুষ আধিপত্যের ফলে তৎকালীন নারীর এই সাফল্য উপেক্ষিত হয়েছিল। এখন অবশ্য অনেক গবেষক ভুলটি সংশোধন করার চেষ্টা করছেন।
তবে পো-এর সমর্থকেরা বিপরীত যুক্তি দেন। তাঁদের মতে, সময়ের দিক থেকে দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ সুসান হপলি আগে লেখা হলেও একে ঠিক গোয়েন্দা কাহিনি বলা যায় না। এটি আসলে রোমান্টিক, প্রেমের গল্প। উপন্যাসের নায়িকা, সুসান হপলি, বহু ভয়ঙ্কর সমস্যার মোকাবিলা করেছেন ঠিকই, কিন্তু তা নিজের প্রেমিককে কাছে পাওয়ার তাগিদে। শুধুমাত্র একটি রহস্য সমাধানের জন্যে তিনি অনুসন্ধান চালাননি। শুধু তাই নয়, একটা পর একটা যুক্তি সুষ্ঠুভাবে সাজিয়ে সমস্যার নিষ্পত্তিও তিনি করেননি। অথচ এই দুটিই হল গোয়েন্দা গল্পের স্বাক্ষর। অতএব পো’কে গোয়েন্দা গল্পের জন্মদাতা পদ থেকে সরানো চলবে না। এই নিয়ে বিতর্ক মুলতুবি রাখাই ভালো। তবু যেন মনে হয় পাঠকমহলে মহিলা গোয়েন্দাদের যতটা পরিচিতি এবং স্বীকৃতি পাওয়া উচিত ছিল, তা তাঁরা পাননি।
বিংশ শতকে এসে ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্যে মহিলা রহস্যভেদীর আনাগোনা বেড়েছে। এঁদের মধ্যে অ্যাগাথা ক্রিস্টির সৃষ্টি মিস মার্পল আর টাপেন্স, এ.এ. ফেয়ারের বর্থা কুল, স্যারা পরেটস্কির ভি.আই. ওয়াসাওস্কি, স্যু গ্র্যাফটনের কিন্সি মিলহোন, অ্যালেকজান্ডার ম্যকল স্মিথের প্রেশাস রামোৎসওয়ে, অ্যানি হোল্টের হ্যানে উইলহেল্মসেন, এবং প্যাট্রিসিয়া কর্নওয়েলের কে স্কারপেটা প্রখ্যাত। বেশির ভাগ পুরুষ গোয়েন্দা-নায়কের মত এঁরা প্রাপ্তবয়স্ক, সক্ষম, ও যুক্তিবাদী। তবে প্রায় প্রতি অভিযানেই মহিলা বলে এঁরা কিছু বিশেষ বাধার সম্মুখীন হন। শারীরিক শক্তিতে গুণ্ডা অপরাধীদের সঙ্গে পেরে না উঠলেও, বন্দুকবাজী এবং বুদ্ধির মারপ্যাঁচে এঁরা এগিয়ে থাকেন। মার্শাল আর্ট শেখার দৌলতে ইদানীং অনেক মহিলা গোয়েন্দা অবশ্য মারদাঙ্গাতেও পিছিয়ে নেই। সমসাময়িক পুরুষ গোয়েন্দা চরিত্রের মত এঁরা পাঠকসমাজে নন্দিত কিনা তা ভেবে অবশ্য লাভ নেই।

গল্পের জগতে পুরুষ গোয়েন্দা চরিত্রের পাশাপাশি কিশোর গোয়েন্দারও আবির্ভাব ঘটেছে। ১৮৬০-এর দশকে, ‘অর্নেস্ট কিন’ নামে এক কিশোর রহস্যভেদী চরিত্রকে কেন্দ্র করে, ‘পেনি ড্রেডফুল’ সিরিজের মধ্যে দিয়ে এই ধারার প্রবর্তন। ১৮৮৭ সালে, কোনান ডয়েলের উপন্যাস, এ স্টাডি ইন স্কারলেট-এ নায়ক শার্লক হোমস-এর জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে প্রথমবার সামনে আসে ‘বেকার স্ট্রিট ইররেগুলার্স’ নামে এক দল পথ-কিশোর গোয়েন্দা। এরা অবশ্য গল্পের মুখ্য অনুসন্ধানকারী নয়। তবে শার্লক হোমসের তিনটি অভিযানে এদের উপস্থিতি রয়েছে।
এরপর থেকে স্কুল-ছাত্র গোয়েন্দা নিয়ে বহু গল্প-উপন্যাস লেখা হয়েছে। উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনে কিশোর অভিযানের গল্প খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ১৯২৭ সালে, হার্ডি বয়েজ’ কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই ধারার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। হার্ডি বয়েজের জনপ্রিয়তা এখনও অক্ষুণ্ণ। ইদানীং কিশোর গোয়েন্দাদের মধ্যে খ্যাতি পেয়েছে ‘এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রাউন’ (ফ্র্যাঙ্কলিন ডিক্সন, সম্মিলিত ছদ্মনাম), ‘থিয়োডর বুন’ (জন গ্রিসাম), ‘ডায়মন্ড ব্রাদার্স ডিটেকটিভ এজেন্সি’ (অ্যান্টনি হরোউইৎজ), এবং ‘জন মিলটন’ (মার্ক ডসন)।
স্বল্পবয়সীদের জন্যে লেখা যুগান্তকারী উপন্যাস, দ্য ওয়ান্ডারফুল উইজার্ড অফ অজ-এর রচয়িতা, এল. ফ্র্যাঙ্ক বম, লিখেছেনঃ
অনেক লেখক ভাবেন শিশুদের জন্যে গল্প লিখলে তা শিশুর জীবন-কেন্দ্রিক হতে হবে। ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল। বহু ক্ষমতাবান লেখকের কাছে শৈশব একটি মধুর স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে – সময়ের প্রবহমানতায় ঘটনাগুলো আবছা আর আবেগের গোলাপি রঙে রাঙানো। কোনো শিশুর জীবনই আসলে তেমন শান্ত আর সুন্দর নয়। তাই সে ধরনের গল্প তাদের পড়তে ভালো লাগে না। শিশুদের দিতে হবে এমন টানটান গল্প যা তাদের জীবনে উত্তেজনা এনে দেয়, তাদের বুদ্ধি প্রসারিত করে। কিশোরীদের হাতেও ন্যাকা ন্যাকা বই তুলে দেবার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ নেই।
(হোয়াট চিলড্রেন ওয়ান্ট, এল. ফ্র্যাঙ্ক বম, ১৯০২)
এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মানতেই হয় গোয়েন্দা কাহিনি কিশোরীদের পক্ষেও উপযুক্ত। সেই ভাবনা থেকেই অ্যানা ক্যাথরিন গ্রিন লিখলেন প্রথম কিশোরী গোয়েন্দার অভিযান, দ্য গোল্ডেন স্লিপার অ্যান্ড আদার প্রবলেমস ফর ভায়োলেট স্ট্রেঞ্জ (১৯১৫)। গ্রিনের নায়িকা, কিশোরী ভায়োলেট, একটি উচ্চবিত্ত পরিবারের মাতৃহীন কন্যা। নিজের বাবার অজান্তে সে গোয়েন্দাগিরি করে অন্যের সমস্যার সমাধান করে এবং উপার্জন করে। নিজের চিন্তাশক্তি আর বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে সে সচেতন এবং নিঃসংশয়। তার উদ্দেশ্য শুধু সমস্যার যুক্তিপূর্ণ সমাধান নয়, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ। টাকার জন্যে প্রতিমুহূর্তে কারোর কাছে হাত পাততে সে চায় না। গ্রিনের বইয়ের বৈশিষ্ট্য হল, লেখায় উল্লিখিত প্রতিটি আইনি তথ্য সঠিক। এ বিষয়ে লেখক খুবই সজাগ ছিলেন।
এদিকে ছেলেদের জন্যে রহস্যগল্প ও লোমহর্ষক অভিযানের জনপ্রিয়তা ক্রমাগত বেড়েই চলল। এবারে আরম্ভ হল মেয়েদের জন্যে কিশোরী গোয়েন্দা কেন্দ্রিক কাহিনির দাবি।
১৯১৬ সালে, এল. ফ্র্যাঙ্ক বম সৃষ্টি করলেন একটি অল্পবয়সী কিশোরী ডিটেকটিভ চরিত্র – মেরি লুইজ। উদ্ধত আর খামখেয়ালি বলে মেরি লুইজের প্রথম সংস্করণ প্রকাশকেরা অনুমোদন করলেন না। অর্থাৎ মেয়েদের ভাবমূর্তির সঙ্গে মেরি লুইজ খাপ খায়নি। ফলে ফ্র্যাঙ্ক বম সেই চরিত্র বেশ কিছুটা সংযত করলেন। পরে বম ছাড়াও বহু নামী অনামী লেখক ঐ একই নামের ছাতার আড়ালে মেরি লুইজকে পুষ্ট করেছেন। বইগুলি হালকা নীল কাপড়ে বাঁধাই হত বলে সিরিজটি “দ্য ব্লুবার্ড বুকস” নামে বিখ্যাত হয়েছিল। এর কিছু পরেই আরম্ভ হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধের চাহিদা মেটাতে পশ্চিমে নারীর সামাজিক ভূমিকা গেল পাল্টে। এই পরিবর্তিত সমাজে মেরি লুইজের কর্মক্ষম, স্বাধীনচেতা চরিত্র গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল। এর কিছু পরেই বম আরও একটি কিশোরী গোয়েন্দা চরিত্র সৃষ্টি করলেন – জোসি ও’গোরম্যান। শক্তপোক্ত জোসি মধ্যবিত্ত পরিবারের কন্যা – তার বাবা গুপ্তচর। জোসি বাকচতুর, সাহসী, অনমনীয়। সে যুদ্ধপরবর্তী যুগের নব্যকন্যা। এই চরিত্রটিও কিছুদিনের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল।
এতেও স্বল্পবয়স্ক পাঠক মহলের তৃপ্তি হল না। তাদেরই দাবিতে, কিশোরী ডিটেকটিভ ন্যান্সি ড্রু-কে নিয়ে ১৯৩০ সালে আরম্ভ হল একটি যুগান্তকারী সিরিজ – ন্যান্সি ড্রু মিস্ট্রিজ। ১৯৩০ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সিরিজটি একটানা প্রকাশিত হয়েছে। কয়েক বছরের বিরতির পর সিরিজটি আবার চালু করা হয়েছে। ন্যান্সি ড্রু চরিত্রটি প্রকাশক এডওয়ার্ড স্ট্র্যাটেমায়ারের মস্তিস্কপ্রসূত; কিন্তু ন্যান্সির পূর্ণাঙ্গ রূপ গড়ে তোলে এডওয়ার্ডের কন্যা, সম্পাদক হ্যারিয়েট স্ট্র্যাটেমায়ার অ্যাডামস। এই সিরিজের প্রথম তিরিশটি বই লিখেছেন মিল্ড্রেড ওয়ার্ট বেনসন। পরে ক্যারলিন কীন ছদ্মনাম গ্রহণ করে বহু লেখক ন্যান্সি ড্রু-এর অ্যাডভেঞ্চার লিখে হাত পাকিয়েছেন। তথ্যে অনেক ভুল থাকলেও মূল ইতিবাচক বার্তা – মেয়েদের ক্ষমতায়ন – কিশোরী ন্যান্সির মাধ্যমে সিরিজটি সমাজে পৌঁছে দিতে পেরেছে। তবে সেদিনের লেখা বইয়ে বর্ণবিদ্বেষের যে ইঙ্গিত রয়েছে, আধুনিক পাঠক তা সহ্য করবে না বুঝে, বইগুলির পরিমার্জনা করে নতুন সংস্করণ প্রকাশের কাজ চলছে।
এরপর, বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে এসে এনিড ব্লাইটন পাঠকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন পাঁচবন্ধুর একটি গোয়েন্দা দল – দ্য ফেমাস ফাইভ। দলটিতে দু’জন মেয়েও রয়েছে। প্রথম উপন্যাস, ফাইভ অন এ ট্রেজার আইল্যান্ড (১৯৪২)। আশির দশকে ব্রিটিশ লেখক, ফিলিপ পুলম্যান, সৃষ্টি করলেন স্যালি লকহার্ট নামে ষোল বছর বয়সের একটি অনাথ কিশোরী গোয়েন্দা। লকহার্ট-এর প্রথম আবির্ভাব দ্য রুবি ইন দ্য স্মোক (১৯৮৫) উপন্যাসে। স্যালির বাবা তাকে বহু বিদ্যায় দক্ষ করেছেন – বন্দুক চালানো, অঙ্ক, অর্থনীতি। সিরিজের চারটি বই-ই ঐতিহাসিক ভিক্টোরিয়ান সমাজের প্রেক্ষাপটে লেখা। সেই নারী বিদ্বেষী সময়েও স্যালি হিসেবরক্ষক হিসেবে চাকরি করেছে।
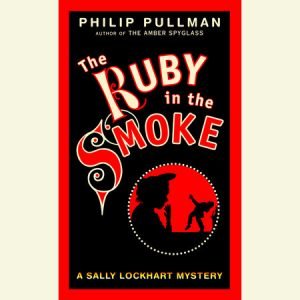
২০০৬ সালে ন্যান্সি স্প্রিংগার পাঠককে উপহার দিলেন একটি অভিনব কিশোরী গোয়েন্দা চরিত্র – এনোলা হোমস। চোদ্দ বছরের এনোলা তার দুই বিখ্যাত দাদা, শার্লক এবং মাইক্রফট হোমসের চেয়ে বয়সে অনেক ছোটো – তাদের কাছে প্রায় অপরিচিত। এনোলার মা হঠাৎ গৃহত্যাগ করে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর, দুই দাদা বোনকে নিয়ে কী করবে ভেবে না পেয়ে বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করে দিল। সেই স্কুল থেকে পালিয়ে আরম্ভ হল মা’কে খুঁজে পাবার জন্যে এনোলার অভিযান। ২০০৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত এনোলাকে নিয়ে ছ’টি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে।
একবিংশ শতাব্দীতে এসেছে আরও কিছু কিশোরী গোয়েন্দা চরিত্র। তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম করছি – কাজুকো জোন্স (শ’না হোলিওক), শার্লি বোনস ও জামিলা ওয়াহিদ (জিলিয়ান গের্স), ক্যান্ডিস মিলার (ভ্যারিয়ান্স জনসন)। এই চরিত্ররা প্রত্যেকেই কিছু অভিনব ক্ষমতার অধিকারী এবং তারা দৈহিক শক্তিও ধরে। কিন্তু এদের সবচেয়ে বড় দুটি গুণ হল বুদ্ধি ও সাহস।
প্রাপ্তবয়স্ক রহস্যভেদীর পাশাপাশি ইংরেজি সাহিত্যে কিশোরী-কিশোর গোয়েন্দার উপস্থিতি আজকাল যথেষ্ট অনুভব করা যায়। গল্পের ধারা অনুযায়ী এই স্বল্পবয়স্ক গোয়েন্দারা রহস্য সমাধানে খুবই পটু। কিন্তু এই কমবয়সী সত্যানুসন্ধানীদের বয়স সংক্রান্ত কিছু বিশেষ বাধার সম্মুখীন হয়। সেগুলোই একটু খুঁটিয়ে আলোচনা করি।
১) সাধারণত প্রাপ্তবয়স্ক অপেশাদারি রহস্যভেদীরা খুবই দক্ষতার সঙ্গে অনুসন্ধান চালান, কিন্তু অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে বা যথাযথ সাজা দিতে হলে শেষ পর্যন্ত তাঁদের পুলিশ বা অন্য কোনো আইনস্বীকৃত কর্তাব্যক্তির শরণাপন্ন হতে হয়। তাতে অবশ্য বিশেষ সমস্যা নেই। তাৎক্ষণিক কিছু অসুবিধে হলেও সঠিক প্রমাণ এবং ব্যাখ্যা পুলিশ বা কর্তাব্যক্তির কাছে পেশ করলে এঁরা সমস্যা সমাধানের স্বীকৃতি পান। অল্পবয়স্ক রহস্যভেদীর ক্ষেত্রে এই বাধাই হয়ে দাঁড়ায় প্রায় অলঙ্ঘনীয়। কিশোর-কিশোরীর কথা শুনবে কে, বিশ্বাস করবে কে! শুধু তাই নয়, একটি ছোটো ছেলে বা মেয়েকে তার সন্দেহ, যুক্তি, এবং চিন্তাধারা প্রাপ্তবয়স্ক কর্তাব্যক্তির কাছে খুব সাবধানে তুলে ধরতে হয়। কল্পনাপ্রবণতা ও মিথ্যে বলার অভিযোগ তাদের প্রতি খুব সহজেই আনা চলে। আবার তেমন নীতিজ্ঞানবর্জিত ব্যক্তি হলে তদন্ত ও সমাধানের কৃতিত্ব সে নিজেই বাজেয়াপ্ত করে নিতে পারে।
২) বেশিরভাগ অপ্রাপ্তবয়স্ক গোয়েন্দাকে তার তদন্ত চালাতে হয় লুকিয়ে – শুধু অপরাধীর থেকে নয়, অভিভাবকদের কাছ থেকেও। এই জন্যেই বহু কমবয়সী গোয়েন্দারা হয় অনাথ, নয় বোর্ডিং স্কুলের অধিবাসীতে পরিণত হয়। অর্থাৎ নির্দ্বিধায় কাজ করতে হলে বাবা-মা এবং অন্যান্য গুরুজনদের আওতার থেকে দূরে, তাদের তদারকি বা নাগালের বাইরে থাকতে হয়। মেয়েদের বেলায় সামাজিক অনুশাসন এবং পরিবারের খবরদারি ছেলেদের চেয়ে অনেক গুণ বেশি। ফলে তদন্তের পক্ষে যা অতি প্রয়োজনীয়, দিনেরাতে বাধাহীন যাতায়ত, তাদের পক্ষে খুবই কঠিন।
৩) একজন অল্পবয়সী সত্যসন্ধানীর পক্ষে প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষী বা অপরাধীকে জেরা বা জিজ্ঞাসাবাদ করা সম্ভব নয়। ফলে কিশোর-কিশোরী গোয়েন্দাকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয় পরোক্ষে – অন্যের কথোপকথন কান পেতে শুনে অথবা দরজায় আড়ি পেতে। তাই, অধিকাংশ স্বল্পবয়সী গোয়েন্দাগল্পের কেন্দ্রে থাকে লোমহর্ষক অভিযান, জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে অনুসন্ধান নয়।
৪) লুকিয়ে অনুসন্ধানের আরেকটি ভয়ও থাকে – অপ্রত্যাশিত দৈহিক বিপদ। প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীর সঙ্গে শারীরিক সংঘাতে লিপ্ত হলে অল্পবয়সী গোয়েন্দার হেরে যাবার সম্ভাবনাই বেশি। তাছাড়া যেহেতু সে বয়স্কদের কাছ থেকে লুকিয়ে তদন্ত করছে, তার গতিবিধি পুলিশ বা মা-বাবার জানার কথা নয়। ফলে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তাকে রক্ষা করার কেউ থাকে না। তাই, সমস্যা সমাধানে কিশোর-কিশোরী গোয়েন্দার শারীরিক শক্তির ওপর নির্ভর না করে নিজের ও বন্ধুদের বুদ্ধিমত্তার ওপর ভরসা করতে হয়।
৫) কিশোর-কিশোরী গোয়েন্দা সাহিত্যে অপরাধের ব্যপ্তিও সীমিত। নৈতিক কারণে, ছোটোদের রহস্যগল্পে ভয়ঙ্কর খুন, জখম, রাহাজানির সমস্যা আনা চলে না। তার বদলে ছোটোখাটো চুরি, অপহরণ, আর অন্যান্য রহস্যময় সমস্যার সমাধান নিয়েই কমবয়সী গোয়েন্দাদের ব্যস্ত থাকতে হয়। এর দু’একটা ব্যতিক্রম অবশ্য আছে।
সাহিত্যে কিশোরী রহস্যানুসন্ধানীর অভাব নিয়ে পাঠকমহলে, বিশেষত নারীবাদীদের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ রয়েছে। কিন্তু কেন? বইয়ের পাতায় কাল্পনিক চরিত্র দু’চারটে কম থাকলেই বা কী! আসলে আমরা এখন জানি, যা কল্পনায় ধরতে পারি না, যা চোখে দেখতে পাই না, তা বাস্তবে পরিণত করা মুশকিল। মেয়েরা কী পেশার উপযুক্ত, সেই সামাজিক ধারণা থেকে কিশোরীদের জন্যে বৃত্তি বাছা হয়, বিদ্যালয়ে তাদের পাঠ্যক্রম স্থির করা হয়। একটা উদাহরণ দিই। আমার ছোটবেলায় ভারতের বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে মেক্যানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিঙের দরজা মেয়েদের জন্য বন্ধ ছিল। ফলে মেক্যানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে হলে যে প্রস্তুতির প্রয়োজন, মেয়েদের পাঠ্যসূচিতে সে সব বিষয় রাখা অবান্তর ধরে নেওয়া হত। এমন মনোভাবের জন্যে আরও কত বিষয় যে মেয়েদের আয়ত্তের বাইরে থেকে যেত, কে জানে! সেই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই, তবুও সব বাধা সরে যায়নি। বুঝতে হবে, শুধু প্রাতিষ্ঠানিক নিষেধ নয়, মানুষের মনের দ্বিধাও এ ব্যাপারে বিশাল বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আর সেই দ্বিধার জন্ম হয় আমাদের সংস্কৃতিতে কী সম্ভব বা সম্ভব নয় তা উপলব্ধি করে।
গোয়েন্দা পেশায় খুব কম সংখ্যক মহিলা এবং কিশোরীর প্রবেশ আরও একটি ক্ষতির ইঙ্গিত আনে। গোয়েন্দাবৃত্তির মূলে রয়েছে বুদ্ধি, যুক্তি, ও সাহস। সমস্যা সমাধানের এই তিনটিই চাবিকাঠি। প্রায় প্রতিটি সমাজেই ধরে নেওয়া হয় মেয়েদের মধ্যে বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তির প্রয়োগ কম। তারা আবেগপ্রবণ, যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণে দক্ষ নয়, এবং তারা ভীরু। খানিকটা সেজন্যেই গোয়েন্দাকাহিনিতে নারীর প্রাধান্য কম। রহস্যগল্পে কিশোরী গোয়েন্দার অনুপস্থিতিও সেই একই কারণে। এই ধারণা ভ্রান্ত কি না, সে বিতর্ক এখানে নিষ্প্রয়োজন। বাস্তবে প্রয়োজন মেয়েদের দক্ষ করে গড়ে তুলে তাদের পুরুষের সমান সুযোগ দেওয়া। সত্যি যদি আমরা জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠা করতে চাই, তাহলে অবশ্যই জীবন ও সংস্কৃতির আনাচে কানাচে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের একই কাজে একই ভাবে টেনে আনতে হবে।
———-
তথ্যসূত্রঃ
Eccleshare, J. (2014, January 6). “Beyond Sherlock: Are there any good detective novels for teens?” The Guardian. Available: https://www.theguardian.com/childrens-books-site/2014/jan/06/book-doctor-sherlock-detective-novels-teens
Murphy, S. G. (2016, March 8). “The secret history of the girl detective.” Smithsonian Magazine. Available: https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/secret-history-girl-detective-180958311/
Young, S. (2001). The simple art of detection: The female detective in Victorian and contemporary mystery novels. MFS Modern Fiction Studies, 47, 448-457.
ছবি অন্তর্জাল থেকে সংগৃহীত।
ইংরেজি উদ্ধৃতির অনুবাদঃ লেখক।

1 Comment