পাঠপ্রতিক্রিয়া: 'কোথায় পাবো তারে'
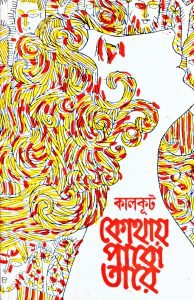
পাঠপ্রতিক্রিয়া: ‘কোথায় পাবো তারে’
লেখক: কালকূট
এমন সব উতল চৈত্র দিনে, নবশ্যামল মুকুলগন্ধী বনের হাওয়া যখন বল্লরী আর্দ্রতা নিয়ে আকাশের নিদাঘ শুষ্কতা ছুঁতে চায়, মায়ানির্ভর জীবনের নিভৃতে কী যেন এক নির্মোহ টান, পাতা ঝরে, মায়া ঝরে, মাথার ওপরে টুপটাপ ঝরে মাখনরঙা শাল ফুলের রেণু; মধ্য রাতের স্বচ্ছ আকাশে জোৎস্নার ঢেউ, ’ও চাঁদ,তোমায় দোলা দেবে কে!’… প্রেমকাব্য নয়, বিরহক্লিষ্ট ব্যথার উন্মন নয়, নির্দিষ্ট কোনও বিশেষ নরনারীর জীবনঋদ্ধ আখ্যান, ঘটনার ঘনঘটায় যা অলস মস্তিষ্ককে সজাগ করে, তাও নয়! বরং মদালসা মন চায় বিশেষ কিছু পড়তে, যার অক্ষরে অক্ষরে লেখা থাকে এমন কোন গানের বৈরাগ্য, ’সুখ নয় সে, দুঃখ সে নয়, নয় সে কামনা’…
আলগোছে হাতে এসে পড়ে লাল হলুদ রেখায় এলোমেলো অবয়বের প্রচ্ছদ আঁকা কোনও একটি বই। প্রচ্ছদে নাম লেখা ‘কোথায় পাবো তারে,’ লেখক কালকূট (সাহিত্যিক সমরেশ বসু নন), এবং প্রচ্ছদশিল্পী প্রখ্যাত চিত্রকর পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রকাশক বাংলার প্রথম শ্রেণীর প্রকাশনা সংস্থা আনন্দ পাবলিশার্স।
সেকালের নিরিখে সব কিছুই অতি বিখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও এমন সাদামাটা প্রচ্ছদ কেন? সচেতন মনে এ প্রশ্ন আসেই। উত্তর খুঁজতে গিয়ে পাতা উল্টোতে উল্টোতেই চোখে পড়লো তৃতীয় পাতার উৎসর্গ পত্রে লেখকের স্বর্গতঃ পিতার নাম। তবে কি এই আখ্যায়িকায় লেখক তাঁর তৎকালীন খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা দূরে সরিয়ে ছুঁতে চেয়েছেন একাকী নির্জন সেই নিরুপায় মানুষটিকে?
দেশভাগের গ্লানি ও ভয়াবহতা যাঁকে দরিদ্র করেছে, নষ্ট শৈশব যাঁকে তথাকথিত সুবোধ বালক হতে দেয়নি, প্রথম যৌবনেই বয়সে বড় এক অনন্যার কূলপ্লাবী প্রেম ও দাম্পত্যে ঋদ্ধ হয়েও তাঁকে ছেড়ে পরবর্তী প্রণয়ে জড়িয়ে পড়ার অপরাধবোধ যাঁকে আজীবন নিরন্তর ব্যথিত করেছে, বামপন্থী রাজনীতির মতাদর্শে দীক্ষিত হওয়ার জন্য যাঁকে পেশা ও সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে জেলবন্দী পর্যন্ত হতে হয়েছে, কালকূট ছদ্মনাম গ্রহণ করে যাঁকে ‘ভোটদর্পণ’ ও সমকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ ট্রাভেলগ ‘অমৃত কুম্ভের সন্ধানে’ লিখতে হয়েছে, জন্ম শতবর্ষের দোরগোড়ায় পৌঁছনো কালজয়ী সাহিত্যিক – ইনি কি সেই তিনিই?
আগ্রহ বাড়ে, পাতা ওল্টাতে হয়, নিবিড় পাঠে মনোযোগ আসে, রুদ্ধশ্বাস আগ্রহে শেষ হয়ে যায় সাতশো ছিয়াত্তর পাতার আখ্যান।
পাতায় পাতায় চিত্রায়িত নানা রঙের, নানা পেশার মানুষ, তাদের নিত্যনিধি জীবন এবং যাপন। দেখতে আলাদা, কিন্তু সবই যেন অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা। গাজির ডুপকির ডুপ্-ডুপ্ শব্দের তালে তালে এই নিত্য ঘূর্ণায়মান জীবন দোলায় নায়কের সঙ্গে দেখা হয় অধর মাঝি, শিক্ষক ব্রহ্মনারায়ণ, গোপীদাস, অবনী, লিলি, রমা, ঝিনি, আঙরি, দুলি, যোগিনী, মাতৃময়ী পরিশীলিতা অলকা, সন্দীপ, নারায়ণ – আরও কত জনের সঙ্গে। বাউলের নিরাসক্ত গানে গানে, তন্ত্রসাধনার রহস্যময়তার ঘোরে, রূপোপজীবিনী হয়েও নারীত্বের দুরন্ত অহংবোধে (দুলি), গ্রাম্য জটিলতায়, নিতান্ত সাধারণী নানীর সহজ ভালোবাসায় যে যার মতো রাঙিয়ে দিয়ে যায় আমাদের মনন মাটি। নদী দিয়ে বয়ে যায় জল – ইচ্ছামতী – কলোকল, ছলোছল, আপন গতির ছন্দে। ধুয়ে মুছে যায় সবকিছুই। আবার নতুন গান, নতুন গল্প, নতুন কুশীলব। তারই মধ্যে নায়কের স্বীকারোক্তি, “মানুষ চেনার বড়াই যেন কখনও না করি…”
বাস্তবিক অর্থে জীবন তো সত্যিই এক বহতা নদী, সময়ক্রম তার ডিঙি। একটা গোটা জীবন জুড়ে মানুষ জন্ম-মৃত্যুর মধ্যবর্তী উৎস থেকে মোহনা যাত্রাপথে অযুত অভিজ্ঞতার নুড়ি কুড়িয়ে কুড়িয়ে পেরিয়ে যায় এই অনাদি পথ। পথে দেখা হয় কত বন্ধু, কত নদী, কত অরণ্য, মর্মর বনবীথির সঙ্গে।সুখে-দুঃখে, পতনে-উত্থানে, জীবন পেরিয়েও অমূল্য, চিরায়ত মাধুরীতে যা মুগ্ধ করে মানুষকে বারংবার।
প্রতীক্ষাকাতর, শুভেচ্ছামধুর আর্তিতে সেসব গাথাই লিখেছেন কালকূট তাঁর এই উপন্যাসে।
স্বভাবসিদ্ধ অপরূপ বাঙ্ময় ভাষাভঙ্গি, প্রকৃতির অনুপুঙ্খ রূপচিত্রণ, মানবচরিত্র বর্ণনায় অদ্ভুত স্বাতন্ত্র্য – যা তাঁর অপরাপর লেখায় দেখা যায়, তার সবকটিই এখানেও উজ্জ্বল। তবু বারংবার পাঠের পরেও মনে হয়, অন্যান্য রচনার চাইতে ‘কোথায় পাবো তারে’ সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী।
কারণ, এই লেখায় কোনও নির্দিষ্ট পটভূমি নেই, নির্দিষ্ট গল্প নেই। কোনও নির্দিষ্ট কালখণ্ডের ব্যাখ্যাও নেই। নদী – যা চিরটা কাল ব’য়ে যায় মানুষের মনে এবং প্রকৃতির বনে, তার স্রোতের চলিষ্ণুতায় ফেলে আসা শৈশব, মধ্যজীবনের চাওয়া পাওয়ার আদিগন্ত প্রান্তর এবং লাল কাঁকরের স্তব্ধতায় ধূসর যন্ত্রণাময় প্রৌঢ়ত্ব; এই সব নিয়েই ইতস্তত সঞ্চারমান একটি পথপাগল পথিকের অবিচিত্র মাধুকরী এ রচনার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। বাংলার নিজস্ব বাউলের মতো, মুর্শিদী গানের ঝোলা নিয়ে কথক গাজীর এ-মেলা, সে-মেলা, আন-গাঁ, ভিন-গাঁ ভেসে যাওয়া, হেঁটে যাওয়া পায়ে পায়ে ধুলো উড়িয়ে, সেই ধুলোয় ধূসর হতে হতে সেই ছোট্ট ছেলেটির জীবনভ’র ডিঙি বাওয়া… এক অবিকল্প অরূপের সন্ধান আমাদেরও উদাস করে উপন্যাসের শুরু থেকেই।
যদিও ভিন্ন আঙ্গিক, ভিন্ন বোধ, তবু মনে পড়ে ইংলিশ সাহিত্যের স্রষ্টা পুরুষ চসারের ‘ক্যান্টারবেরি টেলস’-এর কথা।
এও যেন তেমনই এক মাটি ছোঁওয়া রূপকথা, সমাজের প্রতিটি স্তরের, প্রতিটি মানুষের কথা। যেখানে প্রেম আছে, মায়া আছে, তরুণ তরুণীর পারস্পরিক আকর্ষণ আছে, সাহিত্য প্রীতি আছে, ব্যবসায়িক দ্বন্দ্ব আছে, প্রকৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনও আছে। সর্বোপরি আছে লেখকের আত্মানুসন্ধান এবং আত্মবিনির্মাণের অভীক্ষা।
ইটিন্ডা, মলুটি, ইচ্ছামতীর গাঙে, আদাড়ে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো শৈশব কী যে ভীষণ মায়ায় তাঁকে আকর্ষণ করেছে আজীবন! মাহাতো এবং মাহাতো-বৌয়ের দাম্পত্যে কীভাবে যেন এসে পড়েছে তাঁর আপন দাম্পত্য মাধুরী! জ্ঞানে বা অজ্ঞানে তা আমাদের অনিঃশেষ মুগ্ধ করে। আবার সাধু হয়ে যাওয়া পিসেমশাইয়েরও পিসিমা ও সন্তানদের প্রতি পারস্পরিক টান কি লেখকের নিজেরই পরবর্তী জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে না?
এমনই ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা মণিমুক্তো, অসংখ্য বাউল গানের পংক্তি দিয়ে সাজানো এই আখ্যায়িকা তাই তাঁর অন্যান্য বহুপঠিত এবং বিখ্যাত সৃষ্টিগুলির চাইতে পৃথক বই কী!
তারও মধ্যে মন ছুঁয়ে যায় ব্রহ্মনারায়ণের চরিত্রের ছদ্মগাম্ভীর্যের মধ্যেও হার্দিক উদারতা, গাজীর প্রাজ্ঞতা, অধর মাঝির সরল রসময়তা, হঠাৎ হঠাৎ উঁকি দিয়ে যাওয়া বিশ্বাসমশাই, পালমশাই, এবং তাঁদের বিষয় বুদ্ধির কথা।
তবু একেবারে শেষে,যখন পড়ি,
“আমি ঝিনির দিকে ফিরি। ঝিনি অসহায় করুণ চোখে তাকায়। আবার জিজ্ঞেস করে, ‘আবার কবে কোথায় দেখা হবে?’
একটু চুপ করে থেকে বলি, ‘বলতে পারছি না যে।’
‘কেন।’
‘জানি না যে!’
ঝিনির ঠোঁটের ফাঁকে অস্পষ্ট শব্দ বাজে, ‘বিষ।’
সত্য মাঝি গম্ভীর গলায় ডাক দেয়, ‘বাবু আসেন, ভাঁটা পড়েছে।’
ঝিনির দিকে তাকাই। ঝিনি আমার বুকের দিকে চোখ রেখে বলে, ‘যদি না জানো, তবে কেমন করে বলবে। তবে আর কোথায় দেখা হবে। তবু দেখ-।’
ওরা গলা বন্ধ হয়ে আসে। বলি, ‘বল ঝিনি।’
ও ভাঙা ভাঙা নিচু গলায় বলে, ‘বলি, বলি, বলবই তো। তবু দেখ নিতান্ত মেয়ে তো আমি। তাই একটা কথা জানতে ইচ্ছে করে।’
‘বলো।’
‘মনে থাকবে, আমাকে?’
‘থাকবে।’
যেন সাপের ছোবলে ঝিনি আর্তনাদ করে ওঠে, ‘উঃ, কী ভীষণ বিষ। মনে হয় অমৃতের মতো গলায় ঢেলে দিই, দিয়ে জুড়িয়ে যাই। তবে, একটা কথা।’
আবার ও থামে।
বলি, ‘বলো।’
‘মনে থাকুক না থাকুক, আমি বলি, একটু মনে রেখো।’
আমার বুকের কাছে জামাটা একবার ধরে আবার ছেড়ে দেয়। আমি নেমে যাই ঘাটের
দিকে। যাবার আগে আবার বলি, ‘যাই।’
ও বলে, ‘আমি আর একবার নয়নতারার কাছে যাই।’
ওর এই শেষ কথাটা যেন, সহসা কেমন এক তীব্র ভয়ংকর সুরে বেজে ওঠে। যেন মনে হয়, নয়নতারা আর ঝিনি, একাকার হয়ে গিয়েছে। তারা দু’জনে এক।
ও পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সত্য বাউল নোঙর তুলে নৌকা ঠেলে দেয় জলে।”
দূরে পড়ে থাকে জীবন জুড়ে পাওয়া সমগ্র ঐশ্বর্যের দান। কী প্রগাঢ় প্রেমানুভবে, কী নির্বিকল্প অন্তর্লীনতায় আমরা একাকার হয়ে যাই নিরাকার সর্বংসহা এক পবিত্র জীবনবোধে।
প্রকৃত সাহিত্যের সংজ্ঞা যদি হয় লোকশিক্ষার সঙ্গে আনন্দ বিধান, কালজয়ী সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গি যদি হয় মহাকালের পারিজাতটিকে পরম মমতায় ছুঁয়ে প্রাত্যহিকতার শিউলি ঘ্রাণে যাপন উৎসবে সার্থকতা দান, তবে অবশ্যই সমরেশ বসু, না না, কালকূট তাঁর এই ব্যতিক্রমী আখ্যানটিতে সে কর্মে সফল। দুই হাতে তাঁর কালের মঞ্জিরা, হৃদয় ভরে গেছে মারণ হলাহলে, যুগযন্ত্রণার সুখবেদনা এবং ব্যথার মাধুরী তবু মহাদেবের মতোই কণ্ঠে ধারণ করে আমরণ যিনি দিয়ে গিয়েছেন সমাজকে অমৃত, তাঁর নাম কালকূট না হয়ে অন্য কী-ই বা হতে পারে! তাঁর রচনায় সেই পরম পুরুষ অথবা পরমা প্রকৃতির অন্বেষণ তাই চির কাঙ্খিত, “আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না…”
**অবসর গ্ৰুপের ইভেন্টে পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখা
