আনন্দমেলায় ‘কুন্তক’ – আমাদের শিক্ষক
কিছুদিন আগেই প্রয়াত হয়েছেন আমাদের বাংলা ভাষার এক প্রবাদপ্রতিম লেখক, শ্রী শঙ্খ ঘোষ। কবিরূপে তিনি খুবই জনপ্রিয়, তা ছাড়া তাঁর আর একটি পরিচয়ও সাধারণের কাছে বেশ পরিচিতি পেয়ে আসছে। সেটি হল, তিনি দীর্ঘদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। আমিও যাদবপুরের ছাত্র তবে কারিগরি বিভাগের। আমার বহু পরিচিত মানুষকে জানি যাঁরা তাঁর ছাত্র ছিল, আমার নিজের দিদিই তাঁদের একজন।
বারংবার তাঁদের কাছে শুনেছি তাঁর অনির্বচনীয় শিক্ষাদানের কথা। ঈর্ষান্বিত হয়েছি। আরো বেশি করে হয়েছি, যখন জেনেছি শ্রী শঙ্খ ঘোষ যাদবপুরে কারিগরি বিভাগেও এককালে আবশ্যিক বাংলার ক্লাস নিয়েছিলেন। তা অবশ্য আমাদের সময়ের (১৯৭৯–৮৩) বেশ কিছু বছর আগে। আমাদের সহপাঠী সুকন্যা, গীতি সংসদে গান গাইত। সেখানে তাদের একটি গীতিনাট্যের ভাষ্য রচনা করেছিলেন স্বয়ং শঙ্খ ঘোষ। তাঁর শিক্ষাদানের মধ্যেও তাঁর সুমধুর সরস স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যেত। আমার দিদির কাছে শোনা একটি ঘটনার উল্লেখ করতে পারি।
বাংলার এম এ ক্লাসে শঙ্খ ঘোষ স্পেশাল পেপার পড়াতেন – ‘রবীন্দ্রনাথ।’ প্রথম ক্লাসে তিনি ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করছিলেন, কেন তারা ‘রবীন্দ্রনাথে’ আকৃষ্ট। সবাই নিজেদের মত করে সাজিয়ে গুছিয়ে উত্তর দিচ্ছিল, একজনই শুধু অকপটে বলে ফেলেছিল – ‘ভাষাতত্ত্ব (অন্য স্পেশাল পেপার) ভীষণ শক্ত, তাই।’ শঙ্খ ঘোষ দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন – “কোথাও কিছু না পেয়ে লোকে বাংলা এম এ পড়ে, তার মধ্যেও অন্যকিছু না পেরে রবীন্দ্রনাথ। হা হতোস্মি!”
আরো মজার ঘটনা শুনেছি আমাদের পরিচিত একটি ছেলের কাছে। এটা আরো কিছুদিন আগের ঘটনা – সম্ভবত সত্তর দশকের শেষের দিকে। এক বৃষ্টির দিনে ছাত্রদের সংখ্যা কম থাকায় ছাত্রদের উপরোধ, অনুরোধে তাঁকে তাঁর শিক্ষক জীবনের কিছু ঘটনার কথা বলতে হয়েছিল। তখন শুনিয়েছিলেন এক ভারি মজার ঘটনা।
তখনও যাদবপুরে আসেননি, শিক্ষকতা করছিলেন অন্য কোনো কলেজে। এমনি এক বৃষ্টির দিনে ক্লাসে গিয়ে দেখেন অল্প কিছু ছেলে এসেছে। তাদের নিয়েই ক্লাস চালাচ্ছিলেন, হঠাৎ দমকা হাওয়া আসাতে দরজা খুলে গেল। একটি ছাত্র গিয়ে দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে দিলে আবার ক্লাস শুরু হল। কিছুক্ষণ পরেই, আবার দরজায় শব্দ – টকটক। সম্ভবত কেউ এসেছে। কিন্তু মুশকিল হল, কোনো সাধারণ মানুষ দাঁড়িয়ে টোকা দিলে যে উচ্চতা থেকে আসা উচিত, আওয়াজ আসছে তার বেশ কিছু উপর থেকে। সকলেই বেশ আশ্চর্য! ব্যাপারটা কী? শিল পড়ছে নাকি? সাহস করে একটি ছেলে গিয়ে দরজা খুলতেই অবাক কাণ্ড! ক্লাসে ঢুকে পড়েছে একটি লোক, মাথায় মুটের ঝাঁকা। সেই ঝাঁকাতে বসে সেই ক্লাসের একটি ছাত্র! সকলেই হৈচৈ করে উঠলো, উঁচুতে টোকার আওয়াজ পাওয়ার ব্যাপারটিও পরিষ্কার হল। ছেলেটি জানালো সে কলেজে আসতে গিয়ে দেখেছে সামনের বেশ কিছুটা জায়গা একদম জলে ভর্তি হয়ে গেছে, তার পক্ষে কিছুতেই আসা সম্ভব নয়। কিন্তু বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে ক্লাস তাকে করতেই হবে, কোনক্রমে রাস্তায় একটি মুটেকে ধরে ক্লাসে হাজির। শঙ্খ ঘোষ জানিয়েছিলেন, তাঁর দীর্ঘ ছাত্র ও শিক্ষক জীবনে তিনি ওই একবারই কোন ছাত্রকে মুটের মাথায় ক্লাসে আসতে দেখেছিলেন।
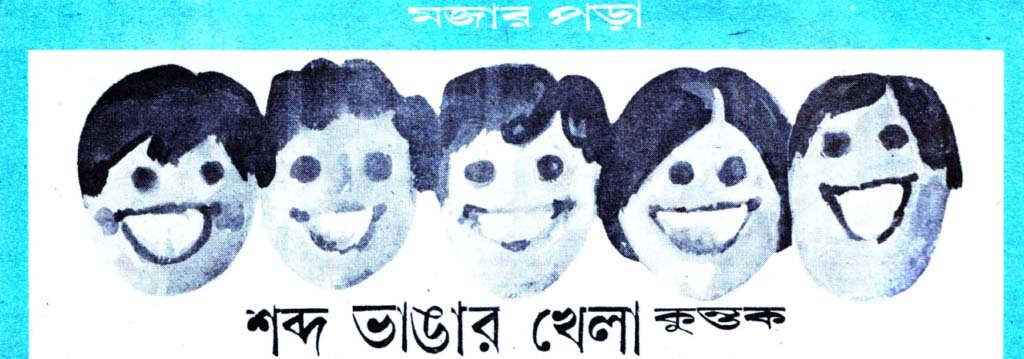
তবে তাঁর ক্লাস আমিও করেছি। স্বনামে নয়, বেনামে। আনন্দমেলা পত্রিকা মাসিক প্রকাশিত হতে শুরু করে ১৯৭৫ সালে, আর পরের বছর ১৯৭৬ সালেই তাতে আসে একটি নতুন বিভাগ – মজার পড়া। লেখকের নাম – কুন্তক। এই বিভাগে চমৎকার সরস করে বাংলা ভাষায় বানান শিক্ষা দেওয়া হত। দুটি কিশোর কিশোরী, নন্তু আর টুম্পি, তাঁদের কাকাবাবু মজা করে তাদের বানান শেখাতেন। শিরোনামগুলিও ছিল অতি আকর্ষক – যেমন ‘চন্দ্রবাবুর নৌকাডুবি।’ এই লেখাটিতে বলা ছিল একটা নৌকোতে করে সাঙ্গোপাঙ্গ সমেত চন্দ্রবাবু যাচ্ছিলেন পদ্মানদী বেড়াতে, তাঁর নৌকাবোঝাই চন্দ্রবিন্দু। মানে চন্দ্রবিন্দুরাই সাঙ্গোপাঙ্গ। হঠাৎ ঝড়ে নৌকোটি পড়ে যায়, পড়ে বাংলার পশ্চিম দিকে। চন্দ্রবিন্দুগুলি সাঁতার কেটে সব এপারে এসে উঠে পড়লো, ফলে পশ্চিম বাংলার লোকেরা যেমন হাঁসতে থাকে, পূর্ববঙ্গের লোকেরা তেমনি কাদতে থাকে। দূর থাকায় চন্দ্রবিন্দু সাঁতরে পুব দিকে গিয়ে আর উঠতে পারেনি যে। বোঝো ব্যাপারখানা।
আর একটি অধ্যায় ছিল – ‘ঘটির মধ্যে মাছ।’ এটা সেই বার্নাড শ’য়ের বিখ্যাত গল্প – ‘Fish=Ghoti।’ আসলে বলা শব্দ আর লিখিত শব্দের মধ্যে তফাৎ সব ভাষাতেই ধরা পড়ে।
মজা করে শিখিয়েছিলেন পুরোহিত থেকেই পৌরোহিত্য। কাজেই ‘পৌরহিত্য’ নয়। নন্তু জিজ্ঞেস করেছিল, কিন্তু ‘পুরোহিত’ লিখতে গিয়ে কেউ যদি ‘ও’কার না দেয়? কাকুর সরস উত্তর, ‘তাহলে পুরো হিত হবে না।’ অধ্যায়টির নাম – ‘ও কোথায় গেল?’ অলক আর অলোক এর তফাৎ বুঝে নন্তু মজা করে গাইতে লাগলো – ‘অলকে ও-কার না দিও / শুধু শিথিল লকেরে বাঁধিও।’
 এমনভাবে শেখার পর আর আমার কোনদিন এই বানান ভুল হয়নি। আরো ছিল – ‘কি নিয়ে গোলমাল’ যেখানে ‘কি’ আর ‘কী’ র তফাৎ বোঝানোর জন্য একই প্রশ্ন করা হয়েছিল দু’জনকেই। প্রশ্নটি ছিল, ‘তুই কি খাবি?’ উত্তরে একজন লিখেছিল, ‘খাব’ আর একজন লিখেছে, ‘আম।’ সেই থেকেই বুঝিয়ে দেওয়া গিয়েছিল ‘কি’ আর ‘কী’র পার্থক্য।
এমনভাবে শেখার পর আর আমার কোনদিন এই বানান ভুল হয়নি। আরো ছিল – ‘কি নিয়ে গোলমাল’ যেখানে ‘কি’ আর ‘কী’ র তফাৎ বোঝানোর জন্য একই প্রশ্ন করা হয়েছিল দু’জনকেই। প্রশ্নটি ছিল, ‘তুই কি খাবি?’ উত্তরে একজন লিখেছিল, ‘খাব’ আর একজন লিখেছে, ‘আম।’ সেই থেকেই বুঝিয়ে দেওয়া গিয়েছিল ‘কি’ আর ‘কী’র পার্থক্য।
এছাড়া ছিল ‘চিৎ হওয়া উচিত নয়’ – যেখানে শেখানো ছিল কেন সত্যজিৎ আর কেন অজিত।
চমৎকার লেখা ছিল ‘খেন্তিপিসির শুচিবাই।’ সেখানে আবার বোঝানো ছিল ‘ণ’ কেন ‘ণত্ব’ বিধি মেনে নিলেও কোন কোন ক্ষেত্রে আবার ‘ন’ হয়ে যায়, যেমন ‘অর্পণ,’ ‘নির্মাণ,’ কিন্তু ‘অর্জন’ বা ‘গর্জন।’ ‘ণ’ এর নাকি খেন্তিপিসির মত শুচিবাই আছে। যখন ‘র’ জাতীয় কিছুর পর স্বরবর্ণ ধরনের কিছু থাকে, তাহলে শুচিবায়ুগ্রস্ত খেন্তিপিসি মূর্ধন্য-কে পাল্টান না। যেমন, ‘উত্তরায়ণ’ বা ‘নারায়ণ।’ একই যুক্তি ‘প’ বর্গের ওষ্ঠ বর্ণ সম্পর্কেও। কারণ এগুলো তো গলায় লেগে এঁটো হয় না। কিন্তু ‘ক, চ, ত, ট’ এই বর্গের শব্দগুলি যথাক্রমে কন্ঠ, তালু, দন্ত্য ও মূর্ধাতে লেগে গিয়ে ‘এঁটো’ হয়ে একাকার কাণ্ড। তাই তারা ‘ণত্ব’ ত্যাগ করে। তাই ‘রূপায়ণ’ বা ‘রামায়ণ’ কিন্ত গ্রন্থায়ন। সুন্দর ব্যাখ্যা।
সঙ্গে ছিল মাঝে মাঝেই রবীন্দ্র কবিতার বা সুকুমার রায়ের ছড়ার ঝলক। একেই বলা যায় সরস পাণ্ডিত্য।
প্রথম পড়েছিলাম সেই ১৯৭৬ সালে ধারাবাহিক ‘আনন্দমেলা’তে। পরে যখন বই হিসেবে কিনেছিলাম তখন, সম্ভবত বছর চার পাঁচ আগে, আবার পড়লাম। আবার নতুন করে ভালো লাগল। যাঁরা বাংলা ভাষায় লেখালেখি করতে চান, বইটি তাঁদের কাছে এক অপূর্ব জগৎ খুলে দিতে পারে বলেই আমার বিশ্বাস।
প্রণাম কুন্তক! সেই ছোটবেলাতেই আপনার মত শিক্ষকেরা আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছিলেন বলে ভাষা শিক্ষা কখনো বিরক্তিকর না হয়ে রীতিমতো চিত্তাকর্ষক হয়েছে।

7 Comments