প্রাচীন ভারতের ‘উট্জ স্টিল’
ম্যাসিডোনিয়ার আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট ইউরোপে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের পর, খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ সনে ভারত আক্রমণ করেছিলেন। সেই সময় পুরুরাজ আলেকজান্ডারের জয়যাত্রা প্রতিহত করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে হাইডাস্পেস নদীর ধারে (এখনকার ঝিলম নদী) যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু এই অসম যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। তাঁকে বন্দি করে আলেকজান্ডারের কাছে আনা হলে আলেকজান্ডার জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি সম্রাটের কাছে কী ধরনের ব্যবহার প্রত্যাশা করেন।

পুরুরাজ সাহসের সঙ্গে বলেন, ‘একজন রাজা অন্য একজন রাজার কাছ থেকে যেমন ব্যবহার পান, তিনি তাই প্রত্যাশা করেন।’ আলেকজান্ডার এই উত্তর শুনে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি পুরুরাজকে তার রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং তার সাথে বন্ধুত্ব করেছিলেন। এই কাহিনি স্কুলের ইতিহাস বইতে লেখা আছে।
কিন্তু যে কথা ছোটবেলার ইতিহাস বইতে লেখা নেই, তা হলো এক খণ্ড ইস্পাত। আলেকজান্ডার স্বদেশে ফিরে যাওয়ার সময় পুরুরাজ তাঁকে উপহার হিসাবে ৩০ পাউন্ড ওজনের একটা ইস্পাতের খণ্ড (স্ল্যাব) দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। দোর্দণ্ড প্রতাপ আলেকজান্ডারকে একটা ইস্পাতের খণ্ড উপহার? বিশ্বাস করা মুশকিল। কিন্তু ওই ইস্পাত সাধারণ ইস্পাত ছিল না, ছিল ভারতীয় ‘উট্জ স্টিল’ বা উট্জ ইস্পাত যা তৎকালে রূপো এমনকি সোনার চেয়েও মূল্যবান ছিল।
তখন যুদ্ধ হত বর্শা ও তলোয়ার দিয়ে। সব যোদ্ধাই চাইত মহা মূল্যবান ভারতীয় (উট্জ) ইস্পাত দিয়ে তৈরি কিংবদন্তি দামাস্কাস তরোয়াল দিয়ে যুদ্ধ করতে। বর্শার ফলাও তৈরি হত উট্জ ইস্পাত দিয়ে, তাই ‘উট্জ স্টিলের’ চাহিদা ও দাম ছিল অত্যন্ত বেশি। ভারত থেকে চড়া দামে এই উট্জ ইস্পাত কিনে দামাস্কাসে তৈরি হত তরোয়াল – “দামাস্কাস সোর্ড।” আমেরিকান ঐতিহাসিক উইল ডুরান্টের লেখাতেও প্রাচীন ভারতীয় এই ইস্পাত যে অত্যন্ত মূল্যবান ছিল তার স্বীকৃতি পাওয়া যায়।
কী এই মহামূল্যবান ‘উট্জ স্টিল’? খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর সময় উট্জ স্টিল নামে পরিচিত একটি বিশেষ ক্রুসিবল ইস্পাত দক্ষিণ ভারতে তৈরি হত এবং বিশ্বব্যাপী রপ্তানি করা হত। এটি প্রাচীনকালে উক্কু, হিন্দভি স্টিল, হিন্দুওয়ানি স্টিল, টেলিং স্টিল, এবং সেরিক আয়রন, ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। উট্জ নামটি “উত্সা”- সংস্কৃত অর্থ ঝর্ণা, “উক্কু”- কান্নাডা ভাষায় স্টিল, এবং/বা “উড়ুকু”- প্রাচীন তামিল ভাষায় অর্থ গলে যাওয়া, এই সব এক বা একাধিক নাম থেকে উদ্ভূত।
এই সময় তামিলনাড়ুর কোডুমানাল, তেলেঙ্গানার গোলকুন্ডা, কর্ণাটকের কিছু স্থানে এই ক্রুসিবল ইস্পাত তৈরি শুরু হয়েছিল। ‘উট্জ স্টিল’ “ইনগট” আকারে ঢালাই করা হত। কাঁচা মাল বা আকর কাছাকাছি খনি থেকেই সংগ্রহ করা হত। বলা ভাল, এই বিশেষ খনিগুলোর কাছাকাছিই এই শিল্প গড়ে উঠেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ সালে (300 BCE) বা তার আগে, উট্জ স্টিল ইনগট তৈরির প্রযুক্তি তানজোর, মাইসোর সহ অনেকগুলি জায়গায়, এমনকি উত্তর পশ্চিমের লাহোর, অমৃতসর, আগ্রা, জয়পুর, গোয়ালিয়র, প্রভৃতি জায়গায় ছড়িয়ে যায়।
গুপ্ত যুগের পরে, ৩১৯ থেকে ৫৫০ খ্রিষ্টাব্দ (319–550 CE) পর্যন্ত, ভারতে লোহা ও ইস্পাত উৎপাদন বেশ উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এখানে বলে রাখা ভালো, ধাতুবিদ্যার উন্নতির ফলে ধাতুবিদ ও ধাতু-কর্মীরা দিল্লির বিখ্যাত লৌহস্তম্ভ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, এই স্তম্ভটি দুই সহস্রাব্দের বেশি সময় ধরে অবিকৃত আছে এবং কোনোরকম ক্ষয় হয়নি বা মরিচা ধরেনি।
বহু যুগ ধরে ইউরোপে উৎপাদিত ইস্পাত, ভারতের উট্জ স্টিলের মানের ধারে কাছে আসতে পারত না। ভারত পরবর্তী শতাব্দীতেও ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় দেশ হিসাবে পরিগণিত হত। ১৭তম শতাব্দীর শেষের দিকে, উট্জ ইস্পাত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হত এবং কয়েক হাজার স্টিল ইনগট করমন্ডল উপকূল থেকে নিয়মিত ভাবে পারস্য দেশে রপ্তানি করা হত। উট্জ স্টিল দিয়ে তরোয়াল ও অন্যান্য অস্ত্র দামাস্কাসে প্রচুর পরিমাণে তৈরি হত। সেকালে দামাস্কাসই ছিলো অস্ত্র তৈরির প্রধান কেন্দ্র। এই উট্জ স্টিলও সেখান থেকে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের নানান দেশে, এমনকি চিন দেশেও রপ্তানি করা হত।
প্রাচীন চিনে বিন্টি নামক এক ধরণের ইস্পাত প্রাচীন ভারতের উট্জ স্টিলের-এর সমকক্ষ বলে প্রশংসিত হত। উট্জ স্টিলের মতই বিন্টির বৈশিষ্ট্য ছিল তীক্ষ্ণধার, শক্তিশালী, পোক্ত, ও নমনীয়। বিন্টির তৈরি তলোয়ার লোহার বর্ম কেটে ফেলতে পারত, কিন্তু তলোয়ারের কোন ক্ষতি হত না। চিনেরই কেউ কেউ দাবি করেন যে আসলে বিন্টি ছিল ভারতীয় উট্জ স্টিল এবং তা হয় সরাসরি ভারত থেকে কিংবা পারস্যের মাধ্যমে চীনে আমদানি হত। চীনের প্রবীণ পণ্ডিতদের (ইয়াং কুয়ান এবং জাং জিগাও) লেখাতেও পাওয়া যায় “বিন্টি হল উট্জ নামক ভারতীয় ইস্পাত থেকে তৈরি।” এখানে বলা যেতে পারে, চিনই প্রথম লোহা ঢালাই করতে সক্ষম হয়েছিল আর ইস্পাত ঢালাই প্রথমে হয়েছিল ভারতে।
মরক্কোর ভূগোল বিশারদ আশ-শরীফ আল-ইদ্রিসি (১১০০ থেকে ১১৬৫ খ্রিস্টাব্দ) ভারতীয় তরোয়ালগুলির পঞ্চমুখে প্রশংসা করেছিলেন আর “হিন্দুরা কীভাবে এই ধরণের মারাত্মক লোহা তৈরিতে দক্ষতা অর্জন করেছিল” তা বর্ণনা করেছিলেন। ভারতীয় ইস্পাত, বিশেষত ভারতীয় তরোয়ালগুলি আরবিতে “হিন্ডুয়ানি” নামে পরিচিত ছিল। এই ভারতীয় ইস্পাত বা উট্জ স্টিলের তৈরি তরোয়ালগুলি ছিল একাধারে শক্ত আবার নমনীয়। এটি এতই নমনীয় ছিল যে তরোয়ালগুলি ৯০ ডিগ্রি কোণে বাঁকানো যেত – ছেড়ে দিলে আবার সোজা হয়ে যেত। এত নমনীয়তা সত্ত্বেও এগুলি ছিল অত্যন্ত শক্ত। ক্রুসেডের সময় মুসলিম বাহিনীর নেতা সালাউদ্দিন এবং তার বাহিনী এই উট্জ স্টিলের তৈরি দামাস্কাস তরোয়াল ব্যবহার করে ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের পরাজিত করেছিল। তরোয়ালগুলি এক কোপে ইউরোপীয় সৈন্যদের শিরস্ত্রাণ কেটে ফেলতে পারত। আবার তরোয়ালগুলি এত ধারালো ছিল যে রেশমের পতনশীল গোছাকে শূন্যেই কেটে ফেলতে পারত। এই তিনটে গুণ, যার মধ্যে দুটি আবার পরস্পর বিরোধী, একই ইস্পাতে একসঙ্গে থাকা এক অভূতপূর্ব ঘটনা। ক্রুসেডের পরে এই “হিন্দুয়ানি” তরোয়ালগুলি ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে স্পেন এবং ইতালিতে প্রচলিত হয়েছিল।

এই ইস্পাতের আর একটি সুন্দর বিশেষত্ব হল – উট্জ স্টিল দিয়ে দামাস্কাসে তৈরি তলোয়ারের গায়ে সুন্দর সুন্দর নক্সা ফুটে উঠত। মনে হত কোনো শিল্পী নিপুণ হাতে এই নক্সাগুলো এঁকেছেন। কিন্তু এই সুন্দর নক্সাগুলো তৈরি হত ধাতু বিজ্ঞানের কোনো এক বিশেষত্বের ফলে।
সপ্তদশ শতক থেকে উনবিংশ শতক অবধি পাশ্চাত্যে ভারতীয় উট্জ স্টিলের বৈশিষ্ট্য, যেমন শক্তি, তীক্ষ্ণতা, এবং নমনীয়তা, ইত্যাদির প্রতিরূপ তৈরি করার জন্যে অনেক গবেষণা করা হয়েছিল। বিদ্যুৎ এবং চৌম্বকবাদের ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বিশেষ ভাবে পরিচিত মাইকেল ফ্যারাডেও এই গবেষণায় বহু বছর ধরে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন ধরণের উপাদান, যেমন ভ্যানডিয়াম, মলিবডেনাম, ক্রোমিয়াম, ইত্যাদি লোহাতে যুক্ত করে স্টিলের কাঠামো এবং বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতিরূপ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সমস্ত প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয় – তাঁরা উট্জ স্টিল তৈরি করতে ব্যর্থ হন।
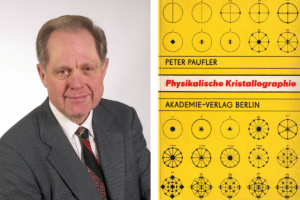
ক্রিস্টালোগ্রাফার পিটার পাউফলার এবং তাঁর দুই সতীর্থের কাছে উট্জ স্টিলের তৈরি কিছু তরোয়াল ছিল। একটি ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করে সেই তরোয়ালের ইস্পাতটির অন্তর্নিহিত কাঠামোটিকে ‘কার্বন ন্যানো-টিউব’ হিসাবে তাঁরা আবিষ্কার করেন। এই তিন বিজ্ঞানী এক-পরমাণু পুরু দেয়াল দিয়ে তৈরি ন্যানো-টিউবের কাঠামো আবিষ্কার করার জন্য স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।
এই ন্যানো-টিউবগুলি শক্ত উপাদান যথা সিমেন্টাইট দিয়ে তৈরি। বিজ্ঞানীদের মতে, তলোয়ার তৈরিতে ব্যবহৃত স্টিলের অন্তর্নিহিত কাঠামোতে ছিল ন্যানো-টিউব যা “ন্যানোওয়ারের” মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তলোয়ারের কঠোরতা, তীক্ষ্ণতা এবং নমনীয়তার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ছিল এই ন্যানো-টিউব ও ন্যানোওয়ারের সমন্বয়।
এর পরেও, ২০০৬ সাল নাগাদ, আন্তর্জাতিক স্তরের বিজ্ঞানীরা ভারতীয় স্টিলের গোপন বিষয়গুলি সম্পর্কে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের গবেষণার ফল ভালো ভাবে জানা যায়নি। পরে বোঝা গেছে যে এই ভারতীয় ইস্পাত ক্রুসিবলে তৈরি করার সময় জ্বলন্ত পাতা এবং কাঠ দিয়ে লোহা উত্তপ্ত করা হত। লোহার সাথে উপস্থিত অপদ্রব্য, যেমন ভ্যানডিয়াম ইত্যাদি, যথেষ্ট উচ্চ তাপমাত্রায় উদ্ভিদ পদার্থের কার্বনের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে ন্যানোটিউব তৈরি করত। রাইবোল্ড এবং আরও অনেকে বিশ্লেষণ করে সিমেন্টাইটের ন্যানোওয়ারকে ঘিরে কার্বন ন্যানোটিউবগুলির উপস্থিতির কথা সমর্থন করেছিলেন। তাঁরা প্রমাণ করেছিলেন যে গরম/ঠাণ্ডা/ফোর্জিং চক্রে ভ্যানডিয়াম, মলিবডেনাম, ক্রোমিয়াম, ইত্যাদির ট্রেস উপাদান বা অপদ্রব্যগুলির অবদান আছে, এর ফলে একটি শক্ত উচ্চ কার্বন যুক্ত ইস্পাতও নমনীয় থেকে যায়।
এখন বোঝা যাচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় ধাতুবিদ ও ধাতুকর্মীরা নিজেদের অজান্তেই অত্যাধুনিক “ন্যানো–টেকনোলজি” ব্যবহার করে এক অত্যাশ্চর্য ইস্পাত শুধু ভারতবাসীদের নয়, সমস্ত পৃথিবীকে উপহার দিয়ে ভারতকে গৌরবান্বিত করেছিলেন।
কিন্তু কীভাবে এই অসাধারণ দক্ষতা পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেল? এই ব্যাপারে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ইতিহাস বলে, ঢাকার “মসলিন কাপড়” বিলেতে তৈরি মিলের কাপড়কে টেক্কা দিচ্ছিল। তাই ব্যবসায়িক কারণে ঢাকা ও তার আশেপাশে খুব পাতলা “মসলিন কাপড়” তৈরি বন্ধ করা দরকার ছিল। এই কাপড় তৈরির কৌশলটি বিলুপ্তির কারণ অনেকেরই হয়তো জানা আছে। “মসলিন কাপড়” তৈরিতে যুক্ত ব্যক্তি এবং তাঁতিদের বুড়ো আঙ্গুল কেটে দেওয়া হয়, যাতে তারা আর তাঁত বুনতে না পারে। স্যার রিচার্ড ফ্রান্সিস বার্টন এবং ডেভিড আর্নল্ডের মতে এটি করা হয়ে ছিল মূলত সরকারি উচ্চ পর্যায়ে গৃহীত নীতি অনুসারেই।
একই ভাবে ব্রিটিশ শাসিত ভারতে উট্জ স্টিল তৈরির দক্ষতাও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকরা বিদ্রোহীদের সাফল্যে লোহা ও ইস্পাত তৈরির দক্ষতার গুরুত্ব অনুধাবন করেছিল। যে খনির আকর থেকে উট্জ স্টিল তৈরি হত, সেই আকরের কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। তা হল আকরের সঙ্গে মিশ্রিত অপদ্রব্য (ইমপিউরিটি)। উট্জ স্টিল তৈরির ক্ষেত্রে এই অপদ্রব্যের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। তাই কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট খনিগুলো জোর করে বন্ধ করার মত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। এমনকি সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে খনিকর্মীদের জাতিও বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং তার সঙ্গে তাদের উট্জ স্টিল তৈরির জ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা চিরতরে হারিয়ে যায়।
উট্জ স্টিল কেবল অতীতের বিস্ময়কর ইস্পাতই নয়, এটি ভবিষ্যতের “সুপার স্টিল।” আশা করব এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী এবং/অথবা কয়েকটি জাতীয় পরীক্ষাগার অবশ্যই প্রযুক্তিটি পুনরায় উদ্ভাবন করে আবারও দেশকে গৌরবান্বিত করবে।
——–
তথ্যসূত্রঃ
[লেখাটিতে অনেকগুলি প্রবন্ধের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। নীচে কয়েকটির উল্লেখ করা হল।]
Ancient Origins. (2015, February 13). “Historic Indian sword was masterfully crafted.” See, https://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/historic-indian-sword-was-masterfully-crafted-002674.
Balasubramaniam, R. (2007). Historical Note: Wootz Steel. Indian Journal of History of Science, 42, 3511-516. See, http://www.insa.ndl.iitkgp.ac.in/xmlui/handle/1234567/1812?show=full
Bintie Steel of China. See, https://www.insa.nic.in/writereaddata/UpLoadedFiles/IJHS/Vol44_3_2_WLox.pdf 5; https://www.britinnica.com/technology/wootz-steel.
Dhwty. (2018, June 2). “Wootz steel: The mysterious metal that was used in deadly Damascus blades,” Ancient Origins. See, https://www.ancient-origins.net/artifacts-ancient-technology/wootz-steel-damascus-blades-0010148.
Grazzi, F., Barzagli, E., Scherillo, A., et al. (2016, March). “Determination of the manufacturing methods of Indian swords through neutron diffraction.” Microchemical Journal, 125, 273-278. See, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0026265X15003057?via%3Di.
Guha, B. (2015, June 20). “Story of swords and steel.” The Telegraph Online. See, https://www.telegraphindia.com/opinion/story-of-swords-and-steel/cid/1441453.
Ranganathan, S., and Srinivasan, S. (2006, June). “Age of Wootz steel: A tale of Wootz steel.” Resonance. See, https://www.ias.ac.in/article/fulltext/reso/011/06/0067-0077.
Srinivasan, S., and Ranganathan, S. “Wootz steel: An advanced material of the ancient world.” Indian Institute of Science, Dept. of Metallurgy. Bangalore, India. See, http://dtrinkle.matse.illinois.edu/MatSE584/articles/wootz_advanced_material/wootz_steel.html.
ShapeCUT. “The Secrets Behind Wootz Steel.” (2016, November 18). See, https://www.shapecut.com.au/blog/the-secrets-behind-wootz-steel/
WikipediaI. “Wootz Steel.” See, https://en.wikipedia.org/wiki/Wootz_steel.
Wikipedia. “Porus.” See, https://en.wikipedia.org/wiki/Porus
ছবিঃ অন্তর্জাল

1 Comment