তেভাগা আন্দোলনে সুন্দরবন

শৈশব ও কৈশোরের খণ্ডকাহিনিঃ
আমাদের গ্রামের নাম গোবিন্দরামপুর। বয়স্ক লোকেরা বলত ‘বেরার লাট।’ আমার ঠাকুমা তো সবসময় ওটাই বলত, কখনও তাঁর মুখে গোবিন্দরামপুর শুনিনি। পরে জেনেছি ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে যখন সুন্দরবনের জঙ্গল হাসিল করে বসতি গড়ে উঠেছিল তখন এই লট (Lot)-এর জমিদার ছিলেন মেদিনীপুরের বেরা পদবির এক জমিদার (নামটা এখন মনে নেই)। সেই থেকেই বেরার লাট। আমাদের বাড়ি ছিল গ্রামের দক্ষিণতম প্রান্তে। ঘিয়াবতী খালের শাখা খাল হল আমাদের গ্রামের দক্ষিণের সীমানা। ওপারের গ্রামের নাম হল বিশালাক্ষিপুর। খালের ঠিক ওপারের রাস্তার পাশে দুটো ভগ্নপ্রায় কুঁড়েঘর ছিল। ছোটো থেকে জেনে এসেছি দুটো বাড়ি দুই ভাইয়ের। পুব দিকের বাড়ির মালিকের নাম হল ভূতনাথ বেরা। সবাই বলত ‘ভুতু বেরা।’ আমিও বলতাম। কালো, বেঁটেখাটো চেহারা। অধিকাংশ সময় ময়লা গামছা পরে থাকে। ওঁর স্ত্রী মারা গেলেও একটা মেয়ে ছিল। মেয়েটা মানসিক রোগগ্রস্ত বলে জানতাম। ছেঁড়া, ময়লা শাড়ি পরে থাকত। মাঠ থেকে গোবর কুড়োত। তো সেই ভুতু বেরা দেখতাম খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। একদিন আমার বাবা কোনও এক প্রসঙ্গে বলেছিলেন, তেভাগা আন্দোলনের সময় ভুতু বেরার পায়ে পুলিশের গুলি লেগেছিল। সেজন্য ও খুঁড়িয়ে হাঁটে। তখন তেভাগা আন্দোলন কী কিছুই জানতাম না।
পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হলাম আমাদের গ্রামের হাইস্কুলে – অশ্বিনীকুমার উচ্চ বিদ্যালয়। গ্রামের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে স্কুল। টালির ছাউনি দেওয়া মাটির দেয়ালের স্কুল। জায়গাটার নাম হাটপাড়া। আগে সেখানে হাট বসত, তাই ওই নাম। গ্রামের উত্তর সীমানায় কালনাগিনী নদী। স্কুল থেকেই দেখা যায়। স্কুলের পাশেই পুবদিকে একটা বড়ো দালানযুক্ত বাড়ি ছিল। সবাই বলত কাছারিবাড়ি। ওটা নাকি একসময় জমিদারদের কাছারি ছিল। টিফিনের সময় আমরা ওখানে খেলতে যেতাম। কাছারির উঠোনে একটা বড়ো কুল গাছ ছিল। সেই গাছ থেকে আমরা কুল পেড়ে খেতাম। আর স্কুলের পশ্চিম দিকে ছিল বেরাদের একটা পরিবার। ওই পরিবারের একটা ছেলে আমার ক্লাসেই পড়ত। ওই ছেলেটা ও তার দাদারা সবাই খুব ফর্সা আর বড়োসড়ো চেহারার। সবাই খুব ভালো ফুটবল খেলত। সবাই বলত, ওরাই ছিল গ্রামের জমিদার। আর বাবার মুখে শুনেছিলাম, তেভাগা আন্দোলনের সময় ওই কাছারি বাড়িতে গোলাগুলি চলেছিল।
ঠাকুমার মুখে বহুবার শুনেছি একটা কাহিনি। তেভাগা আন্দোলনের সময় নাকি আমার সেজো জেঠু আর ন’জেঠুকে ধরার জন্য পুলিশ আর জমিদারের লেঠেল বাড়িতে এসেছিল। তখন ঠাকুমা দরজায় বঁটি হাতে রুখে দাঁড়িয়েছিল। আর সেই সুযোগে পেছনের দরজা দিয়ে দুই জেঠু গোপন আস্তানায় চলে গেছিল। আমার ওই দুই জেঠু তেভাগা আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিল।
তাই আমার শৈশব থেকে তেভাগা আন্দোলন শব্দটার সাথে পরিচিতি ছিলাম। কিন্তু সেটা আসলে কী তা জানতাম না। কৈশোরকাল পর্যন্ত জানার কৌতূহলও হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পড়ি, একজন ছাত্রনেতা আমার বাড়ি কাকদ্বীপ শুনে বলেছিল, ‘কাকদ্বীপ মানে তো তেভাগা আন্দোলনের কেন্দ্র।’ মনে পড়ে গেল শৈশবের সেইসব কথা – ভুতু বেরা, কাছারি বাড়ি, ঠাকুমার বঁটি হাতে দরজায় দাঁড়ানো। তেভাগা আন্দোলন নিয়ে জানার আগ্রহ মনের মধ্যে অঙ্কুরিত হল তখন থেকেই।
তেভাগার প্রেক্ষাপটঃ
১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে সিরাজ-উদ-দ্দৌলার পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে বাংলার দখল নিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। কিন্তু তারা প্রজা শাসনের ভার নিল না ১৭৭২ সাল পর্যন্ত। ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করলেও রাজস্ব আদায়ের প্রকৃত ভার ছিল মোহাম্মদ রেজা খান ও সিতাব রায় নামে দু’জন রাজকর্মচারীর ওপর। এদের শোষণ ও অত্যাচারে বাংলার কৃষকদের ভয়ানক দুর্গতি হয়। এক তৃতীয়াংশ মানুষ অনাহারে মারা যায়। ১৭৭০ সালে (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) বাংলা জুড়ে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ শুরু হয় যা ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। এই পরিস্থিতিতে গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ সালে চালু করেন পাঁচশালা বন্দোবস্ত। এই নিয়মে জমির মালিকানা পাঁচ বছরের জন্য রইল জমিদার জোতদারদের হাতে। ওই বছর বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর জেলায় নিযুক্ত হল ব্রিটিশ শাসনাধীন পরাধীন বাংলার প্রথম জেলাশাসক (কালেক্টর) গুডল্যান্ড সাহেব। ১৭৭৩ সালে উত্তরবঙ্গে অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের প্রতিবাদে হল কৃষক বিদ্রোহ। দুর্ভিক্ষের মধ্যেও লাঠিয়াল দিয়ে জমিদার সেই আন্দোলনকে রক্তাক্ত করেছিল।
পাঁচশালা বন্দোবস্ত ও তারপরে একশালা বন্দোবস্ত ফলপ্রসূ না হওয়ায় ১৭৯০ সালে গভর্নর লর্ড কর্নওয়ালিস দশ বছরের জন্য জমিদারদের জমির মালিকানা দেন। কিন্তু তাতেও সুবিধা না দেখে ১৭৯৩ সাল থেকে চালু করেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এই নিয়মে জমিদার বংশানুক্রমে জমির মালিকানা পেল। আর চাষিরা স্থায়ীভাবে বাঁধা পড়ল জমিদারতন্ত্রের শিকলে। এর ফলে চাষিদের উপর জমিদার জোতদারদের অত্যাচার উঠল চরমে। সরকারকে কর দিত জমিদার। জমিদারের নিচে ছিল ক্রমান্বয়ে পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, লাটদার ইত্যাদি। আর একেবারে শেষে ছিল ক্ষেতমজুর। তাদের ওপরে ক্রমান্বয়ে মাহিন্দার, ভাগচাষি, চাষি ইত্যাদি। সরকার থেকে চাষির মধ্যে ছিল ২৪ টি মধ্যসত্ত্বভোগী। মধ্যসত্ত্বভোগীদের চাহিদা মেটাতে মেটাতে চাষি, ভাগচাষি, মাহিন্দার ও ক্ষেতমজুরদের ভাগে উৎপন্ন ফসলের অতি সামান্য অংশ জুটত। যারা ফসল ফলাত তারাই থাকত অনাহারে আর গোলা ভরত জমিদার জোতদারের। পৌনে দুশো বছর ধরে বাংলার চাষিরা এভাবেই জমিদারতন্ত্রের দ্বারা শোষিত হয়ে এসেছে।
১৯৩৬-৩৭ সাল থেকে বাংলার চাষিদের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে দাবি উঠতে শুরু করেছিল যে ফসলের তিনভাগের এক ভাগ পাবে জমিদার, আর দু’ভাগ পাবে চাষি। কিন্তু সেই দাবি আন্দোলন হিসেবে দানা বাঁধার অবকাশ তখন পায়নি। ১৯৪০ সালে ফ্লাউড কমিশনও অনুরূপ সুপারিশ করেছিল। চারের দশকের শুরু থেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তীব্র প্রভাব পড়ল সাধারণ মানুষের ওপর। কৃত্রিম খাদ্যসংকট তৈরি করা হল। শুরু হল ভয়াবহ লবণ ও বস্ত্র সংকট। সুযোগ বুঝে অবৈধ মুনাফালাভে মেতে উঠল এক শ্রেণির ব্যবসায়ী। শুরু হল ওষুধ নিয়েও চোরাকারবার। ফলশ্রুতি হল দুর্ভিক্ষ যা ইতিহাসে পঞ্চাশের (১৩৫০ বঙ্গাব্দ, ১৯৪২ সাল) মন্বন্তর নামে পরিচিত। অখাদ্য, কুখাদ্য খেয়ে আমাশয় ও কলেরায় ভুগে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যেতে লাগল। ১৯৪৩ সালে চার লক্ষ ও ১৯৪৪ সালে চার লক্ষ গরিব বঙ্গবাসী মারা যায়। অর্থাভাবে ছোটো চাষিরা তাদের জমি বেচে দিতে বা দেনার দায়ে জমিদারকে লিখে দিতে বাধ্য হয়।
১৯৩৮-৩৯ সালে যেখানে বাংলায় ২০ শতাংশ জমি বর্গায় চাষ হত, সেখানে ১৯৪২ সালের পর ৬০ শতাংশ জমি বর্গায় চাষ হতে থাকে। অর্থাৎ নিজের জমি জমিদারকে বেচে চাষি সেই জমিতে বর্গা চাষ করে। ওই সময় নিয়ম ছিল জমির মালিককে বর্গাদার উৎপন্ন ফসলের ৬০ শতাংশ দেবে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। দিতে বাধ্য করা হত হাটতোলা, তোলবাটি, কাকতাড়ানি, খামারচাছানি, সেলামি, কয়ালি, পার্বণী, দারোয়ানি, নজরানা, আওয়াব ইত্যাদি বহু রকমের অবৈধ কর। বস্তুতঃ এত কিছু দেওয়ার পর বর্গাদারের ভাগে তেমন কিছুই জুটত না। ফলে তাদের ঋণ করতে হত জমিদার জোতদারের কাছ থেকে। সুদের হার ছিল ১৫০ – ২০০ শতাংশ। ঋণ করতে হত খাবার ধান এবং বীজ ধান। কিন্তু গরিব চাষির পক্ষে ঋণ শোধ করা সম্ভব হত না। ফলে ঘটি-বাটি পর্যন্ত বিক্রি বা বন্ধক দিয়ে সর্বস্ব হারিয়েছিল বাংলার চাষি, ভাগচাষি, ক্ষেতমজুরেরা।
অতঃপর তেভাগার সূচনাঃ
১৯৩৬ সালে কাকাবাবু কমরেড মুজফফর আহমেদের উদ্যোগে কলকাতার অ্যালবার্ট হলে এক কনভেনশনের মধ্যে দিয়ে বঙ্গীয় কৃষক সংগঠনী কমিটি তৈরি হয়। এর আহ্বায়ক মনোনীত হন কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি। ওই সময় জেল থেকে ছাড়া পাওয়া একদল তরুণ স্বাধীনতা সংগ্রামী এই সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করেন এবং সুন্দরবন অঞ্চলের কৃষকদের সংগঠিত করার উদ্যোগ নেন। প্রথম সফল আন্দোলন হয় হাড়োয়াতে। ব্রিটিশ কোম্পানি ‘পোর্ট ক্যানিং’ সরকারি মদতে হাড়োয়া, ক্যানিং, সন্দেশখালি ইত্যাদি এলাকায় চাষিদের কাছ থেকে জোর করে বসতি উচ্ছেদ করে জমি দখল করেছিল। কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি, কমরেড নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, কমরেড মনোরঞ্জন শূর প্রমুখের নেতৃত্বে ওইসব এলাকার সাধারণ চাষি, ক্ষেতমজুর, এমনকি মহিলারাও সংগঠিত হন। উত্তেজিত জনতা হাড়োয়ায় সাহেব জেলাশাসকের সংবর্ধনা মঞ্চ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। সশস্ত্র পুলিশের সাথে প্রথম মুখোমুখি রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় সুন্দরবনের শোষিত ভাগচাষি, ক্ষেতমজুর ও তাদের পরিবারের মহিলারা। কুন্তি বাছাড় মহিলাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। হাড়োয়ার ব্রাহ্মণচকে এক বিশাল জনসভা হয়। বক্তা ছিলেন বঙ্কিম মুখার্জি, সৌমেন ঠাকুর এবং সর্বভারতীয় কৃষক নেতা ইন্দুলাল যাজ্ঞিক।
সুন্দরবন এলাকার অন্যত্রও নানা দাবি নিয়ে চাষি, ভাগচাষি ও ক্ষেতমজুরদের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ডায়মন্ডহারবার বজবজ সীমান্ত এলাকায় সুষ্ঠু জলনিকাশী ব্যবস্থার দাবিতে সংগঠিত চাষিরা আন্দোলন শুরু করে। নেতৃত্ব দেন বুড়ুলের প্রভাস রায়, মহীরামপুরের যতীশ রায় প্রমুখ টগবগে তরুণেরা। এভাবেই উঠে আসতে থাকে নতুন নতুন কৃষক-নেতৃত্ব। কিন্তু ফসলের অধিকার নিয়ে চাষিদের মধ্যে সংগ্রামের বীজ তখনও রোপিত হয়নি।
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (CPI)-র কৃষক শাখা ‘বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা’ ১৯৪০ সালেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ (ভাগচাষি বা বর্গাদারকে প্রজা বলে মালিককে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং মালিকের প্রাপ্য ফসল হবে বর্গাদারের উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের এক ভাগ) কার্যকর করার জন্য তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এজন্য ভাগচাষি ও ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের মধ্যে সংগঠন ছড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এই উদ্যোগে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে প্রবল সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় সুন্দরবন অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক মানুষ মারা যায়। সমস্ত আমন ধান নষ্ট হয়ে যায়। মারা যায় বেশিরভাগ গবাদি পশু। একদিকে বিশ্বযুদ্ধের কারণে খাদ্যসংকট, জমিদার ও জোতদারদের নির্মম শোষণ, তার ওপর ঘূর্ণিঝড়ে প্রবল ক্ষয়ক্ষতি সুন্দরবনবাসীর জীবন অন্ধকারে ঢেকে দিল। পঞ্চাশের মন্বন্তরে (১৯৪৩-৪৪) সুন্দরবন অঞ্চলের অর্ধেক মানুষ অনাহারে মারা গিয়েছিল। আর এদের বেশিরভাগ ছিল ভাগচাষি ও ক্ষেতমজুর।
ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং মন্বন্তর কৃষক সভার নেতৃত্বের কাছে সুন্দরবন অঞ্চলে সংগঠন বিস্তার করার সুযোগ এনে দিল। ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় এবং মন্বন্তরে বিপর্যস্ত সুন্দরবনের নানা অঞ্চলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার নেতারা ত্রাণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আর এভাবেই কৃষক সভার নেতৃত্বের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক গড়ে উঠল সুন্দরবনের ভাগচাষি ও ক্ষেত মজুরদের।
১৯৪৬ সাল বাংলার ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক বছর। ওই বছর মার্চ-এপ্রিল মাসে ছিল বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচন। নির্বাচনী আবহাওয়ায় বাংলার ভাগচাষিরা তেভাগা আদায়ের জন্য আওয়াজ তুলল। এই সময় বাংলা প্রদেশের আইনসভার গরিষ্ঠতা ছিল মুসলিম লীগের। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সুরাবর্দি। মুসলিম লিগ সরকার সুকৌশলে তেভাগার দাবিকে চেপে দেওয়ার চেষ্টা করে। সরকার প্রতিশ্রুতি দেয় যে তারা ওই বিষয়ে আইন তৈরি করবে এবং সেজন্য আইনসভার অধিবেশনে বিল আনবে। কিন্তু সরকার বিল না এনে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। শুধু তাই নয়, প্রথমে তারা ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব স্বীকার করেছিল। পরে জওহরলাল নেহরু যখন সাংবাদিক সম্মেলনে জানান যে কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব নিয়ে ভাবনা চিন্তা করবে এবং তা নিয়ে তারা রদবদলও করতে পারে তখন আগস্ট মাসে মুসলিম লীগ ক্যাবিনেট মিশনের (পরিবর্তিত) প্রস্তাব স্বীকার করতে রাজি হয় না এবং মুসলিম প্রধান পৃথক রাষ্ট্রের দাবি তোলে। ১৬ আগস্ট তারা হরতাল ডাকে। কলকাতার জনপথে শুরু হয় ভয়ঙ্কর হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা। সে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে নোয়াখালি, বিহার, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশসহ ভারতের নানা প্রান্তে। হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিটেমাটি ছাড়া হয়। সারা বাংলা যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুনে জ্বলছে তখন সুন্দরবনে কিন্তু তার আঁচ লাগেনি, তার একটি কারণ সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষেরা তখন তেভাগার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। অসাম্প্রদায়িক তেভাগার লড়াইয়ের জন্য সুন্দরবনের হিন্দু মুসলিম এক হয়ে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়েছে।
ওই বছরেই সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা তেভাগা আন্দোলনের ডাক দিল। দাঙ্গার মধ্যেই বাংলার হিন্দু-মুসলিম কৃষক সমাজ এই দাবিতে জেলায় জেলায় জোটবদ্ধ হতে থাকল। জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, মাল, তরাই, ডুয়ার্স, খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, হাওড়া, মেদিনীপুর, মালদহ, ২৪ পরগনা – সব জায়গাতেই জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল ভাগচাষি ও ক্ষেতমজুরেরা। সম্মুখ সমরে একদিকে ভাগচাষি ও ক্ষেতমজুর অন্যদিকে জমিদারের লাঠিয়াল ও সরকারি পুলিশবাহিনী। প্রথম পুলিশের গুলি চলল দিনাজপুরে। দু’দিনে মারা গেল ২২ জন ভাগচাষি ও ক্ষেতমজুর। অবিভক্ত বাংলার নানা প্রান্তে সংঘর্ষে ৮৬ জন ভাগচাষি ও ক্ষেতমজুর মারা গেল। তবে এই আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হল না। কারণ ভাগচাষি ও ক্ষেতমজুরদের মধ্যে ঐক্য অটুট থাকলেও সশস্ত্র পুলিশের বিরুদ্ধে লড়ার মত শক্তি ছিল না নিরস্ত্র ভাগচাষি ও ক্ষেতমজুরদের।
চুপ করে ছিল না সুন্দরবনের ভাগচাষি ও ক্ষেতমজুরেরা। কাকদ্বীপ ও নামখানা হয়ে উঠল সুন্দরবনে তেভাগা আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার বিভিন্ন নেতাকে দায়িত্ব দেওয়া হল সুন্দরবন অঞ্চলের ভাগচাষি ও ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করার জন্য। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ড. ভূপেন দত্ত, সৌমেন ঠাকুর, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, হেমন্ত ঘোষাল, নলিনীপ্রভা ঘোষ প্রমুখ। সঙ্গী তরুণ বামপন্থী ব্রিগেডের প্রভাস রায়, যতীশ রায়, গজেন মালী, বিজয় মণ্ডল, এবং বুধাখালির তিন মাইতি – যতীন মাইতি, গুণধর মাইতি ও জগন্নাথ মাইতি। গ্রামে গ্রামে কৃষক সমিতির লাল ঝান্ডার নিচে দাঁড়িয়ে এলাকার ভাগচাষিরা স্লোগান তুলল – “দশ আনা ধান চাষির, ছ’আনা ধান জমিদারের। জমিদারের খামারে আমরা ধান তুলবো না।” ১৯৪৬ সালের ১৮ নভেম্বর কাকদ্বীপের ডাকে বাংলো ময়দানে হল তেভাগার দাবিতে প্রথম বিশাল জনসভা। দূর দূরান্তের প্রত্যন্ত দ্বীপাঞ্চল থেকে নৌকোয় করে, পায়ে হেঁটে হাজার হাজার ভাগচাষি ও ক্ষেতমজুর জড়ো হয়েছিল সভাস্থলে। স্বাধীনতা সংগ্রামী সুনীল চ্যাটার্জির সভাপতিত্বে সেই জনসভায় বক্তৃতা দেন কংসারি হালদার, যতীন মাইতি, গুণধর মাইতি, রাজকৃষ্ণ মণ্ডল, মানিক হাজরা প্রমুখ তেভাগা আন্দোলনের তরুণ নেতৃবৃন্দ।
রক্তে রাঙা প্রথম পর্বের তেভাগাঃ
সুন্দরবনের ভাগচাষিদের লড়াই কিন্তু বাংলার অন্যান্য জায়গার মতো সরাসরি জমিদারের সঙ্গে হয়নি। সুন্দরবনে জমিদারির বদলে ছিল লাটদারি। অর্থাৎ ব্রিটিশরা পুরো সুন্দরবনকে যে ২৩৬ টি লটে ভাগ করেছিল তার এক একটির মালিক হল লাটদার। এরা কেউই স্থানীয় মানুষ ছিলেন না। বেশিরভাগই ছিলেন কলকাতার বিত্তবান বাঙালি, অবাঙালি বা বিদেশি। এঁরা কেউই লাটদারি দেখতে আসতেন না। স্থানীয় জোতদারেরাই লাটদারি দেখভাল করত আর বৎসরান্তে লাটদারের বাড়ি খাজনা পৌঁছে দিত। এই জোতদারেরাই ভাগচাষিদের কাছ থেকে ইচ্ছেমতো কর আদায় করত, নানারকম জোরজুলুম ও অত্যাচার করত। আর তাই এখানে ভাগচাষি ও ক্ষেতমজুরদের মূল টার্গেট হয় স্থানীয় জোতদাররা।
শুধু সুন্দরবন নয়, অবিভক্ত বাংলায় তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম ভরকেন্দ্র ছিল কাকদ্বীপ ও নামখানা। মুসলিম লীগ সরকারের পুলিশ কৃষক নেতাদের গ্রেফতার করে আন্দোলনকে ভেস্তে দেওয়ার প্রবল চেষ্টা করে। কিন্তু স্থানীয় নেতারা লুকিয়ে চুরিয়ে পাড়ায় পাড়ায় রাতের অন্ধকারে ভাগচাষি ও ক্ষেতমজুরদের নিয়ে ছোটো ছোটো সভা করে তাদের সংগঠিত করতে থাকে। নেতাদের মধ্যে মানিক হাজরা গ্রেফতার হন। তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে।
নামখানার শিবরামপুর গ্রামে রাজ্যের মধ্যে প্রথম তেভাগা আন্দোলন সাফল্য পায় ১৯৪৬-এর ডিসেম্বরে। বুধাখালির কৃষক নেতা যতীন মাইতির নেতৃত্বে আন্দোলনকারী সহস্রাধিক নারীপুরুষের সামনে জোতদাররা মাথা নত করে তেভাগার দাবি মেনে নেয়। ওই এলাকার সমস্ত ভাগচাষি সেই প্রথম জমির সমস্ত ধান জোতদারের খামারের পরিবর্তে নিজের নিজের খামারে তোলে। আন্দোলনের এই সাফল্যের খবর হাওয়ার চেয়েও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সুন্দরবনের সর্বত্র। আন্দোলনকারীরা আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। তীব্রতা বাড়ে আন্দোলনের।
১৯৪৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রক্ত ঝরল কাকদ্বীপ থানার অন্তর্গত আমার জন্মস্থান গোবিন্দরামপুর গ্রামে যা লোকমুখে ‘বেরার লাট’ বলেই খ্যাত। ভাগচাষিরা জমি থেকে ধান নিজের নিজের খামারে নিয়ে যেতে চাইলে জোতদাররা বাধা দেয়। তারা লেঠেল লাগিয়ে জোর করে সমস্ত ধান তুলে নিয়ে এলে সংঘবদ্ধ ভাগচাষি ও ক্ষেতমজুররা কাছারিবাড়িতে চড়াও হয়। পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে পুলিশ গুলি চালায় নিরস্ত্র বুভুক্ষু ভাগচাষিদের ওপর। অনেকে গুলিবিদ্ধ হয়। শহিদ হন কার্তিক খাঁড়া। ইনি হলেন তেভাগা আন্দোলনে ২৪ পরগনার প্রথম শহিদ। বুধাখালির তরুণ কৃষক নেতা গুণধর মাইতি মথুরাপুরের কুয়েমুড়ি গ্রামে আন্দোলন সংগঠিত করতে যাওয়ার সময় জোতদারের গুন্ডাবাহিনী তাঁকে আক্রমণ করে। গুণধরবাবুর প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান যতীশ হালদার।
তেভাগা আন্দোলন তীব্র আকার নেয় সুন্দরবনের অন্যান্য অঞ্চলেও। ক্যানিং-এর কালিকাতলা, মঠের দীঘি, দেউলি; বাসন্তীর আমঝাড়া, চড়াবিদ্যা অঞ্চল, গোসাবার পাঠানখালি, দেগঙ্গার চাঁপাডাঙা, সন্দেশখালি, হাড়োয়া, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ – সর্বত্র আন্দোলন শাখা বিস্তার করে। নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নেয় আন্দোলনে যুবক ও নারীদেরও সামিল করা দরকার। সভা করে স্থির করা হয় পরিবারপিছু একজন যুবক, এক টাকা ও একটি লাঠি দিতে হবে আন্দোলনকে তীব্র করতে। এতে দারুণ সাড়া মিলল। ২০ দিনের মধ্যে ১২০০ টাকা ও ১২০০ লাঠি নিয়ে আন্দোলনে যোগ দিল ভাগচাষি পরিবারের ১২০০ যুবক। শুধু কি তাই, ২০ দিনের মধ্যেই গঠিত হল ১৫০০ মহিলাকে নিয়ে নারী প্রতিরোধ বাহিনী। পুলিশ গ্রামে ঢুকে গ্রেফতার করতে এলে মহিলারা শাঁখ ও কাঁসর-ঘন্টা বাজিয়ে যুবকদের সতর্ক করে দিত। এমনকি বঁটি, দা, কাস্তে, শাবল, কুড়ুল, ঝাঁটা, লাঠি ইত্যাদি নিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলল নারীবাহিনী।



রক্তক্ষয়ী তেভাগার দ্বিতীয় পর্বঃ
তেভাগা আন্দোলনের উত্তাল ধারাবাহিকতার মধ্যেই ১৯৪৭ সালের পনেরোই আগস্ট দেশ স্বাধীন হল। কিন্তু সুন্দরবন অঞ্চলের ভাগচাষিরা স্বাধীনতার কোনও স্বাদই অনুভব করতে পারল না কারণ তারা বাঁধা পড়েছিল জোতদারদের অত্যাচার আর শোষণের শৃঙ্খলে। আর স্বাধীন বাংলার কংগ্রেস সরকার মেতেছিল জমিদার-জোতদারদের স্বার্থরক্ষায়।
১৯৪৬ সালের ১৮ নভেম্বর কাকদ্বীপের ডাকবাংলো ময়দানে তেভাগার ঐতিহাসিক সমাবেশের পর কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগর, মথুরাপুর, পাথরপ্রতিমা এলাকার ভাগচাষিরা উন্মত্ত হয়ে উঠল। তারা দল বেঁধে জোতদার ও নায়েবদের কাছারি আক্রমণ করে আগুন ধরিয়ে দিতে লাগল। প্রতিরোধ গড়ে তুলল সরকারের সশস্ত্র পুলিশ আর জোতদারদের পোষা লেঠেলবাহিনী। সংঘর্ষে হতে লাগল প্রাণহানি ও রক্তক্ষয়। নামখানার শিবরামপুর গ্রামে নগেন দোলুই, বুধাখালি গ্রামের সুরেন, সুধীর, ও নীলকণ্ঠ পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারাল।
সুন্দরবন অঞ্চলে পুলিশের গুলিতে এই হতাহতের সংবাদ যত দ্রুত ছড়াতে লাগল ততই তেভাগার সংগ্রাম শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগল। গ্রামের নারীরাও এতে সামিল হতে শুরু করল। ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট পার্টিকে ‘নিষিদ্ধ’ ঘোষণা করল গণ-আন্দোলনে ভীত সরকার। ফলে অশোক বোস, কংসারি হালদার, প্রভাস রায়, যতীন মাইতি, গুণধর মাইতি প্রমুখ নেতারা গোপন ঘাঁটি থেকে সংগঠন গড়ে তোলা ও তেভাগার আন্দোলন সংগঠিত করার কাজ করতে লাগলেন। সরকার জানত নেতাদের ধরতে পারলেই আন্দোলনকে থামিয়ে দেওয়া যাবে। তাই পুলিশ নেতাদের ধরার জন্য গুপ্তচর লাগাল। নেতাদের ধরে দিতে পারলে পুলিশ পুরস্কার ঘোষণা করল। ফতোয়া জারি করল – “কমিউনিস্ট ‘সন্ত্রাসবাদী’দের নেতা অশোক বোস ও লাটদারদের ত্রাস গজেন মালীকে হাতেনাতে ধরা চাই।” তখন তেভাগা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কিছু স্থানীয় মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদী-নালা সাঁতরে, জঙ্গল ডিঙিয়ে নেতাদের গোপন ঘাঁটি থেকে পার্টির নানা নির্দেশ গ্রামে গ্রামে আন্দোলনরত ভাগচাষিদের কাছে পৌঁছে দিত এবং অনেক গোপন খবর নেতাদের কাছেও নিয়ে আসত। তেমনই একজন হলেন অতুল কামিল্যা। নদী সাঁতরে উনি চন্দনপিঁড়িতে খবর পৌঁছে দিতেন। শুধু তাই-ই নয়, ছেনি-হাতুড়ি-করাত দিয়ে আন্দোলনকারীদের জন্য অস্ত্রও তৈরি করে দিত। সেই অস্ত্র গোপনে তেভাগার বিপ্লবীদের সরবরাহ করা হত। নদীর চরে বিপ্লবীদের জন্য বোমা লুকোতে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন ভূপতি।
জঙ্গলে লুকিয়ে তেভাগার বিপ্লবীদের গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিত গজেন মালী, ভূষণ কামিল্যা, বিজয় মণ্ডলরা। পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিতে এই গজেন মালী মাসের পর মাস ডিঙি নৌকোয় করে নদীতে ভেসে জঙ্গল-খাঁড়িতে ঘুরে বেড়িয়েছেন। দিনের পর দিন এমন অবস্থাও গেছে যে পেটে একটা দানা-পানি পড়েনি। গজেন মালীর মাথার দাম পুলিশ ঘোষণা করেছিল ১০ হাজার টাকা। শেষরক্ষা অবশ্য হয়নি। গজেন ধরা পড়ে যান। দীর্ঘদিন জেলের অন্ধকারে পচেছেন গজেন মালী।
বাংলা ১৩৫৫ সনের ২০ কার্তিক। চন্দনপিঁড়ির যেদিকে চোখ যায় মাঠে মাঠে হাওয়ায় দোলা খাচ্ছে পাকা ধানের শীষ। কোনও কোনও জমিতে সবে ধান কাটা শুরু হয়েছে। চন্দনপিঁড়ির ভাগচাষিরা সঙ্কল্পবদ্ধ – তারা জোতদার ও নায়েবের খামারে কিছুতেই ধান তুলবে না। গ্রামে খবর এল সেনদের কাছারির নায়েব পরেশ দাস বারো জন সশস্ত্র পুলিশকে পথ দেখিয়ে চন্দনপিঁড়ি গ্রামে নিয়ে আসছে গ্রামের কমিউনিস্ট কৃষক নেতা তথা সমিতির সম্পাদক রাখাল জানাকে গ্রেফতার করানোর জন্য। সাথে সাথে গ্রামের মহিলা ও পুরুষেরা জড়ো হতে শুরু করল। মহিলারা নিল বঁটি ও ঝাঁটা, পুরুষরা লাঠি। প্রায় আড়াইশো মহিলা ও এক হাজার পুরুষের মিছিল এগিয়ে চলল পুলিশের পথ রোধ করার জন্য। সামান্য এগোতেই মুখোমুখি হল পুলিশের। সামনে পথপ্রদর্শক পরেশ আর গ্রামের এক বিশ্বাসঘাতক রাইচরণ। জনরোষ দেখে পুলিশ ভয় পেয়ে সাময়িক পিছু হঠল। উত্তেজিত গ্রামবাসী পাকড়াও করল পরেশকে। এমন সময় দেখা গেল কাকদ্বীপ থানার বড়বাবু ৩২ জন সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে হাজির হয়েছেন। পুলিশের পথ অবরোধ করল উত্তেজিত জনতা। বিশ্বাসঘাতক রাইচরণ যেই চেঁচিয়ে উঠল, “পথ ছাড় তোরা,” অমনি গ্রামের মেয়ে সরোজিনী “বিশ্বাসঘাতক” বলে চিৎকার করে রাইচরণের মুখে সজোরে কষিয়ে দিল ঝাঁটার বাড়ি। সাথে সাথে থানার বড়বাবু চিৎকার করে নির্দেশ দিলেন, “ফায়ার!” নির্বিচারে গুলি ধেয়ে এল মিছিলের দিকে। প্রথমে বুকে গুলি খেয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল অশ্বিনী। “একটু জল,” একটু জল,” বলে কাতরাতে লাগল মৃত্যুপথযাত্রী। ছুটে এল দিদি সরোজিনী। রাস্তার পাশে ডোবায় জমা নোনা জলে আঁচল ভিজিয়ে সেই জলের ফোঁটা ফেলল ভাইয়ের মুখে। আর তখনই এক পুলিশ বন্দুকের আগায় লাগানো ফলা দিয়ে ফালাফালা করে দিল সরোজিনীর তলপেট। ভাই-বোনের রক্তে দলা পাকিয়ে যেতে লাগল চন্দনপিঁড়ির নোনা ধুলো। ছুটে এল গর্ভবতী অহল্যা দাস। অশ্বিনীকে বাঁচানোয় জন্য কোলে তুলে নিতেই তলপেটে এসে লাগল পুলিশের গুলি। গুলি খেয়েও অশ্বিনীকে নিয়ে দৌড়ে এগোতে যেতে এক পুলিশ সঙ্গিন দিয়ে চিরে দিল গর্ভবতী অহল্যার পেট। এই দৃশ্য দেখেই লাঠি, বঁটি, ঝাঁটা নিয়ে পুলিশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল উন্মত্ত জনতা। কিন্তু পুলিশের গোলার সামনে অসহায়ভাবে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগল অসংখ্য নারী-পুরুষ। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল উত্তমী, বাতাসী, গজেন ভুঁঞ্যা, দেবেন বর্মণ। চন্দনপিঁড়ির ক্ষিপ্ত গ্রামবাসী পরেশের দেহ টুকরো টুকরো করে পুঁতে দিল সপ্তমুখী নদীর চরের নোনা কাদায়। ‘কাকদ্বীপ কনস্পিরেসি’ কেসে গ্রেফতার করা হল বহু আন্দোলনকারী ও তেভাগার নেতাদের।


সাহিত্যে সুন্দরবনের তেভাগাঃ
বিশ্ব ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাই যখনই শোষিত ও মেহনতি মানুষ ন্যায্য দাবি আদায়ের লড়াইয়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছে তখনই সমকালীন কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকরা সেই আন্দোলনে সহায়ক শক্তি জুগিয়েছেন তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। তেভাগা আন্দোলনও তার ব্যতিক্রম নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, গোলাম কুদ্দুস, আবু ইসহাক, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, ননী ভৌমিক, সুশীল জানা, সৌরী ঘটক, মিহির আচার্য, মিহির সেন প্রমুখ সাহিত্যিক তেভাগা আন্দোলন নিয়ে বেশ কিছু ছোটোগল্প লিখেছেন। সংখ্যাটা খুব বেশি নয়। সাকুল্যে ২১-২২টি। উপন্যাস লিখেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (খোয়াবনামা), শিশির দাস (শৃঙ্খলিত মৃত্তিকা) ও আব্দুল্লাহ রসুল (শহর থেকে গ্রাম)। ‘শৃঙ্খলিত মৃত্তিকা’-তে শিশিরবাবু কাকদ্বীপের তেভাগা আন্দোলনকে জীবন্ত তুলে ধরেছেন। তবে কাকদ্বীপের তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতে ১৯৯৪ সালে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের লেখা উপন্যাস “স্বজনভূমি” শুধু একটি উপন্যাস নয়, তেভাগা আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য দলিল।
উপন্যাস ও গল্পের সংখ্যা কম হলেও কবিতা ও গানের সংখ্যা নেহাত কম নয়। তেভাগা আন্দোলনকে উদ্দীপনা জোগাতে এইসব কবিতা ও গান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর ‘দুর্মর’ কবিতায় মন্বন্তরের যন্ত্রণা আর মৃত্যুভয় ভুলে কৃষকসমাজ যে জেগে উঠেছে তা প্রকাশ করেছেন।
হঠাৎ নিরীহ মাটিতে কখন
জন্ম নিয়েছে সচেতনতার ধান,
গত আকালের মৃত্যুকে মুছে
আবার এসেছে বাংলাদেশের প্রাণ।
‘হয় ধান নয় প্রাণ’ এ শব্দে
সারা দেশ দিশাহারা,
একবার মরে ভুলে গেছে আজ
মৃত্যুর ভয় তারা।
তেভাগা নিয়ে একাধিক কবিতা লিখেছেন সমসাময়িক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায় ও রাম বসু। “পরাণ মাঝি হাঁক দিয়েছে” কবিতায় রাম বসু তেভাগা আন্দোলনে প্রান্তিক মানুষের প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করে লিখেছেন –
এবার আমরা ধান তুলে দিয়ে মুখ বুজিয়ে মরবো না,
এবার আমরা প্রাণ তুলে দিয়ে অন্ধকারে কাঁদবো না,
এবার আমরা তুলসীতলায় মনকে বেঁধে রাখবো না।
কিংবা তেভাগা আন্দোলনে নামখানার তুখোড় কৃষক নেতা গজেন মালীকে নিয়ে রাম বসুর লেখা “গজেন মালী” কবিতায় আমরা দেখতে পাই গজেন মালীর আহ্বান কীভাবে প্রান্তিক কৃষক সমাজের নারীদেরও উদ্দীপ্ত করেছিল।
জল নিয়ে ফেরা বৌ চমকায় বাঁকের কোণে,
এখান থেকে সে শাঁখে ফুঁ দিয়েছে সংগোপনে,
গজেন মালীর গলার শব্দে কেঁপেছে তারা
মার খেয়ে ঘুরে রুখে উঠেছিল বাঁচবে যারা।
পুলিশের সঙ্গিন চন্দনপিঁড়ির কৃষক বধূ গর্ভবতী অহল্যা দাসের পেট ফালা-ফালা করে দেওয়ার মর্মন্তুদ কাহিনি যেসব কবির কবিতায় উঠে এসেছিল তাঁদের মধ্যে প্রবীর মজুমদার, সাধন গুহ ও সলিল চৌধুরী উল্লেখযোগ্য। “শোন গো ও দূরের পথিক” কবিতায় প্রবীর মজুমদার লিখেছেন –
রুধির রাঙা এই প্রাঙ্গণে ধূলিকণার মাঝে,
অহল্যা মার প্রসব ব্যথা আজো জেগে আছে
(ভাইরে) ঘরে ঘরে বধূ যখন সিঁথেয় সিঁদুর পরে,
অহল্যা মার রক্তলেখায় সে দাগ যেন ভরে।
সাধন গুহ তাঁর “শোন কাকদ্বীপ রে” কবিতায় লিখলেন –
শোন কাকদ্বীপ রে,
এই চন্দনপিড়ি শ্মশানে
অহল্যা মা’র চিতার আগুন জ্বলে রে।
আহা কিষানী মার প্রসব যন্ত্রণা
বাতাসে বাতাসে গুমরিয়া কান্দে রে।
সেই অহল্যা মা’র সন্তান শোন বন্ধু জন্ম নিল না,
বন্ধুরে – নতুন শিশু এই ধরণী দেখতে পেল না।
গানটিতে সুরারোপও করেছিলেন সাধন গুহ।




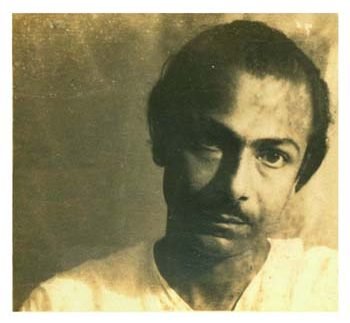
সলিল চৌধুরী লিখলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা ‘শপথ’। জন্মাতে না-পারা অহল্যা মায়ের গর্ভের সন্তানকে নিয়ে তিনি লিখলেন,
এই পৃথিবীর আলো-বাতাসের অধিকার পেয়ে
পায়নি যে শিশু জন্মের ছাড়পত্র
তার দাবী নিয়ে সেদিন রাত্রে সারা কাকদ্বীপে
কোন গাছে কোন কুঁড়িরা ফোটেনি
কোন অঙ্কুর মাথাও তোলেনি
প্রজাপতি যত আরো একদিন গুটি পোকা হয়ে ছিল
সেদিন রাত্রে সারা কাকদ্বীপে হরতাল হয়েছিল।
এই কবিতাতেই সলিল চৌধুরী আন্দোলনে সামিল হতে কৃষক, শ্রমিক, যুবক সবাইকে আহ্বান করলেন।
ঘরে ঘরে ডাক পাঠাই তৈরী হও জোট বাঁধো,
মাঠে কিষান, কলে মজুর, নওজোয়ান জোট বাঁধো,
এই মিছিল
এই মিছিল সর্বহারার সব পাওয়ার এই মিছিল
প্রতিজ্ঞা আর যশোদা মার রক্তবীজ এই মিছিল।
স্বামীহারা অনাথিনীর চোখের জল এই মিছিল,
শিশুহারা মাতাপিতার অভিশাপের এই মিছিল
এই মিছিল সর্বহারার সব পাওয়ার এই মিছিল
হও সামিল।
চন্দনপিঁড়ির মর্মান্তিক ঘটনা নিয়ে সমরেশ বসু লিখলেন বিখ্যাত ছোটোগল্প ‘প্রতিরোধ।’ গল্পে ‘রাধা’ চরিত্রের মধ্যে দিয়ে অহল্যা দাসকে তিনি চিত্রায়িত করেছেন। সুশীল জানার ছোটো গল্প ‘বেটি’-তে অত্যাচারের শিকার হয়ে মরতে হয়েছে কৃষক-রমণী পান্তিকে। সুন্দরবনের জমিদার-জোতদারদের অত্যাচারের সামনে কৃষকদের অসহায়তার চিত্র তুলে ধরেছেন ননী ভৌমিক তাঁর ‘বাদা’ গল্পে। সেখানেও গল্পের মূল চরিত্রে অহল্যা, সরোজিনী, উত্তমীদের অসহায়তার চিত্র সন্নিবিষ্ট করেছেন। বিনয় রায় বাঁধলেন গান। সেই গানে তিনি অহল্যা মায়ের গর্ভের সন্তানের হত্যার জন্য হাহাকারের পাশাপাশি তাঁর বিশ্বাসের কথা শোনালেন যে ঘরে ঘরে সেই সন্তান জন্মাবে এবং শোষকের বিরুদ্ধে তারাই সংগ্রাম গড়ে তুলবে।
অহল্যা মা তোমার সন্তান জন্ম নিল না
ঘরে ঘরে সেই সন্তানের প্রসব যন্ত্রণা
শত কংস ধ্বংস করে যে শিশু জন্মিবে
মাঠে মাঠে তারই জল্পনা
প্রাণ আর মানে না।
তবে তেভাগা আন্দোলনরত মেহনতি মানুষকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে যত গান রচিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় হল সলিল চৌধুরীর লেখা ও সুর দেওয়া গান।
হেই সামালো ধান হো
কাস্তেটা দাও শান হো
জান কবুল আর মান কবুল
আর দেবো না আর দেবো না
রক্তে বোনা ধান মোদের প্রাণ হো
গানটি তেভাগার প্রেক্ষিতে লেখা হলেও আজও সমান প্রাসঙ্গিক ও জনপ্রিয়। গানটি ইউরোপ ও রাশিয়াতেও দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল। সুইৎজারল্যান্ডে মাতৃ সম্মেলনে রেবা রায়চৌধুরী এই গানটি গাওয়ার পর ইউরোপে তাঁর নাম হয়ে যায় ‘হেই সামালো।’ গানটির সুর ও কথার আবেদন এমনই হৃদয়গ্রাহী। বিভিন্ন চলচ্চিত্রেও গানটিকে ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বনে প্রণব চৌধুরি পরিচালিত ‘হারানের নাতজামাই।’ এই গল্পে কৃষক নেতা ভুবন মণ্ডলকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য কৃষক রমণী ময়নার মা ভুবনকে জামাই সাজিয়ে নিজের মেয়ের ঘরে সারা রাত কাটাতে পাঠিয়েছিল। পরবর্তীকালে বাস্তবে সুন্দরবনের তেভাগা আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা হেমন্ত ঘোষালও একইভাবে পুলিশের হাত থেকে একবার বেঁচেছিলেন। মানিকবাবুর লেখা ‘ছোট বকুলপুরের যাত্রী’ গল্পেও কৃষক রমণীর মধ্যে শ্রেণিচেতনার বিকাশ এবং তার উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহস প্রত্যক্ষ করি। বস্তুতঃ তেভাগা আন্দোলন অবলম্বন করে মানিকবাবু যত গল্প লিখেছেন তা আর কোনও সাহিত্যিক লেখেননি।
তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা সলিল চৌধুরীর আর একটি গান “ধন্য আমি জন্মেছি মা তোমার ধূলিতে / জীবন মরণে তোমায় চাই না ভুলিতে” আজও তুমুল জনপ্রিয়। বড়া কমলাপুর, কাকদ্বীপ, ডোঙাজোড়া প্রভৃতি স্থানে জোতদার-জমিদার এবং তাদের মদতদাতা সরকারের বিরুদ্ধে কৃষক-মজুর যখন আন্দোলনরত তখন তিনি গানের মধ্যে দিয়ে হিন্দু-মুসলমান সবাইকে আহ্বান করলেন।
ও রাম রহিমের বাছা
ও বাঁচা আপন বাঁচা
চল ধান কাটি আর কাকে ডরি
নিজ খামার নিজে ভরি
কাস্তেটা শানাইরে …
ওই কমলাপুর বড়া
আর কাকদ্বীপ, ডোঙাজোড়া
এসেছে ডাক চলনা সবাই সোনা তুলি ঘরে।
সলিল চৌধুরী তেভাগা নিয়ে গান লিখেছেন আরও। তিনি “এই মাটিতে” নামে তেভাগা নিয়ে একটি নাটকও লিখেছিলেন। চন্দনপিঁড়িতে পুলিশের গুলিতে হত অহল্যা, সরোজিনী, বাতাসী, উত্তমী, অশ্বিনী, গজেন ও দেবেনের লড়াইকে উপজীব্য করে গণনাট্য সংঘ মঞ্চস্থ করে নাটক ‘নয়ানপুর।’
শিশু-কিশোরদের কাছে তেভাগার লড়াইয়ের কথা পরবর্তীকালে সহজ করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন সরোজমোহন মিত্র ও শুভময় মণ্ডল। সরোজমোহনবাবুর লেখা ‘বুদাখালির লড়াই’ অন্যতম কিশোরপাঠ্য।
সত্যি বলতে কি, তেভাগা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট গল্প, উপন্যাস, কবিতা, গান, নাটক ইত্যাদি নিয়ে তেমন চর্চা ও গবেষণা হয়নি। আর তাই হয়তো কালের গর্ভে অনেক গান ও কবিতা হারিয়ে গেছে। এই কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীদের অনেকে সরাসরি কৃষক আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। আবার কেউ কেউ তাঁদের রচনার মধ্যে দিয়ে কৃষক আন্দোলনকে গতিদান করেছেন। এইসব কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক বাংলার ইতিহাস ও সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদই নয়, ভবিষ্যৎ আন্দোলনের প্রেরণাও।
সুন্দরবনে তেভাগা আন্দোলনের প্রাপ্তিঃ
তেভাগার দাবি মেটার আগেই অধিকাংশ নেতাদের ধরপাকড় ও শাস্তি তেভাগা আন্দোলনকে তাৎক্ষণিক কাঙ্ক্ষিত সাফল্য এনে দিতে পারেনি। কিন্তু তা বলে তেভাগা আন্দোলনে প্রাপ্তির ভাঁড়ার কিন্তু খালি নয়।
প্রথমতঃ, তেভাগার লড়াই ছিল জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে শোষিত ও বঞ্চিত ভাগচাষি ও ক্ষেতমজুরদের লড়াই। জাতিভেদ ও ধর্মভেদ ঘুচে গিয়ে গড়ে উঠেছিল এক শ্রেণিগত ঐক্য। তার প্রমাণ আমরা পাই যখন দেখি ছেচল্লিশের দাঙ্গায় বাংলা জ্বলছিল, অথচ তখন সুন্দরবনে তার সামান্য আঁচও পড়েনি।
দ্বিতীয়তঃ, ন্যায্য দাবি আদায় করতে হলে শোষিত জনতার সংগ্রামের যে কোনও বিকল্প নেই তা সমাজের প্রান্তিক মানুষরা উপলব্ধি করতে পেরেছিল, দাবি আদায় করার সাহস অর্জন করেছিল এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে।
তৃতীয়তঃ, শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে মানুষকে সংঘবদ্ধ হতে শিখিয়েছে তেভাগা আন্দোলন।
চতুর্থতঃ, এই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে আজ উৎপন্ন ফসলের তিন চতুর্থাংশের আইনি অধিকার অর্জন করেছে ভাগচাষিরা।
পঞ্চমতঃ, এই আন্দোলনের ফলেই ভাগচাষিদের অকারণ উচ্ছেদ বন্ধ হয়েছে।
ষষ্ঠতঃ, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা ১৯৪৫ সালে তেভাগার পাশাপাশি যেসব দাবি তুলেছিল সেগুলির মধ্যে বেশিরভাগই পরবর্তীকালে অর্জিত হয়েছিল। যেমন, বর্গা জমিতে দখলি স্বত্ব প্রদান, প্রথা বহির্ভূত কর আদায় রদ ও দণ্ডনীয়, জমি চাষ না করে ফেলে রাখা দণ্ডনীয়, মহাজনের দেওয়া টাকা বা ধানের উপর সুদের হার ১২.৫ শতাংশ করা, ভূমিহীনদের মধ্যে অনাবাদি জমি বিলি বন্দোবস্ত করা, ভূমিহীনদের সরকারের পক্ষ থেকে সস্তায় চাল সরবরাহ করা ইত্যাদি।
সপ্তমতঃ, তেভাগা আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে পরবর্তীকালে ভূমি সংস্কার আইন, মহাজনি ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ আইন, বর্গাস্বত্ব আইন, জমি বণ্টন আইন, রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তন ইত্যাদি চালু হয়েছিল।
১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভাগচাষিদের অধিকার হয়েছে সুরক্ষিত, ভূমিহীন পেয়েছে ভূমি, বন্ধ হয়েছে মহাজনি শোষণ। জমিদারের উদ্বৃত্ত জমি গিয়েছে ভূমিহীনের কাছে। কৃষক পরিবারে ফিরেছে হাসি। ফিরেছে স্বাবলম্বন। ফিরেছে আর্থিক সুনিশ্চয়তা। আর এর জন্য বামপন্থী কৃষকসভার নেতৃত্বে তেভাগা আন্দোলনের অবদান অনস্বীকার্য।
——————
তথ্যসূত্রঃ
(১) তেভাগা আন্দোলন ও সুন্দরবন – সুকুমার দাস (প্রবন্ধ)
(২) তেভাগার কবিতাও গান – শরিফ আতিকুজ্জামান (প্রবন্ধ)
(৩) বাংলা কথা-সাহিত্যে তেভাগা কৃষক-সংগ্রাম – সুস্নাত দাশ (প্রবন্ধ)
চিত্রঋণ-
তেভাগা ও কাকদ্বীপ সংক্রান্ত ছবিগুলি লেখক সংগ্রহ করেছেন।
বাকি ছবির জন্যে কৃতজ্ঞতাস্বীকারঃ অন্তর্জাল
